আমরা তিনজন
বুদ্ধদেব বসু
আমরা তিনজন একসঙ্গে তার প্রেমে পড়েছিলাম : আমি, অসিত আর হিতাংশু; ঢাকায় পুরানা পল্টনে, উনিশ-শো সাতাশে। সেই ঢাকা, সেই পুরানা পল্টন, সেই মেঘে-ঢাকা সকাল!
এক পাড়ায় থাকতাম তিনজন। পুরানা পল্টনে প্রথম বাড়ি উঠেছিল তারা-কুটির, সেইটে হিতাংশুদের। বাপ তার পেনশন পাওয়া সাব-জজ, অনেক পয়সা জমিয়েছিলেন এবং মস্ত বাড়ি তুলেছিলেন একেবারে বড় রাস্তার মোড়ে। পাড়ার পয়লা নম্বর বাড়ি তারা-কুটির, দু-অর্থেই তাই, সবচেয়ে আগেকার এবং সবচেয়ে ভালো। ক্রমে ক্রমে আরো অনেক বাড়ি উঠে ঘাস আর লম্বা-লম্বা চোর-কাঁটা ছাওয়া মাঠ ভরে গেল, কিন্তু তারা-কুটিরের জুড়ি আর হলো না।
আমরা এসেছিলাম কিছু পরে, অসিতদের বাড়ির তখন ছাদ পিটোচ্ছে। একটা সময় ছিল, যখন ঐ তিনখানাই বাড়ি ছিল পুরানা পল্টনে; বাকিটা ছিল এবড়োখেবড়ো জমি, ধুলো আর কাদা, বর্ষায় গোড়ালি-জলে গা-ডোবানো হলদে-হলদে-সবুজ রঙের ব্যাঙ আর নধর সবুজ ভিজে-ভিজে ঘাস। সেই বর্ষা, সেই পুরানা পল্টন, সেই মেঘ-ঢাকা দুপুর!
আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকতাম সব সময়—যতটা এবং যতক্ষণ থাকা সম্ভব। রোজ ভোরবেলায় আমার শিয়রের জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে অসিত ডাকত, ‘বিকাশ! বিকাশ!’ আর আমি তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে আসতাম, দেখতাম অসিত সাইকেলে বসে আছে এক-পা মাটিতে ঠেকিয়ে—এমন লম্বা ও, কাঁধে হাত রাখতে কনুই ধরে যেত আমার। হিতাংশুকে ডাকতে হতো না, দাঁড়িয়ে থাকত তাদের বাগানের ছোট ফটকের ধারে, কি বসে থাকত বাগানের নিচু দেয়ালে পা ঝুলিয়ে, তারপর অসিত সাইকেলে চেপে চলে যেত পাকা সড়ক ধরে স্কুলে, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে; আমি আর হিতাংশু ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম হাতে হাত ধরে, হাওয়ায় গন্ধ, যেন কিসের, যেন কার, সে-গন্ধ আজও যেন পাই, কী মনে পড়ে, কাকে মনে পড়ে!
বিকেলে দুটি সাইকেলে তিনজনে চড়ে প্রায়ই আমরা শহরে যেতাম, কোনো দিন বিখ্যাত ঘোষবাবুর দোকানে চপ-কটলেট খেতে, কোনো দিন শহরে একটিমাত্র সিনেমায়, কোনো দিন চিনেবাদাম পকেটে নিয়ে নদীর ধারে। সাইকেল চালানোটা আমার জীবনে হলো না—চেষ্টা করেও শিখতে পারিনি ওটা, কিন্তু ঐ দু-চাকার গাড়িতে চড়েছি অনেক; কখনো অসিতের, কখনো হিতাংশুর গলগ্রহ হয়ে লম্বা-লম্বা পাড়ি দিয়েছি তাদের পিছনে দাঁড়িয়েই। আবার কত সন্ধ্যা কেটেছে পুরানা পল্টনেরই মাঠে, ঘাসের সোফায় শুয়ে-বসে ছোট ছোট তারা ফুটছে আকাশে, চোর-কাঁটা ফুটছে কাপড়ে, হিতাংশুদের সামনের বারান্দার লণ্ঠনটা মিটমিট করছে দূর থেকে। এ-সময়টা হিতাংশ বেশিক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকত না—আটটার মধ্যে তাকে ফিরতেই হতো বাড়িতে। অত কড়া শাসন আমার ওপর ছিল না, অসিতের ওপরেও না, দুজনে বসে থাকতাম অন্ধকারে, ফেরবার সময় আস্তে আস্তে একবার ডাকতাম হিতাংশুকে, পড়া ফেলে উঠে এসে চুপি চুপি দু-একটা কথা বলেই সে চলে যেত।
আমরা তিনজন তিনজনের প্রেমে পড়েছিলাম, আবার তিনজন একসঙ্গে অন্য একজনের প্রেমে পড়লাম, সেই ঢাকায়, পুরানা পল্টনে উনিশ-শো সাতাশ সনে।
নাম তার অন্তরা। তখনকার ঢাকার পক্ষে নামটি অত্যন্তই শৌখিন, কিন্তু ঢাকার মতো কিছুই তো তাঁদের নয়, মেয়ের নামই বা হবে কেন। ভদ্রলোক বাড়িতেও প্যান্ট পরে থাকেন, আর ভদ্রমহিলা এমন সাজেন যে পিছন থেকে হঠাৎ তাঁকে তাঁর মেয়ে বলে ভুল হয়—আর তাঁর মেয়ে, তাঁদের মেয়ে, তার কথা আর কী বলব! সে সকালে বাগানে বেড়ায়, দুপুরে বারান্দায় বসে থাকে বই কোলে নিয়ে, বিকেলে রাস্তায় হাঁটে প্রায় আমাদের গা ঘেঁষেই, সব সময় দেখা যায় তাকে, মাঝে মাঝে শোনা যায় গলার আওয়াজ—সেই ঢাকায়, সুদূর সাতাশ সনে, কোনো একটা মেয়েকে চোখে দেখা যখন সহজ ছিল না, যখন বন্ধ-গাড়ির দরজার ফাঁকে একটুখানি শাড়ির পাড় ছিল আমাদের স্বর্গের আভাস, তখন—এই যে মেয়ে, যাকে আমরা দেখতে পাই একেক দিন একেক রঙের শাড়িতে, আর তার ওপর নাম যার অন্তরা, তার প্রেমে পড়ব না এমন সাধ্য কি আমাদের!
নামটা কিন্তু বের করেছিলাম আমি। রোজ সই করে পাউরুটি রাখতে হয় আমাকে, একদিন রুটিওয়ালার খাতায় নতুন একটা নাম দেখলাম নীল কালিতে বাংলা হরফে পরিষ্কার করে লেখা : ‘অন্তরা দে’। একটু তাকিয়ে থাকলাম লেখাটুকুর দিকে, খাতা ফিরিয়ে দিতে একটু দেরি করলাম, তারপর বিকেলে হিতাংশুকে বললাম, ‘নাম কি অন্তরা?’
‘কার’—কিন্তু তক্ষুনি কথাটা বুঝে নিয়ে হিতাংশু বলল, ‘বোধ হয়।’ অসিত বলল, ‘সুন্দর নাম!’
‘ডাকে তরু বলে।’
তরু! এই ঢাকা শহরেই দু-তিনশো অন্তত তরু আছে, কিন্তু সে-মুহূর্তে আমার মনে হলো এবং আমি বুঝলাম অসিতেরও মনে হলো যে সমস্ত বাংলা ভাষায় তরুর মতো এমন একটি মধুর শব্দ আর নেই। তা হোক, হিতাংশুর একটু বাজে কথা বলা চাই। কেননা যাকে নিয়ে বা যাদের নিয়ে কথা হচ্ছে, তাদেরই বাড়ির এক তলায় তারা ভাড়াটে, আমাদের চাইতে বেশি না-জানলে ওর মান থাকে না। তাই ও নাকের বাঁশিটা একটু কুঁচকে বলল, ‘অন্তরা থেকে তরু—এটা কিন্তু আমার ভালো লাগে না।’
‘ভালো না কেন, খুব ভালো!’ গলা চড়িয়ে দিলাম, কিন্তু ভেতরটা কেমন দমে গেল। ‘আমি হলে অন্তরাই ডাকতাম।’
কী সাহস! কী দুঃসাহস! তুমি ডাকতে, তাও আবার নাম ধরে। ইস! প্রতিবাদের তাপে আমার মুখ গরম হয়ে উঠল, বেশ চোখা চোখা কয়েকটা কথা মনে-মনে গোছাচ্ছি, ফস করে অসিত বলে উঠল, ‘আমিও তা-ই।’
বিশ্বাসঘাতক!
এ-রকম ছোট ছোট ঝগড়া প্রায়ই হতো আমাদের। এমন দিন যায় না যেদিন ওকে নিয়ে কোনো কথা না হয়, আর এমন কোনো কথা হয় না যাতে তিনজনেই একমত হতে পারি। সেদিন যে নীল শাড়ি পরেছিল তাতেই বেশি মানিয়েছিল, না কালকের বেগুনি রঙেরটায়; সকালে যখন বাগানে দাঁড়িয়ে ছিল তখন পিঠের ওপর বেণি দুলছিল, না চুল খোলা ছিল, বিকেলে বারান্দায় বসে কোলের ওপর কাগজ রেখে কী চিঠি লিখছিল, না আঁক কষছিল—এমনই সব বিষয় নিয়ে চেঁচামেচি করে আমরা গলা ফাটাতুম। সবচেয়ে বেশি তর্ক হতো যে-কথা নিয়ে সেটা একটু অদ্ভুত : ওর মুখের সঙ্গে মোনালিসার মিল কি খুব বেশি, না অল্প একটু, না কিছুই না। আমি তখন প্রথম মোনালিসার ছাপা ছবি দেখেছি এবং বন্ধুদের দেখিয়েছি। হঠাৎ একদিন আমারই মুখ দিয়ে বেরোল কথাটা—‘ওর মুখ অনেকটা মোনালিসার মতো।’ তারপর এ নিয়ে অসংখ্য কথা খরচ করেছি আমরা, কোনো মীমাংসা হয়নি; তবে একটা সুবিধা এই হলো যে আমাদের মুখে-মুখে ওর নাম হয়ে গেল মোনালিসা। অন্তরাতে যতই সুর ঝরুক, তরুতে যতই তরুণতা, যে-নামে ওকে সবাই ডাকে সে-নামে তো আমরা ওকে ভাবতে পারি না—অন্য একটি নাম, যা শুধু আমরা জানি, আর কেউ জানে না, এমন একটি নাম পেয়ে আমরা যেন ওকেই পেলাম।
হিতাংশুকে প্রায়ই বলতাম, ‘তোমার সঙ্গে একদিন আলাপ হবেই—একই তো বাড়ি’, আর হিতাংশুও একটু লাল হয়ে বলত, ‘যাঃ!’ যার মানে হচ্ছে যে সেটা হলেও হতে পারে—আর তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনাই চলত আমাদের, কিন্তু মনে-মনে আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে এ-সব কিছু না, শুধুই কথার কথা।
একদিন সন্ধ্যার একটু পরে তিনজনে ফিরছি সাইকেলে রমনা বেড়িয়ে, আমি হিতাংশুর পিছনে, নির্জন পথে নিশ্চিন্তে গল্প চালিয়েছি, হঠাৎ হিতাংশু কথা বন্ধ করে সাইকেলের ওপর কী রকম কেঁপে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম সাইকেল থেকে, টাল সামলাতে গিয়ে টেনে ধরলাম হিতাংশুর জামার গলা; ‘উঃ’ বলে সে নেমে পড়ল, আমি পায়ের তলায় মাটি পেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে মোটা গলায় কে একজন বলে উঠলেন, ‘Take care young man!’ তাকিয়ে দেখি, ঠিক আমাদের সামনে দে-সাহেব দাঁড়িয়ে, আর তাঁর স্ত্রী—আর কন্যা। অসিত সাইকেলটা একটু ঘুরিয়ে এক পা মাটিতে ঠেকিয়ে চুপ করে আছে, তার মুখের ভাবটা বেশ বীরের মতো।
‘Really you must—’ বলতে বলতে দে-সাহেব হিতাংশুর মুখের ওপর চোখ রাখলেন।— ‘Oh it’s you! কেশব বাবুর ছেলে!’
‘আমি স্পষ্ট দেখলাম, হিতাংশুটা বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।’
‘আর এরা—তিনজনকে একসঙ্গেই তো দেখতে পাই সব সময়। বন্ধু বুঝি! বেশ, বেশ। I like young men. এসো একদিন আমাদের ওখানে তোমরা।’
ওঁরা চলে গেলেন। আমরা রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে ঘাসের ওপর পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম লম্বা হয়ে। একটু পরে অসিত বলল, ‘কী কাণ্ড! হিতাংশু ঘাবড়ে গিয়েছিলে না?’
‘না তো! ঘাবড়াব কেন? ব্রেকটা হঠাৎ—’
‘কোনো দিন তো এ-রকম হয় না। আর আজ কিনা ওঁদের সামনে—’
‘বেশ তো! হয়েছে কী? কারো গায়েও পড়েনি, পড়েও যাইনি, হঠাৎ ব্রেক কষতে গিয়ে—’
‘না, না, তুমি তো ঠিকই নেমেছিলে, তবে তোমার মুখটা যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। আর বিকাশ তো—’
আমার নাম করতেই আমি খেঁকিয়ে উঠলাম, ‘চুপ করো, ভালো লাগে না!’
‘ও বোধ হয় একটু হেসেছিল’, অসিত তবু ছাড়ল না (‘ও’ বলতে কাকে বোঝায় তা বোধ হয় না বললেও চলে)।
‘হেসেছিল তো বয়ে গেল!’ চিৎকার করল হিতাংশু, কিন্তু সে চিৎকার যেন কান্না।
‘তুমি দেখেছিলে বিকাশ? ঠিক মোনালিসার হাসির মতো কি?’
‘যা বোঝো না তা নিয়ে ঠাট্টা কোরো না!’ বলতে গিয়ে আমার গলা ভেঙে গেল। সে-রাত্রে ভালো ঘুমোতে পারলাম না, দুদিন আধমরা হয়ে রইলাম, সাত দিন মন-মরা।
রাগ করি আর যা-ই করি, আমাদের মধ্যে অসিতটাই তুখোড়। সে কেবলই বলতে লাগল, ‘চল না একদিন যাই আমরা ওঁদের ওখানে।’
‘পাগল।’
‘পাগল কেন? দে-সাহেব বললেন তো যেতে! বললেন না?’
ক্রমে-ক্রমে হিতাংশুর আর আমারও ধারণা জন্মাল যে দে-সাহেব সত্যিই আমাদের যেতে বলেছেন, আমরা গেলে রীতিমতো সুখী হবেন তিনি, না-গেলে দুঃখিত হবেন—এমনকি তাঁকে অসম্মানই করা হবে তাতে। তাঁর সম্মান রক্ষার জন্য ক্রমশই আমরা বেশি রকম ব্যস্ত হতে লাগলাম। রোজ সকালে স্থির করি ‘আজ’, রোজ বিকেলে মনে করি, ‘আজ থাক’। কোনো দিন দেখি ওঁরা বাগানে বসেছেন বেতের চেয়ারে; কোনো দিন বাড়ির সামনে মোটরগাড়ি দাঁড়ানো, তার মানে শহরের একমাত্র ব্যারিস্টার দাস-সাহেব বেড়াতে এসেছেন। আর কোনো দিন বা চুপচাপ দেখে ধরে নিই ওঁরা বাড়ি নেই। দৈবাৎ একদিন হয়তো চোখে পড়ে দে-সাহেব একা বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, মনে হয় এইটে ভারি সুসময়, কিন্তু বাগানের গেটের সামনে পা থমকে যায় আমাদের, অসিতের যতটা নয় ততটা হিতাংশুর, হিতাংশুর ততটা নয় যতটা আমার, একটু ঠেলাঠেলি ফিসফিসানি হয়, আর শেষ পর্যন্ত তারা-কুটির ছাড়িয়ে মোড় ঘুরে আমরা অন্যদিকে চলে যাই। কেবলই মনে হয় এখন গেলে বিরক্ত হবেন, আবার তখনই ভাবি—বিরক্ত কেন, আর এ নিয়ে এত ভাববারই বা কী আছে, মানুষ কি মানুষের সঙ্গে দেখা করে না? আমরা চোরও নই, ডাকাতও নই, যাব, বসব, আলাপ করব, চলে আসব—ব্যস!
সেদিন আকাশে মেঘ টিপটিপ বৃষ্টি। বাইরে থেকে মনে হলো ওঁরা বাড়িতেই আছেন। ছোট্ট গেট ঠেলে সকলের আগে ঢুকল অসিত, লম্বা ফরসা, সুশ্রী; তারপর হিতাংশু, গম্ভীর, চশমা পরা, ভদ্রলোক মাফিক; আর সকলের শেষে পুঁচকে আমি। বাগান পার হয়ে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম আমরা, কাউকে ডাকব কি না, কাকে ডাকব, কী বলে ডাকব—এসব আমরা যতক্ষণ ধরে ভাবছি, ততক্ষণ পরদা ঠেলে দে-সাহেব নিজেই বেরিয়ে এলেন। দাঁতের ফাঁকে পাইপ চেপে ধরে বললেন, ‘Yes?’
এই বিজাতীয় সম্ভাষণে সপ্রতিভ অসিতও একটু বিচলিত হলো। ‘আমি—আমরা—মানে আমরা এসেছিলাম—আপনি বলেছিলেন—’ আবছা আলোয় তখন দে-সাহেব আমাদের চিনলেন। ‘ও, তোমরা! তা…’
অসিত আবার বলল, ‘আপনি বলেছিলেন আমাদের একদিন আসতে।’
‘ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ…’ একটু কেশে—‘এসো, এসো তোমরা’, পর্দা তুলে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন দে-সাহেব, আমরাও দাঁড়িয়ে থাকলাম।
‘যাও, ভেতরে যাও।’
ঢুকতে গিয়ে হিতাংশু তার নিজেরই বাড়ির চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে আমার পা মাড়িয়ে দিল, খুব লাগল আমার, কিন্তু চুপ করে থাকা ছাড়া তখন আর উপায় কী। আমাদের কাদামাখা স্যান্ডেলে ঝকঝকে মেঝে নোংরা করে এলাম আমরা। কী সুন্দর সাজানো ঘর, এমন কখনো দেখিনি। পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। সামনের দিকে সোফায় বসে মিসেস দে উল বুনছেন, আর দেয়ালের সঙ্গে ঠেকানো কোণের চেয়ারটিতে বসে আছে আমাদের মোনালিসা, কোলের ওপর মস্ত মোটা নীল মলাটের বইয়ের পাতায় চোখ নামিয়ে।
দে-সাহেব বললেন, ‘সুমি, এই আমাদের পুরানা পল্টনের থ্রি মস্কেটিঅর্স। এটি কেশব বাবুর ছেলে, আর এরা…’
হিতাংশু পরিচয় করিয়ে দিল, ‘এর নাম অসিত আর এই হচ্ছে বিকাশ।’
মিসেস দে মৃদু হেসে মৃদুস্বরে বললেন, ‘তিন বন্ধু বুঝি তোমরা? বেশ, রোজই তো দেখি তোমাদের। বসো।’
একটা লম্বা সোফায় ঝুপঝুপ বসে পড়লাম তিনজনে। মিসেস দে ডাক দিলেন—’তরু’!
মোনালিসা চোখ তুলল।
‘এঁরা আমাদের প্রতিবেশী—আর এই আমার মেয়ে।’
মোনালিসা বই রেখে উঠল, ছিপছিপে সবুজ একটি গাছের মতো দাঁড়াল, অল্প হাওয়ায় গাছ যেমন নড়ে, তেমনি করে মাথা নোয়াল একটু, তারপর আবার চেয়ারে বসে বই খুলে চোখ নিচু করল।
আমার মনে হলো আমি স্বপ্ন দেখছি।
অসিত কলকাতার ছেলে, আমাদের সকলের চাইতে খবর রাখে বেশি, চটপট কথা বলতেও পারে; আর হিতাংশু—সেও তার বাবার সঙ্গে নানা দেশ ঘুরেছে, উচ্চারণ পরিষ্কার, আর তা ছাড়া এই তারা-কুটির তো তাদেরই বাড়ি। কথাবার্তা যা একটু তা ওরা দুজনেই বলল, আমি মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ, কী বলব ভেবেও পেলাম না, বলতেও ভরসা হলো না, পাছে আমার বাঙাল টান বেরিয়ে পড়ে। মোনালিসাকে দেখবার ইচ্ছা ভেতরে-ভেতরে পাগল করে দিচ্ছিল আমাকে, কিন্তু কিছুতেই কি একবারও চোখ তুলতে পারলাম!
ইলেকট্রিসিটি না থাকলে জীবন কী রকম দুর্বহ, ঢাকার মশা কী সাংঘাতিক, রমনার দৃশ্য কত সুন্দর, এসব কথা শেষ হবার পর মিসেস দে বললেন, ‘তোমরা কি কলেজে পড়ো?’
অসিত যথাযথ জবাব দিয়ে সগর্বে বলল, ‘হিতাংশু পনেরো টাকা স্কলারশিপ পেয়েছে ম্যাট্রিকে।’
‘বাঃ বেশ, বেশ। আমার মেয়ে তো অঙ্কের ভয়ে পরীক্ষাই দিতে চায় না।’
হঠাৎ ঘরের কোণ থেকে তারের মতো একটি আওয়াজ বেজে উঠল, ‘বাবা, কীটস কত বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন?’
দে-সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমরা কেউ বলতে পারো?’
অসিত ফস করে বলল, ‘বিকাশ নিশ্চয়ই বলতে পারবে—বিকাশ কবিতা লেখে।’
‘সত্যি?’ মুখে একটি ছেলেমানুষি হাসি ফোটালেন মিসেস দে, আর মুহূর্তের জন্য—আমি অনুভব করলাম—মোনালিসার চোখও আমার ওপর পড়ল। হাত ঘেমে উঠল আমার, কানের ভেতর যেন পিঁ-পিঁ আওয়াজ দিচ্ছে।
সবসুদ্ধু কতটুকু সময়? পনেরো মিনিট? কুড়ি মিনিট? কিন্তু বেরিয়ে এলাম যখন এত ক্লান্ত লাগল, কলেজে চারটা-পাঁচটা লেকচার শুনেও তত লাগে না।
মিসেস দে জোর করেই দুটা ছাতা দিয়েছিলেন আমাদের, কিন্তু ছাতা আমরা খুললাম না, টিপটিপ বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মাঠের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম। হঠাৎ অসিত—বকবক না করে ও থাকতেও পারে না—বলে উঠল, কী চমৎকার ওঁরা!’
‘সত্যি! চমৎকার!’ হিতাংশু সায় দিল সঙ্গে সঙ্গে।
আমি কথা বললাম না, কোনো কথাই ভালো লাগছিল না আমার।
একটু পরে অসিত আবার বলে, ‘কিন্তু জুতোগুলো বাইরে ছেড়ে গেলেই পারতাম আমরা! আর হিতাংশু, তুমি আবার আজ হোঁচট খেলে!’
‘কখন?’
‘ঘরে ঢুকতে গিয়ে।’
‘যাঃ!’
‘যাঃ আবার কী। আর ঘুরে ঢুকে নমস্কার করেছিলে তো মিসেস দে-কে?’
‘নিশ্চয়ই!’ একটু চুপ করে থাকল হিতাংশু, তারপর হঠাৎ বলল, কিন্তু যখন মোনালিসা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল…’
অন্ধকারে আমরা তিন বন্ধু একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম এবং অন্ধকারেই বোঝা গেল যে তিনজনেরই মুখ ফ্যাকাসে হয়েছে। একটি মেয়ে, একজন ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন, আর আমরা কিনা জরদ্গবের মতো বসেই থাকলাম—উঠে দাঁড়ালাম না, কিছু বললাম না, কিচ্ছু না, ওঁরা আমাদের বাঙাল ভাবলেন, কাঠ-বাঙাল, জংলি, বর্বর, খাস কলকাতার ছেলে অসিত মিত্তিরও আমাদের মুখ-রক্ষা করতে পারল না।
কী যে মন-খারাপ হলো, কী আর বলব।
পরের দিন তিনজনে আবার গেলাম ছাতা ফেরত দিতে। চাকর আমাদের ঘরে নিয়ে বসাল, তারপর—তারপর মোনালিসাই এলো ঘরে, তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম, একটু হেসে বললাম, ‘এই ছাতাটা…’! ‘ও মা! এর জন্য আবার…বসুন…।’ মনে-মনে এই রকম ভেবে গিয়েছিলাম ঘটনাটা, কিন্তু হলো একটু অন্য রকম। চাকর এসে ছাতাটি নিয়ে ভেতরে চলে গেল, আর ফিরে এলো না, কেউই এলো না। আমরা একটু দাঁড়িয়ে থেকে মাথা নিচু করে নিঃশব্দে ফিরে এলাম—কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। না, না। ঐ সুন্দর করে সাজানো ঘর, যেখানে সাদা ধবধবে আলোয় দেয়ালের প্রতিটি কোণ ঝকঝক করে, আর কোণের চেয়ারে বসে পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়েটি কোনো এক নীল মলাটের আশ্চর্য বইয়ের পাতা ওল্টায়—সেখানে জায়গা নেই আমাদের। কিন্তু তাতে কী। মোনালিসা—মোনালিসাই। ঝমঝম করে বর্ষা নামল পুরানা পল্টনে, মেঘে-ঢাকা সকাল, মেঘ-ডাকা দুরু দুরু দুপুর, নীল জ্যোৎস্নায় ভিজে-ভিজে রাত্রি। পনেরো দিন ধরে প্রায় অবিরাম বৃষ্টির পর প্রথম যেদিন রোদ উঠল, সেদিন বাইরে এসে দেখি শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তারের মোটরগাড়ি তারা-কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে।
হিতাংশুকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমাদের বাড়িতে কারো অসুখ নাকি?’
‘না তো!’
তবে কি ওদের বাড়িতে—প্রশ্নটা উচ্চারিত না হয়েও ব্যক্ত হলো। পরের দিন হিতাংশু গম্ভীর মুখে বলল, ‘ওদের বাড়িতেই অসুখ।’
‘কার?’
‘ওরই অসুখ।’
‘ওর অসুখ!’
‘ওর!’
সেদিনও বড় ডাক্তারের গাড়ি দেখলাম, তার পরদিন দুবেলাই। আমরা কি একবার যেতে পারি না, কিছু করতে পারি না? ঘুরঘুর করতে লাগলাম রাস্তায়, ডাক্তারের গাড়ির আড়ালে। ডাক্তার বেরিয়ে এলেন, দে-সাহেব সঙ্গে সঙ্গে গেট পর্যন্ত। আমাদের চোখেই দেখলেন না তিনি, তারপর হঠাৎ দেখতে পেয়ে বললেন, ‘তোমরা একবার যাও তো ভেতরে, উনি একটু কথা বলবেন।’
সিঁড়ির ওপরের ধাপে দাঁড়িয়েছিলেন মিসেস দে, এক সিঁড়ি নিচে দাঁড়িয়ে অসিত বলল, ‘আমাদের ডেকেছেন, মাসিমা?’ কলকাতার ছেলে, ডাক-টাকগুলো দিব্যি আসে, আমি মরে গেলেও ওসব পারি না।
মিসেস দে বললেন, ‘তরুর অসুখ।’ তার কণ্ঠস্বর আমার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিল।
‘কী অসুখ?’
‘টাইফয়েড!’ ঐ ভয়ংকর শব্দটা আস্তে উচ্চারণ করে তিনি বললেন, ‘আমার কিছু ভালো লাগছে না।’
অসিত বলে উঠল, ‘কিছু ভাববেন না। আমরা সব করে দেব।’
‘পারবে, পারবে তোমরা? দ্যাখো বাবা, এই একটাই সন্তান আমার…’ বলতে বলতে চোখে তাঁর জল এলো।
মোনালিসা, কোনোদিন জানলে না তুমি, কোনোদিন জানবে না, কী ভালো আমাদের লেগেছিলো, কী সুখী আমরা হয়েছিলাম, সেই সাতাশ সনের বর্ষায়, পুরানা পল্টনে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, সেই জ্বরে ঝড়ে, বৃষ্টিতে থমথমে অন্ধকারে, ছমছমে ছায়ায়। দেড় মাস তুমি শুয়ে ছিলে, দেড় মাস তুমি আমাদের ছিলে। দেড় মাস ধ’রে সুখের স্পন্দন দিনে-রাত্রে কখনো থামল না আমাদের হৃৎপিণ্ডে। তোমার বাবা আপিস যান, ফিরে এসে রোগীর ঘরে উঁকি দিয়েই হাত-পা এলিয়ে শুয়ে পড়েন ইজি-চেয়ারে; তোমার মা-র সারাদিন পায়ের পাতা দাঁড়ায় না, কিন্তু রাত্তিরে আর পারেন না তিনি, রোগীর ঘরেই ক্যাম্পখাটে ঘুমোন, আর সারারাত পালা ক’রে ক’রে জেগে থাকি আমরা—কখনো একসঙ্গে দুজনে, ক্বচিৎ তিনজনেই, বেশির ভাগ একলা একজন। আর তোমাকে নিয়ে এই একলা রাত-জাগায় সুখ আমিই পেয়েছি বেশি—অসিত সারাদিন ছুটোছুটি করেছে সাইকেলে, হিতাংশুও বারবার। সবচেয়ে কাছের বরফের দোকান এক মাইল দূরে, ওষুধের দোকান দুই মাইল, ডাক্তারের বাড়ি সাড়ে তিন মাইল—কোনোদিন অসিত দশবার যাচ্ছে, দশবার আসছে, কতবার ভিজে কাপড় শুকোল তার গায়ে, কোনোদিন রাত বারোটায় হিতাংশু ছুটল বরফ আনতে, সব দোকান বন্ধ, রেলের স্টেশন নিঃসাড়, নদীর ধারে বরফের ডিপোতে গিয়ে লোকজনের ঘুম ভাঙিয়ে বরফ নিয়ে আসতে-আসতে দুটো বেজে গেলো তার, এদিকে আমি আইসব্যাগে জলের পরিমাণ অনুভব করছি বারবার, আর অসিত বাথরুমে বরফের ছোট ছোট ছড়ানো টুকরো দু-হাতে কুড়োচ্ছে। সাইকেলে আমার দখল নেই ব’লে বাইরের কাজ আমি কিছুই প্রায় পারি না, সারাদিন ঘুর-ঘুর করি তোমার মা-র কাছে কাছে, হাতের কাছে এগিয়ে দিই সব, ওষুধ ঢালি, টেম্পারেচার লিখি, ডাক্তার এলে তাঁর ব্যাগ হাতে ক’রে নিয়ে আসি, নিয়ে যাই। তারপর সন্ধ্যা হয়, রাত বাড়ে, বাইরে অন্ধকারের সমুদ্র, সে-সমুদ্রে ক্ষীণ আলো-জ্বলা একটি নৌকোয় তুমি আর আমি চলেছি ভেসে, তুমি তা জানলে না মোনালিসা, কোনোদিন জানবে না। সারাদিন, সারারাত মোনালিসা মূর্ছিতের মতো প’ড়ে থাকে, ভুল বকে মাঝে মাঝে—এত ক্ষীণ-স্বর যে কী বলছে বোঝা যায় না—তবু যে ক’টি কথা আমরা কানে শুনেছি তা-ই যত্ন ক’রে তুলে রেখেছি মনে, একের শোনা কথা অন্য দুজনকে বলাই চাই; কখনো হঠাৎ একটু অবসর হলে তিনজন ব’সে সেই কথা ক’টি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, যেন তিনজন কৃপণ সারা পৃথিবীকে লুকিয়ে তাদের মণি-মুক্তো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে, বন্ধ ঘরে, অন্ধকার রাত্রে। যদি বলেছে ‘উঃ’, সে যেন বাঁশির ফুঁয়ের মতো আমাদের হৃদয়কে দুলিয়ে গেছে; যদি বলেছে ‘জল’, তাতে যেন জলের সমস্ত তরলতা ছলছল ক’রে উঠেছে আমাদের মনে।
এক রাত্রে হিতাংশু বাড়ি গেছে আর অসিত বারান্দায় বিছানায় ঘুমুচ্ছে, আমি জেগে আছি একা। টেবিলের উপর জ্বলছে মোমবাতি, দেওয়ালের গায়ে ছায়া কাঁপছে বড়-বড়, অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ ক’রে ঐ আলোটুকু যেন আর পারছে না; আমিও আর পারছি না ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, ডাকাতের মতো ঘুম আমার হাত-পা কেটে-কেটে টুকরো ক’রে দিলো, মোমের মতোই গলে যাচ্ছে আমার শরীর। যতবার চাবুক মেরে নিজেকে সোজা করছি; লাফিয়ে উঠছে অতল থেকে বিশাল ঢেউ। ডুবতে ডুবতে মনে হ’লো মোনালিসা তুমিও কি এমন করেই যুদ্ধ করছ মৃত্যুর সঙ্গে, মৃত্যু কি এই ঘুমের মতোই টানছে তোমাকে, তবু তুমি আছো—কেমন ক’রে আছো! মনে হ’তেই ঘুম ছুটল। সোজা হ’য়ে বসলাম, তাকিয়ে রইলাম তোমার মুখের দিকে সেই ক্ষীণ আলোয় কাঁপা-কাঁপা ছায়ায় রাত চারটের স্তব্ধ মহান মুহূর্তে। তুমি কি মরবে? তুমি কি বেঁচে উঠবে? কোনো উত্তর নেই। তোমার কি ঘুম পেয়েছে? উত্তর নেই। তুমি ঘুমিয়েছ না জেগে আছো? উত্তর নেই। তবুও আমি তাকিয়ে থাকলাম, মনে হ’লো এর উত্তর আমি পাবই, পাব তোমারই মুখে, তোমার মুখের কোনো একটি ভঙ্গিতে হয়তো—কে জানে—তোমার কণ্ঠেরই কোনো একটি কথায়। আর, আমি অবাক হ’য়ে দেখলাম, আস্তে আস্তে চোখ তোমার খুলে গেলো, মস্ত বড় হ’লো, উন্মাদের মতো ঘুরে ঘুরে স্থির হ’লো আমার মুখের উপর। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল—‘কে?’
আমি তাড়াতাড়ি আইসব্যাগ চেপে ধরলাম।
‘কে তুমি?’
‘আমি।’
‘তুমি কে?’
‘আমি বিকাশ।’
‘ও, বিকাশ। বিকাশ, এখন দিন, না রাত্রি?’
‘রাত্রি।’
‘ভোর হবে না?’
‘হবে, আর দেরি নেই।’
‘দেরি নেই? আমার ঘুম পাচ্ছে, বিকাশ।’
আমি তার কপালে আমার বরফে-ঠাণ্ডা হাত রাখলাম।
‘আহ্, খুব ভালো লাগছে আমার।’
‘আমি বললাম, ‘ঘুমোও।’
‘তুমি চলে যাবে না তো?’
‘না।’
‘যাবে না তো?’
‘না।’
‘আমি তাহলে ঘুমুই, কেমন?’
নিশ্বাস উঠলো আমার ভিতর থেকে, নিশ্বাসের স্বরে বললাম,—‘ঘুমোও, ঘুমোও, আমি জেগে আছি, কোনো ভয় নেই।’
তুমি ঘুমিয়ে পড়লে আর বাইরে, দু-একটা পাখি ডাকল। ভোর হ’লো।
প্রলাপ, জ্বরের প্রলাপ, তবু এটা আমারই থাক। একলা আমার। এই একটা কথা ওদের দুজনেক বলি নি, হয়তো ওদেরও এমন কিছু আছে যা আমি জানি না, আর-কেউ জানে না। তুমি, মোনালিসা, তুমিও জানলে না, জানবে না কোনোদিন।
তারপর একদিন তুমি ভালো হলে। সে তো খুব সুখের কথা, কিন্তু আমরা যেন বেকার হ’য়ে পড়লাম। আর তুমি ভাতটাত খাবার দিন-পনের পরে যে-রবিবারে তোমার মা আমাদের তিনজনকে নিমন্ত্রণ ক’রে খাওয়ালেন, সেদিন আমার অন্তত মনে হ’লো যে এই খাওয়াটা আমাদের ফেয়ারওএল পার্টি।
কিন্তু তা-ই বা কেন? এখনো আমরা যেতে পারি, বসতে পারি কাছে, গ্রামোফোন বাজিয়ে শোনাতে পারি, সে ক্লান্ত হলে পিঠের বালিশটা দিতে পারি ঠিক ক’রে। এদিকে আকাশে কালো মেঘের সঙ্গে সাদা মেঘের খেলা, আর ফাঁকে-ফাঁকে নীলের মেলা, এই ক’রে-ক’রে আশ্বিন যেই এলো, ওঁরা চলে গেলেন মেয়ের শরীর সারাতে রাঁচি।
বাঁধাছাঁদা থেকে আরম্ভ ক’রে নারায়ণগঞ্জে স্টিমারে তুলে দেয়া পর্যন্ত সঙ্গে-সঙ্গে থাকলাম আমরা তিনজন।
ফার্স্ট ক্লাসের ডেকে রেলিং ধরে দাঁড়ানো মোনালিসার ছবিটি যখন চোখের সামনে ঝাপসা হ’লো তখন আমাদের মনে পড়লো যে ওঁদের রাঁচির ঠিকানাটা জেনে রাখা হয়নি আমার ইচ্ছে করছিলো বাড়ি ফিরেই একটা চিঠি লিখে ডাকে দিই, তা আর হ’লো না।
অসিত বললো, ‘ওরই তো আগে লেখা উচিত।’
‘তা কি আর লিখবে?’ একটু হতাশভাবেই বললো হিতাংশু।
‘কেন লিখবে না, না-লেখার কী আছে।’
কী আছে কে জানে, কিন্তু কুড়ি দিনের মধ্যেও কোনো চিঠি এলো না। এলো হিতাংশুর বাবার নামে মনি-অর্ডার, বাড়ি-ভাড়ার টাকা। তাই থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে আমরা চিঠি লিখব স্থির করলাম। ও লেখে নি বলে আমরাও না-লিখে রাগ দেখাব, এটা কোনোরকম যুক্তি বলেই মনে হলো না আমাদের। অসুখ থেকে উঠে গেছে, হয়তো এখনো ভালো ক’রে শরীর সারেনি—কেমন আছে সে খবরটা আমাদেরই তো নেয়া উচিত। কিন্তু চিঠিতে পাঠে কী লিখব? আপনি লিখব, না তুমি? মুখে ও অবশ্য আমাদের তুমিই বলেছে, আমরাও তা-ই, কিন্তু কতটুকু কথাই বা এ পর্যন্ত বলেছি আমরা—এতখানি কথা নিশ্চয়ই বলি নি যার জোরে কালির আঁচড়ে জ্বলজ্বলে একটা তুমি লিখে ফেলা যায়। তাছাড়া, কী লিখবই বা চিঠিতে? কেমন ভালো তো? এতেই তো সব কথা ফুরিয়ে গেলো। আমরা কেমন আছি, কী করছি, সে-সব লিখলে তো কতই লেখা যায়—কিন্তু মোনালিসা কি আমাদের খবর জানতে ব্যস্ত?
অনেকক্ষণ ধ’রে জটলা ক’রেও কোনো মীমাংসা যখন হ’লো না, তখন ওরা আমাকেই বললো চিঠিখানা রচনা ক’রে দিতে। আমি কবিতা-টবিতা লিখি, তাই।
সে-রাত্রেই লণ্ঠনের সামনে ঘামতে ঘামতে আমি লিখে ফেললাম :
সুচরিতাষু,
ভেবেছিলাম একখানা চিটি আসবে, চিঠি এলো না। ভাবতে-ভাবতে একুশ দিন কেটে গেলো। খুবই ভালো লাগছে বুঝি রাঁচিতে? অবশ্য ভালো লাগলেই ভালো, আমরা তাতেই খুশী। তারা-কুটিরের একতলা বন্ধ, পুরানা পল্টন তাই অন্ধকার। ওখানে পেট্রোম্যাক্স জ্বলত কিনা রোজ সন্ধ্যায়।
বসে বসে রাঁচির ছবি দেখছি আমরা। পাহাড়, জঙ্গল, লাল কাঁকরের, কালো-কালো-সাঁওতাল। হাসি, আনন্দ, স্বাস্থ্য। সত্যি, কী বিশ্রী অসুখ গেলো—আর যেন কখনো অসুখ না ক’রে।
কারো কোনো অসুখ না ক’রেও এমন কি হয় না যে আমাদের খুব খাটতে হয়? সত্যি, শুয়ে-ব’সে আর সময় কাটে না। চিঠি পেলে আবার আমাদের চিঠি লিখতে হবে, কিছু কাজ তবু জুটবে আমাদের।
মাসিমা মেসোমশায়কে প্রণাম।
আপনি তুমি দুটোই বাঁচিয়ে এর বেশি পারলাম না। এটুকুতেই রাত তিনটে বাজল। তাকিয়ে দেখি, কাটাকুটির ফাঁকে-ফাঁকে এই ক’টি কথা যেন কালো জঙ্গলে ঝিকিমিকি রোদ্দুর। বার-বার পড়লাম; মনে হ’লো বেশ হয়েছে, আবার মনে হ’লো ছি-ছি, ছিঁড়ে ফেলি এক্ষুনি। ছিঁড়ে ফেললামও, কিন্তু তার আগ ভালো একটি কাগজে নকল ক’রে নিলাম, আর পরদিন তিনজন বসিয়ে দিলাম যে যার নাম সই, চোখ বুজে ছেড়ে দিলাম ডাকে।
ঢাকা থেকে রাঁচি, রাঁচি থেকে ঢাকা। চারদিন, পাঁচদিন—আচ্ছা ছ-দিন। না, চিঠি নেই। সন্ধ্যায় কুয়াশা, একটু একটু শীত; চিঠি নেই। শিউলি ফুরিয়ে স্থলপদ্ম ফুটল; চিঠি নেই।
চিঠি এলো শেষ পর্যন্ত, হিতাংশুর নামে শীর্ণ একটা পোস্টকার্ড, লিখেছেন ওর মা। অনেকটা এই রকম :
কল্যাণীয়েষু,
হিতাংশু, অসিত, বিকাশ, তোমরা তিনজনে আমাদের বিজয়ার আশীর্বাদ জেনো। আমাদের রাঁচির মেয়াদ শেষ হ’লো, শিগগিরই ফিরব। ইতিমধ্যে, হিতাংশু তুমি যদি আমাদের ঘরগুলি খুলিয়ে তোমাদের চাকর দিয়ে ঝাঁটপাট করিয়ে রাখো, তাহলে বড় ভালো হয়। চাবি তোমার বাবার কাছে।
আশা করি ভালো আছো সকলে। তরুর শরীর এখন বেশ ভালো হয়েছে, মাঝে মাঝে সে তোমাদের কথা ব’লে। ইতি—তোমাদর মাসিমা।
মাঝে মাঝে আমাদের কথা ব’লে! আর আমাদের চিঠি? পোস্টকার্ডটি তন্ন তন্ন ক’রে খুঁজেও কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলো না যে চিঠিটা পৌঁছেছিলো। কি হ’লো চিঠির? কিন্তু সে কথা বেশিক্ষণ ভাববার সময় কই আমাদের, তক্ষুনি লেগে গেলাম কাজে। একদিনের মধ্যেই তারা-কুটিরের একতলাকে আমরা এমন ক’রে ফেললাম যে মেঝেতে মুখ দেখা যায়। কয়েকদিন পরে আর-একটি পোস্টকার্ড : ‘রবিবার ফিরছি, স্টেশনে এসো।’ শুধু স্টেশনে। আমরা ছুটলাম নারায়ণগঞ্জে।
আ, কী সুন্দর দেখলাম মোনালিসাকে, কচিপাতার রঙের শাড়ি পরনে, লাল পাড়, লালচে মুখের রং, একটু মোটা হয়েছে, একটু যেন লম্বাও। পাছে কাছে দাঁড়ালে ধরা প’ড়ে যে সে আমাকে মাথায় ছাড়িয়ে গেছে, আমি একটু দূরে দূরে থাকলাম, হিতাংশু ছুটোছুটি ক’রে বরফ লেমনেড কিনতে লাগল, আর অসিত কুলিকে ঠেলে দিয়ে বড়-বড় বাক্স-বিছানা হাই-হাই ক’রে তুলতে লাগল গাড়িতে।
মাসিমা বললেন, ‘তোমরা এ-গাড়িতেই এসো।’
‘না, না, সে কী কথা, আমরা-আমরা এই পাশের গাড়িতেই—’
‘আরে এসো না’—ব’লে দে-সাহেব অসিতের পিঠের উপর হাত রাখলেন।
নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা : মনে হ’লো আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়টি এতকাল এই পঁয়তাল্লিশটি মিনিটের জন্যই অপেক্ষা ক’রে ছিলো। ফার্স্ট ক্লাসের গদিকে অবজ্ঞা ক’রে আমরা বসলাম বাঙ্-বিছানার উপর; তাতে একটা সুবিধে এই হ’লো যে একসঙ্গে সকলকেই দেখতে পেলাম—দেখলাম মোনালিসা খুশী, ওর মা খুশী। বাবা খুশী, দেখতে-দেখতে আমরাও খুশীতে ভ’রে গেলাম; এতদিন যা বাধো-বাধো ছিলো তা সহজ হ’লো, এতদিন যা ইচ্ছে ছিলো তা মূর্ত হ’লো—রীতিমতো কলরব করতে-করতে চললাম আমরা; এতবড় রেলগাড়িটা যেন আমাদের খুশীর বেগেই চলেছে। মোনালিসা নাম ধ’রে-ধ’রে ডাকতে লাগল আমাদের—কত তার কথা, কত গল্প—আর গাড়ি যখন ঢাকা স্টেশনের কাছাকাছি, কোনো-এক ঝর্নার বর্ণনা দিচ্ছে সে, হঠাৎ আমি ব’লে উঠলাম, ‘আমাদের চিঠি পেয়েছিলে?’
‘তোমাদের চিঠি, না তোমার চিঠি?’
আমি একটু লাল হ’য়ে বললাম, ‘জবাব দাও নি যে?’
‘এতক্ষণ ধ’রে তো সেই জবাবই দিচ্ছি। বাড়ি গিয়ে আরও দেবো।’
মিথ্যো বলে নি মোনালিসা। স্বর্গের দরজা হঠাৎ খুলে গেলো আমাদের, আমরা তিনজন আমরা চারজন হ’য়ে উঠলাম।
তারপর একদিন মাসিমা আমাদের ডেকে বললেন, ‘একবার তোমরা তরুর জন্য খেটেছ, আর একবার খাটতে হবে। ঊনতিরিশে অঘ্রাণ ওর বিয়ে।’
ঊনতিরিশে! আর দশ দিন পরে!
ছুটে গেলাম ওর কাছে, বললাম, ‘মোনালিসা, এ কী শুনছি!’
ভুরু কুঁচকে বললো, ‘কী? কী বললে?’
গোপন নামটা হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় আমি একটু থমকে গেলাম, কিন্তু একবার যখন বেরিয়েই গেছে তখন আর ভয় কী! মরিয়া হলে মানুষের যে সাহস হয়, সেই সাহসের বশে আমি সোজা তাকালাম ওর চোখের দিকে, চোখের ভিতরে—যা যা আগে আমি কখনো করি নি—বেগুনি-বেগুনি কালো রঙের ওর চোখ, একফোঁটা হীরের মতো চোখের মণি—তাকিয়ে থেকে আবার বললাম, ‘মোনালিসা।’
‘মোনালিসা’ সে আবার কে?’
‘মোনালিসা তোমারই নাম’, বললো অসিত, ‘জানো না?’
‘সে কী?’
হিতাংশু বললো, ‘আর কোনো নামে আমরা ভাবতেই পারি না তোমাকে।’
‘মজা-তো—’ কৌতুকের রং লাগল ওর মুখে, মিলিয়ে গেলো, পলকের জন্য ছায়া পড়লো সেখানে, যেন একটি ক্ষণিক বিষাদের মেঘ আস্তে ভেসে গেল মুখের উপর দিয়ে। একটু তাকিয়ে রইল, চোখের পাতা দুটি চোখের উপর নামল একবার।
হঠাৎ, মুহূর্তের জন্য—কী কারণে বুঝলাম না—আমাদের একটু যেন মন-খারাপ হ’লো, কিন্তু তখনই তা উড়িয়ে দিল হাসির হাওয়া, আমাদের কথায় লাগল ঠাট্টার বুড়বুড়ি।
‘কী শুনছি? মোনালিসা, কী শুনছি?’
‘কী শুনছ বলো তো?’ ব’লে আঁচলে মুখ চেপে খিলখিল ক’রে হেসে পালিয়ে গেলো।
বর এলো বিয়ের দু’দিন আগে কলকাতা থেকে। ধবধবে ফর্সা, ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবি পরনে, কাছে দাঁড়ালে সূক্ষ্ম একটি সুগন্ধে মন যেন পাখি হ’য়ে উড়ে যায়। দেখে আমরা মুগ্ধ। হিতাংশু বারবার বলতে লাগল—’হীরেন বাবু কী সুন্দর দেখতে।’
অসিত জুড়ল—‘ধুতির পাড়টা!’
‘পা দুটো!’ বলে উঠলো হিতাংশু। ‘অমন ফর্সা পা না-হলে কি আর ও-রকম ধুতি মানায়!’
আমি ফস্ করে বললাম, ‘যা-ই বলো, ঠোঁটের কাছটা একটু বোকা-বোকা।’
‘কী! বোকা-বোকা!’ অসিত চেঁচিয়ে উঠলো, কিন্তু চিৎকার বেরোল না, কারণ লোকজন নিয়ে চ্যাঁচামেচি ক’রে-ক’রে বিয়ের অনেক আগেই সে-গলা ভেঙে ব’সে আছে। রেগে যাওয়া বেড়ালের মতো ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ ক’রে বললো, ‘এমন সুন্দর দেখেছ কখনো!’
‘মোনালিসার মতো তো নয়!’ আমি আমার গোঁ ছাড়লাম না।
‘একজন কি আর-একজনের মতো হয় কখনো! খুব মানিয়েছে দু’জনে। চমৎকার!’ ব’লে অসিত লাফিয়ে সাইকেলে উঠে বোঁ ক’রে কোথায় যেন চলে গেলো। বিয়ের সমস্ত ভারই তার উপর, তর্ক করার সময় কোথায়।
বিয়ের দিন শানাইয়ের শব্দে রাত থাকতেই আমার ঘুম ভাঙল। চোখ মেলেই মনে পড়লো সেই আর-একটি শেষ-রাত্রি, যখন মৃত্যুর হাত থেকে—তা-ই মনে হয়েছিলো তখন—মোনালিসাকে আমি ফিরিয়ে এনেছিলাম। সেদিন অন্ধকারের ভিতর থেকে একটু একটু ক’রে আলো বেরিয়ে আসা দেখতে-দেখতে যে আনন্দে আমি ভেসে গিয়েছিলাম, সেই আনন্দ ফিরে এলো আমার বুকে, গা কাঁটা দিয়ে উঠলো, শানাইয়ের সুরে চোখ ভ’রে উঠলো জলে। আর শুয়ে থাকতে পারলাম না, তারা-ভরা আকাশের তলায় দাঁড়ালাম এসে। শুনতে পেলাম বিয়েবাড়ির সাড়াশব্দ, শাঁখের ফুঁ—কাছে গেলাম। মনে হ’লো আর একবার যদি দেখতে পাই, এই ভোর হবার আগের মুহূর্তে, যখন আকাশ ঘোষণা করছে মধ্যরাত্রি আর হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ভোর—এই আশ্চর্য অপার্থিব সময়ে একটু দেখতে পাই যদি। কিন্তু না—গায়ে-হলুদ হচ্ছে, কত-কত অচেনা মেয়ে ঘিরে আছে তাকে, কত কাজ, কত সাজ—এর মধ্যে আমি তো তাকে দেখতে পাব না। বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতরকার চলাফেরা, কথাবার্তা শুনতে লাগলাম, আর সব ছাপিয়ে, সব ছাড়িয়ে শানাইয়ের সুর ঝরল, আমার চোখের সামনে কাঁপতে-কাঁপতে তারার ঝাঁক মিলিয়ে গেলো, ফুটে উঠলো মাঠে মাঠে গাছপালার চেহারা, মাটির অবয়ব, পৃথিবীতে আর একবার ভোর হলো।
সেদিনে অসিতের গলা একেবারেই ভেঙে গিয়ে নববধূর মতো ফিসফিসে হ’লো। এত ব্যস্ত সে, আমাকে যেন চেনেই না। হিতাংশুও ব্যস্ত, ব্যস্ত এবং একটু গর্বিত, কেননা বর সদলে বাসা নিয়েছেন তাদেরই বাড়ির দুটো ঘরে, একতলা দোতলায় দূতের কাজ করতে-করতে সে স্যান্ডেল ক্ষইয়ে ফেলল। আমি একবার হিতাংশুকে, একবার অসিতকে সাহায্য করার চেষ্টা করলাম সারাদিন ভ’রে, কিন্তু আমার নিজের মনে হ’লো না বিশেষ-কোনো কাজে লাগছি, আর শেষ পর্যন্ত যখন বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে কনেকে সাতপাক ঘোরাবার সময় এলো, তখনও আমি এগিয়ে গেলাম, কিন্তু আমাকে ঠেলে দিয়ে অসিত আর হিতাংশুই পিঁড়ি তুলল, দু’হাতে দু’জনের গলা জড়িয়ে ধ’রে ও সাত পাক ঘুরল, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম।
বিয়ের পরদিন থেকেই আমরা তিনজন হীরেন বাবুর চাকর বনে গেলাম। তাঁর মতো সুন্দর কেউ না, তাঁর মতো বিদ্যেবুদ্ধি কারো নেই, তাঁর মতো ঠাট্টা কেউ করতে পারে না। অন্য পুরুষদের বাঁদর মনে হ’লো তুলনায়—আমারও আর মনে হ’লো না যে তাঁর ঠোঁটের কাছটা একটু বোকা-বোকা। এমনকি, আমি চেষ্টা করতে লাগলাম তাঁর মতো ক’রে বসতে, দাঁড়াতে, হাঁটতে, হাসতে, কথা বলতে; ওরা দু’জনও তা-ই করলো, আবার তা দেখে হাসি পেলো আমার, হয়তো প্রত্যেকেই আমরা অন্য দু’জনের চেষ্টা দেখে হেসেছি মনে-মনে, যদিও মুখে কেউ কিছু বলি নি।
একদিন দুপুরবেলা হীরেনবাবুর কাছে খুব একটা মজার গল্প শুনছি, তিনি একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, ‘দ্যাখো তো ভাই, তরু গেলো কোথায়।’
‘ডেকে আনব?’ ব’লে আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম।
দক্ষিণের বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়ে ব’সে মোনালিসা চুল আঁচড়াচ্ছে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভুলে গেলাম। হঠাৎ যেমন নতুন লাগল তাকে, একটু অন্যরকম সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, পরনে কড়কড়ে শাড়ি, কানে হাতে গলায় চিকচিকে গয়না, আর কেমন একটা গন্ধ দিচ্ছে গা থেকে—হীরেনবাবুর সেন্টের গন্ধ না, নতুন ফার্নিচারের মদ-মদ গন্ধ না, চুলের তেল কি মুখের পাউডারেরও না—আমার মনে হ’লো এই সমস্ত মিলিত গন্ধের যেটা নির্যাস, সেটাই ভর করেছে মোনালিসার শরীরে। জোরে নিশ্বাস নিলাম কয়েকবার, মাথা যেন ঝিমঝিম ক’রে উঠলো।
চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, ‘কী?’
‘কিছু না’—সঙ্গে সঙ্গে কাজের কথাটা মনে পড়লো, ‘হীরেনবাবু ডাকছেন তোমাকে।’
আমার কথাটা যেন শুনতেই পেলো না মোনালিসা, নিশ্চিন্তে চুলই আঁচড়াতে লাগল।
‘শুনছ না কথা! হীরেনবাবু ডাকছেন তোমাকে।’
‘ডাকছেন তো হয়েছে কী। উনি ডাকলেই যেতে হবে?’
‘বাঃ—!’
চিরুনি থামিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো—‘আর কী—চলেই তো যাব শিগগির।’
আমি বললাম, ‘কত ভালো লাগবে তোমার কলকাতায় গিয়ে—ঢাকা কি একটা জায়গা!’
‘ঢাকা খুব ভালো।’ ঘাড় বেঁকিয়ে বাইরের দিকে তাকালো, একটু, শীতের দুপুরের সবুজ-সোনালি মাঠের দিকে। সেদিকে তাকিয়েই আবার বললো, ‘তোমরা আমাকে মনে রাখবে, বিকাশ?’
আমি ব্যস্ত হ’য়ে বললাম, ‘আর কথা না। চলো এখন।’
‘দেখছো না চুল আঁচড়াচ্ছি। বলো গিয়ে এখন যেতে পারবো না।’
কথা শুনে প্রায় ভড়কে গিয়েছিলাম, কিন্তু একটু পরেই মোনালিসা উঠলো, তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও এলাম ঘরে। এসেই বললাম, ‘তারপর? সেই লোকটার কী হ’লো, হীরেনবাবু?’
কিন্তু হীরেনবাবুর গল্প বলার উৎসাহ দেখি মিইয়ে গেছে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি, আর মোনালিসা চেয়ারে ব’সে টেবিলের কাপড় খুঁটতে লাগল।
আমি পীড়াপীড়ি করলাম, ‘বলুন না কী হ’লো!’
‘এখন থাক।’
আমি খাটে ব’সে একটি ইংরেজি বইয়ের পাতা উল্টিয়ে বললাম, ‘এটা পড়েছি, ভারি মজার বই।’
হীরেনবাবু হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আর-একটি বই টেনে নিয়ে বললেন, ‘এ-বইটাও ভারি মজার। এক কাজ করো তুমি—এটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে প’ড়ে ফ্যালো, আমি চট ক’রে একটু ঘুমিয়ে নিই। কেমন?’ বলতে-বলতে তিনি একেবারে উঠে দাঁড়ালেন।
আর কথা না-ব’লে আস্তে বেরিয়ে এলাম আমি, পিঠ দিয়ে অনুভব করলাম ও-ঘরের দরজা বন্ধ হ’য়ে গেলো। বাড়ি গেলাম না; বারান্দায় যেখানে ও ব’সেছিলো ঠিক সেখানটায় ব’সে পড়লাম। ওর চুলের গন্ধমাখা চিরুনিটা সেখানেই প’ড়ে ছিলো, হাতে তুলে নিয়ে দাঁতগুলির উপর আস্তে আস্তে আঙুল চালাতে লাগলাম, বার-বার, বার-বার।
আরো একদিন, আরো একদিন। যাবার দিন এলো, পেছোল, আর-একটা একটা দিন শুধু; তারপর চলে গেলো।
চিঠি এলো এবার, তিনজনের কাছে একখানা, চিঠি, মোটা নীল খামে, আমার নামে! তিনজনের হ’য়ে জবাব লিখলাম, আমি, একটু লম্বাই হ’লো, সেই সঙ্গে একটা কবিতাও লিখে ফেললাম, সেটা অবশ্য পাঠালাম না। চিঠি বন্ধ হ’য়ে গেলো শিগগিরই, তারপর শুধুই কবিতা লিখতে লাগলাম, দেখতে দেখতে খাতা ভ’রে উঠলো!
মাসিমার কাছে খবর পাই সবই। ভালো আছে ওরা, খুব ভালো আছে। হীরেন গাড়ি কিনেছেন, সেদিন ওরা আসানসোল বেড়িয়ে এলো। কলকাতায় কথা-বলা সিনেমা দেখাচ্ছেন, টোম্যাটোর সের এক পয়সা, তবে শীত কমে গেছে, হঠাৎ অসুখ-বিসুখ দেখা না দেয়। আর-একটু গরম পড়লেই ওরা চলে যাবে দারজিলিং।
না-দেখা দারজিলিং-এর ছবি দেখতে লাগলাম, মনে-মনে, কিন্তু সে-ছবি মুছে দিয়ে মাসিমা একদিন বললেন, ‘ওরা তো আসছে।’
আসছে! এখানে! ঢাকায়। দারজিলিং-এর কী হ’লো? আমাদের নীরব প্রশ্নের উত্তরে বললেন, ‘শরীরটা খারাপ হয়েছে ওর, আমার কাছেই থাকবে এখন।’
‘কী? অসুখ করেছে আবার?’ চমকে উঠলাম তিনজনে।
‘না, অসুখ ঠিক না, শরীরটা ভালো নেই আর কি’, মাসিমা মৃদু হাসলেন।
খুব খারাপ লাগল। খারাপ লাগল মাসিমার কথা শুনে, হাসি দেখে। শরীর ভালো না, অথচ অসুখও না—এ আবার কী-রকম কথা? আর মাসিমা কেমন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ,—যেন খুশীই হয়েছেন খবর শুনে। রীতিমতো রাগ হ’লো মনে মনে।
ওরা পৌঁছোবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা তিন মূর্তি গিয়ে হাজির হলাম। মোনালিসা সোফায় ব’সে আছে একটু এলিয়ে, হাতে সিগারেটের টিন। চকিতে আমরা তিনজন মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলাম—হীরেনবাবু কি সিগারেট ধরিয়েছেন ওকে?
আমাদের দেখে ফিকে একটু হাসলো। কথা বললো না।
‘কেমন আছো মোনালিসা?’ আমরা চেষ্টা করলাম স্ফূর্তির সুর লাগাতে।
সিগারেটের টিনটা মুখের কাছে এনে তার সঙ্গে একবার মুখ ঠেকিয়ে ডালা বন্ধ ক’রে বললো, ‘এই—’
‘তোমার নাকি অসুখ?’
সে-কথার কোনো জবাব না-দিয়ে বললো, ‘তোমাদের কী খবর?’ তারপর আস্তে আস্তে এটা-ওটা গল্প করতে লাগল, আর সিগারেটের টিনটা মুখে তুলতে লাগল ঘন ঘন।
হীরেনবাবু ঘরে এসে ব্যস্তভাবে বললেন, ‘তরু এখন কেমন আছো?’
ক্লান্ত চোখ তুলে বললো, ‘ভালো।’
‘তুমি বরং একটু শোও।’
‘না, এই বেশ আছি।’
‘এই যে তোমরা এসেছো দেখছি। তরু তো এদিকে—’ হঠাৎ থেমে গেলেন হীরেনবাবু।
‘হয়েছে কী ওর?’
‘হয় নি কিছু, তবে…’
তবে কী? ওর কী এমন সাংঘাতিক কোনো অসুখ করেছে যা কারো কাছে বলাও যায় না? আর ও যেন কেমন হ’য়ে গেছে, যেন আধ-মরা, আস্তে কথা ব’লে, একভাবে স্থির হ’য়ে ব’সে থাকে, হাসি পেলে ভালো ক’রে হাসেও না। মায়েদের মুখে শুনেছি যে বিয়ের পরে মেয়েদের শরীর আরো ভালো হয়, কিন্তু আমাদের মোনালিসার নাকি এই হ’লো?
ছোট একটা প্লেট হাতে ক’রে মাসিমা এসে বললেন, ‘এটা একটু মুখে দিয়ে দ্যাখ তো?’
‘কী, মা?’
‘দ্যাখ না—’ ব’লে তিনিই আঙুল দিয়ে মুখে গুঁজে দিলেন।
‘না, না, আর না—’, মোনালিসার মুখে কষ্টের রেখা ফুটে উঠলো, গলার কাছটায় হাত রেখে মুখ নিচু করলো সে।
বেরিয়ে এসে খানিকক্ষণ নিঃশব্দ হাঁটলাম আমরা, মন বিষণ্ন খুবই। হঠাৎ অসিত বললো, ‘ও বার-বার থুতু ফেলছিলো সিগারেটের টিনে।’
‘যাঃ!’ আমি আঁতকে উঠলাম।
‘সত্যি! আমি দেখলাম!’
হিতাংশু বললো, ‘তা হলে এটাই বোধহয় ওর অসুখ।’
‘অসুখ না’, অসিত গম্ভীরভাবে বললো, ‘ওর ছেলে হবে।’
শুনে হিতাংশুটা খুকখুক ক’রে হেসে উঠলো।
‘হাসছো কেন?’—আমি রেগে গেলাম—‘হাসবার কী আছে এতে?’
অসিত বললো, ‘ঐ জন্যেই তো টক এনে দিলেন মাসিমা। এ-রকম হলে টক খেতে ভালো লাগে।’
‘তুমি সবই জানো!’ রাগে গর্জে উঠলাম আমি।
‘হ’লো কী তোমার?’ অসিত যেন সকৌতুকে আমার দিকে তাকালো।
‘যাও! কিছু ভালো লাগছে না আমার, আমি বাড়ি যাই।’ ওদের ত্যাগ ক’রে একা ফিরে এলাম বাড়িতে, বেলা শেষের আলোয় একটা বই খুলে পড়তে ব’সে গেলাম।
হীরেনবাবু ফিরে গেলেন দু’দিন পরেই। দুপুরবেলা গাড়ি। ঘোড়ার গাড়িতে মাল তোলা হ’লো : হীরনেবাবু উঠতে গিয়ে থমকালেন। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, ‘কিছু ফেলে এসেছেন, নিয়ে আসবো?’
‘না, না, আমি যাচ্ছি।’
তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে গেলেন তিনি, ফিরে এসে কোনোদিকে না তাকিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। চাবুকের শব্দ হ’লো। অসিত সাইকেলে উঠলো—স্টেশনে যাবে সে। হিতাংশু গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, ‘কবে আসবেন আবার?’
‘আসবো—তোমরা দেখো ওকে’, ব’লে হীরেনবাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমার মনটা হু হু ক’রে উঠলো।
কী স্তব্ধ সেই দুপুরবেলা, কী-রকম ছবির মতো সুন্দর, সেই উনিশ-শো-আটাশ সনে, পুরানা পল্টনের ফাল্গুন মাসে! ঘোড়ার গাড়ি আর অসিতের সাইকেল, ছোট হ’তে-হ’তে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হ’লো; আমি আর হিতাংশু ভেতরে এলাম। বালিশে মুখ গুঁজে মোনালিসা ফুলে ফুলে কাঁদছে।
‘মোনালিসা!’
‘শোনো, কথা শোনো।’
‘হীরেনবাবু আবার তো আসবেন—’
‘এরপর ওঁকে আর যেতেই দেব না আমরা!’
‘আর না—আর কেঁদো না, মোনালিসা, তোমার পায় পড়ি।’ থামল না কান্না। আমি মেঝেতে ওর কাছে হাঁটু ভেঙে ব’সে পড়লাম, ওর মাথায় হাত রেখে গুনগুন ক’রে বলতে গেলাম, ‘আর না, আর কাঁদে না, একটু থামো, একটু চুপ ক’রো মোনালিসা!’ হঠাৎ গলা ভেঙে গিয়ে আমিও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।
একটু পরে মোনালিসা আমাকে ঠেলা দিয়ে বললো, ‘এই—কাঁদছ কেন? বোকা!’ আমি দু’হাতে মুখ ঢেকে থাকলাম, আমাকে চুলে ধ’রে ঝাঁকানি দিয়ে আবার বললো, ‘পুরুষমানুষ—কাঁদতে লজ্জা ক’রে না। থামো এক্ষুনি!’
আমি হাত সরিয়ে ভেজা চোখে তাকালাম। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সুখে আমার বুক কেঁপে উঠলো, তারপর সারাদিন ধ’রে একটু একটু কাঁপল, রাত্রে ঘুমের মধ্যেও ভুলতে পারলাম না।
আমরা তিনজন ওকে ঘিরে রইলাম। ও যাতে ভালো থাকে, কখনো মন খারাপ না ক’রে। হঠাৎ এক-একটা অদ্ভুত জিনিষ ওর খেতে ইচ্ছা ক’রে, অসিত শহর ঢুঁড়ে তা জোগাড় ক’রে আনে। দেখেই ওর ইচ্ছে চলে যাবে, জানা কথা; কবে আবার নতুন ইচ্ছে হবে সেই আশায় থাকি আমরা। আর যদি কখনো একটু খায়, খেয়ে ভালো ব’লে, তাহলে তো কথাই নেই—আহ্লাদে আমরা হাবুডুবু।
হীরেনবাবুর চিঠি আসতে দেরি হলেই আমরা বলি, উনি হঠাৎ এসে অবাক ক’রে দেবেন ব’লেই চিঠি লিখছেন না। কথাটা ঠিক নয় জেনেও প্রতিবারেই মোনালিসার মুখ উজ্জ্বল হ’য়ে ওঠে। আমরা চুপ ক’রে উপভোগ করি।
হীরেনবাবু এলেন তিন মাস পরে। ততদিন ওর শরীরটা অনেকটা সেরেছে, খায়, বেড়ায়, ফেরিওলা ডেকে কাপড় কেনে, চেহারাও ভারী হয়েছে একটু। এবারে দিন দশেক থাকলেন তিনি, তারপর পুজোর সময় এসে এক মাস কাটালেন।
ততদিন ওর শরীর আবার খারাপ হচ্ছে। ডাক্তার আসছেন ঘন-ঘন, ওষুধ দিচ্ছেন, কিন্তু যা শুনি তাতে মনে হয় কিছুই উপকার হচ্ছে না। কী কষ্ট জানি না, বুঝি না, শুধু চোখে দেখতে পাই;—চোখে কালি পড়েছে, দু’টো কথা বললেই হাঁপিয়ে প’ড়ে, মুখটা এক-এক সময় নীল হ’য়ে যায়। আমরা কাছে কাছে ঘুরঘুর করি, শুয়ে থাকলে হাওয়া করি হাতপাখায়, কখনো একটু ভালো দেখলে হাসি-ঠাট্টায় ভোলাতে চাই—কিছুই পারি না।
একদিন আমি বললাম, ‘বাবর নিয়েছিলেন হুমায়ুনের অসুখ, ও-রকম পারলে বেশ হ’তো।’
অসিত হো হো ক’রে হেসে উঠলো—’আর যাই পারো, ওর এ-অসুখটা তুমি নিতে পারবে না!’
লাল হ’য়ে বললাম, ‘অসুখ না, অসুখের কষ্ট।’
হিতাংশু বললো, ‘কী কষ্ট, সত্যি! সারারাত নাকি পায়চারি ক’রে—ঘুমোতে পারে না, শুতেও নাকি কষ্ট হয়।’
অসিত বললো, ‘হবে না, দেখতে কীরকম হয়েছে দেখেছ!’
আমি ঝাঁঝিয়ে উঠে বললাম, ‘কীরকম আবার হবে! সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর।’
‘যত সুন্দরই হোক, এই শেষের সময়টা…’
আর-এক পরদা গলা চড়িয়ে বললাম, ‘এই সময়টাই তো সবচেয়ে সুন্দর!’
সত্যিই তাই, আমার চোখে সত্যিই তা-ই দেখলাম। দিন যত কাটল, তত ওকে আরো বেশি সুন্দর দেখলাম আমি, ওর সমস্ত শরীর এক অসহ্য সৌন্দর্যে ভরপুর হ’য়ে উঠলো আমার চোখে। একদিন ওকে না-ব’লে পারলাম না সে-কথা। আগের বছর যেদিনে ওরা রাঁচি থেকে ফিরেছিলো, যেদিন রেলগাড়ির একটা ছোট কামরায় সমস্ত স্বর্গ ধ’রে গিয়েছিলো, ঠিক সেইরকম একটি শীতের আমেজ-লাগা দিনে হঠাৎ ও বললো, ‘বিকাশ তোমার হয়েছে কী বলো তো? বড্ড আজকাল তাকিয়ে থাকো আমার দিকে!’
আমি একটুও লজ্জিত না হ’য়ে জবাব দিলাম, ‘তুমি আজকাল খুব সুন্দর হয়েছ কি না, তাই।’
‘আগে বুঝি সুন্দর ছিলাম না?’
‘এখনকার মতো না!’
‘তাই বুঝি?’ মোনালিসা ভুরু কুঁচকে বাইরে মাঠের দিকে তাকালো। একটু চুপ ক’রে থেকে বললো, ‘সত্যি আমাকে ভালোবাসো তোমরা। কিন্তু ও-রকম ক’রে আর তাকিয়ো না, ভারি অসুবিধে লাগে আমার।—ইস্, কী রোদ!’
আমি উঠে সামনের জানালাটা ভেজিয়ে দিলাম।
‘একটু ঘুমিয়ে নিই কেমন?’
পায়ের কাছে একখানা চাদর ছিলো, ভাঁজ-করা, খুলে গায়ের উপর ছড়িয়ে দিতে-দিতে বললাম, ‘আজকাল তুমি বেশ ভালো আছো, না?’
‘আমি তো ভালোই আছি।’
ওর মুখে দেখলাম সাহসের সঙ্গে আশা, আশার সঙ্গে ভয়, ভয়ের সঙ্গে ধৈর্য। পায়ের পাতা দুটির উপর থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে বললাম, ‘হীরেনবাবু চলে গেলেন কেন?’
‘বা রে! ওর বুঝি কাজকর্ম নেই?’
‘কবে আসবেন আবার?’
‘আসবেন সময়মতো।’
‘কী দরকার ছিলো যাবার—আমার মোটেও ভালো লাগে না!’
‘হয়েছে হয়েছে, আর সর্দারি করতে হবে না’—বলে পাশ ফিরে চোখ বুজল। বোজা চোখেই ব’লে নিলো, ‘আমি কিন্তু ঘুমোলাম’, এবং বলবার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লো। আহা, রাত্তিরে ঘুমোতে পারে না, কত ক্লান্তি ওর শরীরে! মনে-মনে বললাম—কার কাছে বললাম জানি না—ওর ভালো হোক, ওর ভালো হোক।
রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনে হ’লো ও হয়তো এতক্ষণ ছটফট করছে কষ্টে, উঠে পায়চারি করছে ঘরের মধ্যে, আর বাইরে শেয়াল-ডাকা অন্ধকার, আর আকাশে এখনো সাত-আট ঘণ্টা রাত্রি। কেন আমি কিছু করতে পারি না, কেন এক্ষুনি যেতে পারি না ওর কাছে, কোনো অলৌকিক উপায়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি না ওকে? চোখের উপর কষ্ট দেখতে হবে, কিছু করা যাবে না, এই কি মানুষের ভাগ্য? সত্যি কি আমাদের হাত-পা বাঁধা, কোনো উপায় নেই? ভাবতে ভাবতে ঘুম ছুটল চোখের, কবিতার লাইন মনে এলো, উঠে বসতেই চোখে পড়লো ছায়া-ছায়া জ্যোৎস্না ফুটেছে বাইরে, আমার জানালা দিয়ে আবছা দেখা যাচ্ছে তারা-কুটির স্বপ্নের মতো। বেশিক্ষণ তাকালাম না, লণ্ঠন জ্বেলে কেরোসিনের গন্ধে আর মশার কামড়ে ব’সে ব’সে কবিতা বানাতে লাগলাম।
রোজ হ’তে লাগল এ-রকম, আমার রাত্রি থেকে ঘুম প্রায় চলে গেলো। আমিও জেগে আছি ওর সঙ্গে-সঙ্গে, আমি ওর প্রহরী, সকল দুঃখ থেকে আমি বাঁচাব ওকে—এ কথা ভাবতে-ভাবতে দেবতা মনে হ’লো নিজেকে, কবিতায় এমন সুন্দর সুন্দর কথা এলো যে নিজেই অবাক হলাম।
এমনি এক রাত্রে—রাত তখন দুটো প্রায়—লিখতে লিখতে হঠাৎ আমার হাত কেঁপে একটা অক্ষর বেঁকে গেলো। শুনলাম বাইরে কে ডাকছে আমাকে, ‘বিকাশ বিকা—শ!’ একটু অপেক্ষা করলাম, আবার শুনলাম চাপা গলার ডাক। আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখি, ওরা দু’জন ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে।
সে রাত্রে তখনও চাঁদ ওঠেনি, সারা রাত্রেও বোধহয় ওঠেনি, অমাবস্যার কাছাকাছি রাত সেটা। আকাশ ছিলো তারায় ঝকঝকে, তারই ধুলোর মতো আলোয় আমরা তিনজন দাঁড়ালাম—শীতের রাত্রি, মাঠের মধ্যে, ঢিপঢিপ বুকে।
‘কী, অসিত? হিতাংশু কী খবর?’
‘আরম্ভ হয়েছে বোধহয়’, কথা বললো হিতাংশু।
‘আরম্ভ হয়েছে?’
‘একতলায় শুনলাম চলাফেরা, কথাবার্তা, আর চাপা একটা গোঙানি। ঘুমের মধ্যেই যেন শুনলাম, তারপর আর বিছানায় থাকতে পারলাম না। অসিতকে ডেকে তুলে তোমার কাছে এলাম। তুমি কি জেগেই ছিলে?’
আমি কথা বললাম না, তারার আলোয় দেখলাম হিতাংশুর মুখ শাদা হ’য়ে গেছে, আর অসিত মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে দূরের দিকে। এ-কদিনে আমরাও যেন বদলে গিয়েছিলাম; হাসি, ঠাট্টা, ঘোরাঘুরি কমে গিয়েছিলো আমাদের, বেশি কথা বলতাম না, আর এতদিন ধ’রে যে-মানুষকে নিয়ে লক্ষ কথা আমরা বলেছি, তার সম্বন্ধে একেবারে নীরব হ’য়ে গিয়েছিলাম। রুদ্ধশ্বাস আমরা, প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস।
আমরা বুঝলাম না যে আমরা কাঁপছি, জানলাম না যে আমরা হাঁটছি, কখন বাগানের ছোট গেট খুলে এসে সিঁড়ির তলায় দাঁড়ালাম। নিশ্চয়ই আমরা কোনো শব্দ করি নি, কোনো কথাও বলি নি, কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দে-সাহেব টর্চ হাতে বেরিয়ে এলেন, যেন আমাদেরই অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ। নিচুগলায় বললেন, ‘অসিত, একবার যাও তো সাইকেলটা নিয়ে ডক্টর মুখার্জির কাছে—একেবারে সঙ্গে ক’রে নিয়ে আসবে তাঁকে।’
অন্ধকারে হাওয়ার মতো মিলিয়ে গেলো অসিত। আমি আর হিতাংশু সিঁড়ির উপরেই ব’সে পড়লাম। একটা কান্না, চাপা একটানা, আমাদের পিঠ ফুঁড়ে বুকের মধ্যে ঢুকলো, তার যেন আওয়াজ নেই, শুধু কষ্ট আছে, যেন পৃথিবীর প্রাণে আঘাত দিয়েছে কেউ, পৃথিবীর বুক থেকে এই কান্না উঠছে, তাই কোনোদিন থামবে না।
ওকে চোখে দেখতে পারি না আমরা, দূর থেকেও না; ও-ঘরে যেতে পারি না আমরা, ঘরের কাছেও না। শুধু বাইরে ব’সে থাকতে পারি, শীতে, অন্ধকারে, না-জেগে, না-ঘুমিয়ে, আকাশের সামনে, অদৃষ্টের মুখোমুখি।
ডাক্তারের আনাগোনা শুরু হ’লো, চললো বাকি রাত ভ’রে, চললো তার পরের দিন। ভোর হ’তেই চড়া মাশুলের টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম হীরেনবাবুকে—মনে মনে ভাবলাম, টেলিগ্রাম যত দ্রুতই ছুটে যাক, তার চেয়েও দ্রুতবেগে ছুটে আসুক হীরেনবাবুর মন, কাল বিকেলের আগে তিনি পৌঁছতে পারবেন না কিছুতেই—কী অসহায় মানুষ, কী নিরুপায়! ডাক্তার, নার্স, ওষুধ, ইনজেকশন, পরিশ্রম, প্রার্থনা;—তবু অসহায়, তবু মানুষ অসহায়—কী হচ্ছে, কী হ’লো, কী হবে, এসব প্রশ্নের উত্তর নেই কারো চোখে, ডাক্তারের মুখ পাথরের মতো, ওর মা-বাবার মুখে সংক্ষিপ্ত ফরমাশ ছাড়া আর-কোনো কথা নেই, মাসিমা আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি পর্যন্ত ক’রেন না, আর দে-সাহেবের পরিপাটি চেহারাটির তলায় একজন কোঁকড়ানো বুড়োমানুষ যে লুকিয়ে ছিলো তা কে জানতো! কে জানতো আকাশের নীল নরম ঘোমটার তলায় এই কান্না লুকিয়ে আছে! আর আমাদের কি আর কিছু নেই, আর কিছু করবার নেই, শুধু কান পেতে এই কান্না শোনা ছাড়া?
দুপুরের আগেই বিকেল হ’য়ে গেলো সেদিন, বিকেলের আগেই অন্ধকার। তারপর, রাত যখন একটু ভারি হয়েছে, হঠাৎ যেন পৃথিবীর বুক চিরে চিৎকার উঠলো একটা; উঠলো, পড়লো, আবার উঠলো আকাশের দিকে; আকাশ চুপ, তারাদের নড়চড় হ’লো না; আবার উঠলো চিৎকার, যেন প্রতিমার সামনে ছাগশিশুর আর্তরব, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বিরামহীন। আমরা ছুটে চলে গেলাম বাইরে, মাঠের মধ্যে, কিন্তু যতদূর সে-শব্দ চলে আমাদের, মাতা পৃথিবীর আদিম কান্না এটা, এ থেকে নিস্তার কোথায়?
ফিরে এলাম। ভিতরে আলো, ব্যস্ততার ঢেউয়ের পর ঢেউ, ফাঁকে ফাঁকে ডাক্তারের মোটা গলা, আর বাইরে অফুরন্ত তারা, অসীম অন্ধকার, অপরূপ রাত্রি, কিন্তু পৃথিবীর কান্না তো থামে না।
যে-তারা ছিলো মাথার উপরে নেমে এলো পশ্চিমে, যে-তারা ছিলো চোখের বাইরে উঠে এলো দিগন্তের উপরে, পুবের কালো ফিকে হ’লো, ছোট ছোট অনেক তারা মুছে গিয়ে মস্ত সবুজ একলা একটি তারা জ্বলজ্বল করতে লাগল সেখানে। এই সেই অপার্থিব মুহূর্ত, সেই অলৌকিক লগ্ন, যখন আমি জেগে উঠে বাইরে এসেছিলাম ওর বিয়ের দিন, যখন আমি ওকে পেয়েছিলাম মৃত্যুর হাত থেকে, অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে একটিমাত্র ভেসে চলা আলো-জ্বলা নৌকায়। অন্তত একমুহূর্তের জন্য সেদিন সে আমার হয়েছিলো, আজ কি আবার এলো সেই মুহূর্ত?
অসিত ফিসফিস ক’রে বললো, ‘কী হ’লো?’
হিতাংশু বললো, ‘কই, না!’
‘সব যেন চুপ?’
‘তাই তো।’
‘যাব একবার ভেতরে?’ অসিত উঠে দাঁড়াল, কিন্তু গেলো না। অনেক, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমরা, কিন্তু আর কোনো শব্দ নেই, সব স্তব্ধ, তারপর হঠাৎ দেখি দে-সাহেব আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভোরের প্রথম ছাইরঙা আলোয় দেখলাম তাঁর ঠোঁট নড়ে উঠলো, এমন স্থির হ’য়ে আমরা তাকিয়েছিলাম আর এমন স্তব্ধ চারদিক যে তাঁর কথাটা আমরা কানে না-শুনে যেন চোখ দিয়ে দেখলাম :
‘এসো তোমরা, ওকে দেখবে।’
অসিত আর হিতাংশুই সব করলো, রাশি রাশি ফুল নিয়ে এলো কোথা থেকে, আরো কত কিছু বেলা দু’টো পর্যন্ত শুধু সাজাল শুধু সাজাল, তারপর নিয়ে যাবার সময় সকলের আগে রইল ওরা দু’জন। আরো অনেকে এলো কাঁধ দিতে, শুধু আমি বেঁটে ব’লে বাদ পড়লাম, পিছনে পিছনে হেঁটে চললাম একা-একা। ঠিক একা-একাও নয়, কারণ ততক্ষণ হীরেনবাবু এসে পৌঁছেছেন, গাড়ির কাপড়ে জুতো-ছাড়া পায়ে তিনিও চললেন আমার পাশে পাশে।
হীরেনবাবু পরের বছর আবার বিয়ে করলেন, দে-সাহেব চলে গেলেন বদলি হ’য়ে। কিছুদিন পর্যন্ত লোকেরা বলাবলি করলো ওঁদের কথা, তারপর তারা-কুটিরের একতলায় অন্য ভাড়াটে এলো, পুরানা পল্টনে আরও অনেক বাড়ি উঠলো, ইলেকট্রিক আলো জ্বললো। অসিত স্কুল থেকে বেরিয়ে চাকরি নিলো তিনসুকিয়ায়, ছ-মাসের মধ্যে কী একটা অসুখ ক’রে হঠাৎ মরে গেলো। হিতাংশু এম.এস.সি. পাস ক’রে জার্মানিতে গেলো পড়তে আর ফিরল না, সেখানকারই একটা মেয়েকে বিয়ে ক’রে সংসার পাতল, এখন এই যুদ্ধের পরে কেমন আছে, কোথায় আছে কে জানে। আর আমি—আমি এখনো আছি, ঢাকায় নয়, পুরানা পল্টনে নয়, উনিশ-শো সাতাশে কি আটাশে নয়, সে-সব আজ মনে হয় স্বপ্নের মতো, কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু স্বপ্ন, ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে একটু হাওয়া—সেই মেঘে-ঢাকা সকাল, মেঘ-ডাকা দুপুর, সেই বৃষ্টি, সেই রাত্রি, সেই—তুমি! মোনালিসা, আমি ছাড়া আর কে তোমাকে মনে রেখেছে!
বুদ্ধদেব বসু
আমরা তিনজন একসঙ্গে তার প্রেমে পড়েছিলাম : আমি, অসিত আর হিতাংশু; ঢাকায় পুরানা পল্টনে, উনিশ-শো সাতাশে। সেই ঢাকা, সেই পুরানা পল্টন, সেই মেঘে-ঢাকা সকাল!
এক পাড়ায় থাকতাম তিনজন। পুরানা পল্টনে প্রথম বাড়ি উঠেছিল তারা-কুটির, সেইটে হিতাংশুদের। বাপ তার পেনশন পাওয়া সাব-জজ, অনেক পয়সা জমিয়েছিলেন এবং মস্ত বাড়ি তুলেছিলেন একেবারে বড় রাস্তার মোড়ে। পাড়ার পয়লা নম্বর বাড়ি তারা-কুটির, দু-অর্থেই তাই, সবচেয়ে আগেকার এবং সবচেয়ে ভালো। ক্রমে ক্রমে আরো অনেক বাড়ি উঠে ঘাস আর লম্বা-লম্বা চোর-কাঁটা ছাওয়া মাঠ ভরে গেল, কিন্তু তারা-কুটিরের জুড়ি আর হলো না।
আমরা এসেছিলাম কিছু পরে, অসিতদের বাড়ির তখন ছাদ পিটোচ্ছে। একটা সময় ছিল, যখন ঐ তিনখানাই বাড়ি ছিল পুরানা পল্টনে; বাকিটা ছিল এবড়োখেবড়ো জমি, ধুলো আর কাদা, বর্ষায় গোড়ালি-জলে গা-ডোবানো হলদে-হলদে-সবুজ রঙের ব্যাঙ আর নধর সবুজ ভিজে-ভিজে ঘাস। সেই বর্ষা, সেই পুরানা পল্টন, সেই মেঘ-ঢাকা দুপুর!
আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকতাম সব সময়—যতটা এবং যতক্ষণ থাকা সম্ভব। রোজ ভোরবেলায় আমার শিয়রের জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে অসিত ডাকত, ‘বিকাশ! বিকাশ!’ আর আমি তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে আসতাম, দেখতাম অসিত সাইকেলে বসে আছে এক-পা মাটিতে ঠেকিয়ে—এমন লম্বা ও, কাঁধে হাত রাখতে কনুই ধরে যেত আমার। হিতাংশুকে ডাকতে হতো না, দাঁড়িয়ে থাকত তাদের বাগানের ছোট ফটকের ধারে, কি বসে থাকত বাগানের নিচু দেয়ালে পা ঝুলিয়ে, তারপর অসিত সাইকেলে চেপে চলে যেত পাকা সড়ক ধরে স্কুলে, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে; আমি আর হিতাংশু ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম হাতে হাত ধরে, হাওয়ায় গন্ধ, যেন কিসের, যেন কার, সে-গন্ধ আজও যেন পাই, কী মনে পড়ে, কাকে মনে পড়ে!
বিকেলে দুটি সাইকেলে তিনজনে চড়ে প্রায়ই আমরা শহরে যেতাম, কোনো দিন বিখ্যাত ঘোষবাবুর দোকানে চপ-কটলেট খেতে, কোনো দিন শহরে একটিমাত্র সিনেমায়, কোনো দিন চিনেবাদাম পকেটে নিয়ে নদীর ধারে। সাইকেল চালানোটা আমার জীবনে হলো না—চেষ্টা করেও শিখতে পারিনি ওটা, কিন্তু ঐ দু-চাকার গাড়িতে চড়েছি অনেক; কখনো অসিতের, কখনো হিতাংশুর গলগ্রহ হয়ে লম্বা-লম্বা পাড়ি দিয়েছি তাদের পিছনে দাঁড়িয়েই। আবার কত সন্ধ্যা কেটেছে পুরানা পল্টনেরই মাঠে, ঘাসের সোফায় শুয়ে-বসে ছোট ছোট তারা ফুটছে আকাশে, চোর-কাঁটা ফুটছে কাপড়ে, হিতাংশুদের সামনের বারান্দার লণ্ঠনটা মিটমিট করছে দূর থেকে। এ-সময়টা হিতাংশ বেশিক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকত না—আটটার মধ্যে তাকে ফিরতেই হতো বাড়িতে। অত কড়া শাসন আমার ওপর ছিল না, অসিতের ওপরেও না, দুজনে বসে থাকতাম অন্ধকারে, ফেরবার সময় আস্তে আস্তে একবার ডাকতাম হিতাংশুকে, পড়া ফেলে উঠে এসে চুপি চুপি দু-একটা কথা বলেই সে চলে যেত।
আমরা তিনজন তিনজনের প্রেমে পড়েছিলাম, আবার তিনজন একসঙ্গে অন্য একজনের প্রেমে পড়লাম, সেই ঢাকায়, পুরানা পল্টনে উনিশ-শো সাতাশ সনে।
নাম তার অন্তরা। তখনকার ঢাকার পক্ষে নামটি অত্যন্তই শৌখিন, কিন্তু ঢাকার মতো কিছুই তো তাঁদের নয়, মেয়ের নামই বা হবে কেন। ভদ্রলোক বাড়িতেও প্যান্ট পরে থাকেন, আর ভদ্রমহিলা এমন সাজেন যে পিছন থেকে হঠাৎ তাঁকে তাঁর মেয়ে বলে ভুল হয়—আর তাঁর মেয়ে, তাঁদের মেয়ে, তার কথা আর কী বলব! সে সকালে বাগানে বেড়ায়, দুপুরে বারান্দায় বসে থাকে বই কোলে নিয়ে, বিকেলে রাস্তায় হাঁটে প্রায় আমাদের গা ঘেঁষেই, সব সময় দেখা যায় তাকে, মাঝে মাঝে শোনা যায় গলার আওয়াজ—সেই ঢাকায়, সুদূর সাতাশ সনে, কোনো একটা মেয়েকে চোখে দেখা যখন সহজ ছিল না, যখন বন্ধ-গাড়ির দরজার ফাঁকে একটুখানি শাড়ির পাড় ছিল আমাদের স্বর্গের আভাস, তখন—এই যে মেয়ে, যাকে আমরা দেখতে পাই একেক দিন একেক রঙের শাড়িতে, আর তার ওপর নাম যার অন্তরা, তার প্রেমে পড়ব না এমন সাধ্য কি আমাদের!
নামটা কিন্তু বের করেছিলাম আমি। রোজ সই করে পাউরুটি রাখতে হয় আমাকে, একদিন রুটিওয়ালার খাতায় নতুন একটা নাম দেখলাম নীল কালিতে বাংলা হরফে পরিষ্কার করে লেখা : ‘অন্তরা দে’। একটু তাকিয়ে থাকলাম লেখাটুকুর দিকে, খাতা ফিরিয়ে দিতে একটু দেরি করলাম, তারপর বিকেলে হিতাংশুকে বললাম, ‘নাম কি অন্তরা?’
‘কার’—কিন্তু তক্ষুনি কথাটা বুঝে নিয়ে হিতাংশু বলল, ‘বোধ হয়।’ অসিত বলল, ‘সুন্দর নাম!’
‘ডাকে তরু বলে।’
তরু! এই ঢাকা শহরেই দু-তিনশো অন্তত তরু আছে, কিন্তু সে-মুহূর্তে আমার মনে হলো এবং আমি বুঝলাম অসিতেরও মনে হলো যে সমস্ত বাংলা ভাষায় তরুর মতো এমন একটি মধুর শব্দ আর নেই। তা হোক, হিতাংশুর একটু বাজে কথা বলা চাই। কেননা যাকে নিয়ে বা যাদের নিয়ে কথা হচ্ছে, তাদেরই বাড়ির এক তলায় তারা ভাড়াটে, আমাদের চাইতে বেশি না-জানলে ওর মান থাকে না। তাই ও নাকের বাঁশিটা একটু কুঁচকে বলল, ‘অন্তরা থেকে তরু—এটা কিন্তু আমার ভালো লাগে না।’
‘ভালো না কেন, খুব ভালো!’ গলা চড়িয়ে দিলাম, কিন্তু ভেতরটা কেমন দমে গেল। ‘আমি হলে অন্তরাই ডাকতাম।’
কী সাহস! কী দুঃসাহস! তুমি ডাকতে, তাও আবার নাম ধরে। ইস! প্রতিবাদের তাপে আমার মুখ গরম হয়ে উঠল, বেশ চোখা চোখা কয়েকটা কথা মনে-মনে গোছাচ্ছি, ফস করে অসিত বলে উঠল, ‘আমিও তা-ই।’
বিশ্বাসঘাতক!
এ-রকম ছোট ছোট ঝগড়া প্রায়ই হতো আমাদের। এমন দিন যায় না যেদিন ওকে নিয়ে কোনো কথা না হয়, আর এমন কোনো কথা হয় না যাতে তিনজনেই একমত হতে পারি। সেদিন যে নীল শাড়ি পরেছিল তাতেই বেশি মানিয়েছিল, না কালকের বেগুনি রঙেরটায়; সকালে যখন বাগানে দাঁড়িয়ে ছিল তখন পিঠের ওপর বেণি দুলছিল, না চুল খোলা ছিল, বিকেলে বারান্দায় বসে কোলের ওপর কাগজ রেখে কী চিঠি লিখছিল, না আঁক কষছিল—এমনই সব বিষয় নিয়ে চেঁচামেচি করে আমরা গলা ফাটাতুম। সবচেয়ে বেশি তর্ক হতো যে-কথা নিয়ে সেটা একটু অদ্ভুত : ওর মুখের সঙ্গে মোনালিসার মিল কি খুব বেশি, না অল্প একটু, না কিছুই না। আমি তখন প্রথম মোনালিসার ছাপা ছবি দেখেছি এবং বন্ধুদের দেখিয়েছি। হঠাৎ একদিন আমারই মুখ দিয়ে বেরোল কথাটা—‘ওর মুখ অনেকটা মোনালিসার মতো।’ তারপর এ নিয়ে অসংখ্য কথা খরচ করেছি আমরা, কোনো মীমাংসা হয়নি; তবে একটা সুবিধা এই হলো যে আমাদের মুখে-মুখে ওর নাম হয়ে গেল মোনালিসা। অন্তরাতে যতই সুর ঝরুক, তরুতে যতই তরুণতা, যে-নামে ওকে সবাই ডাকে সে-নামে তো আমরা ওকে ভাবতে পারি না—অন্য একটি নাম, যা শুধু আমরা জানি, আর কেউ জানে না, এমন একটি নাম পেয়ে আমরা যেন ওকেই পেলাম।
হিতাংশুকে প্রায়ই বলতাম, ‘তোমার সঙ্গে একদিন আলাপ হবেই—একই তো বাড়ি’, আর হিতাংশুও একটু লাল হয়ে বলত, ‘যাঃ!’ যার মানে হচ্ছে যে সেটা হলেও হতে পারে—আর তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনাই চলত আমাদের, কিন্তু মনে-মনে আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে এ-সব কিছু না, শুধুই কথার কথা।
একদিন সন্ধ্যার একটু পরে তিনজনে ফিরছি সাইকেলে রমনা বেড়িয়ে, আমি হিতাংশুর পিছনে, নির্জন পথে নিশ্চিন্তে গল্প চালিয়েছি, হঠাৎ হিতাংশু কথা বন্ধ করে সাইকেলের ওপর কী রকম কেঁপে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম সাইকেল থেকে, টাল সামলাতে গিয়ে টেনে ধরলাম হিতাংশুর জামার গলা; ‘উঃ’ বলে সে নেমে পড়ল, আমি পায়ের তলায় মাটি পেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে মোটা গলায় কে একজন বলে উঠলেন, ‘Take care young man!’ তাকিয়ে দেখি, ঠিক আমাদের সামনে দে-সাহেব দাঁড়িয়ে, আর তাঁর স্ত্রী—আর কন্যা। অসিত সাইকেলটা একটু ঘুরিয়ে এক পা মাটিতে ঠেকিয়ে চুপ করে আছে, তার মুখের ভাবটা বেশ বীরের মতো।
‘Really you must—’ বলতে বলতে দে-সাহেব হিতাংশুর মুখের ওপর চোখ রাখলেন।— ‘Oh it’s you! কেশব বাবুর ছেলে!’
‘আমি স্পষ্ট দেখলাম, হিতাংশুটা বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।’
‘আর এরা—তিনজনকে একসঙ্গেই তো দেখতে পাই সব সময়। বন্ধু বুঝি! বেশ, বেশ। I like young men. এসো একদিন আমাদের ওখানে তোমরা।’
ওঁরা চলে গেলেন। আমরা রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে ঘাসের ওপর পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম লম্বা হয়ে। একটু পরে অসিত বলল, ‘কী কাণ্ড! হিতাংশু ঘাবড়ে গিয়েছিলে না?’
‘না তো! ঘাবড়াব কেন? ব্রেকটা হঠাৎ—’
‘কোনো দিন তো এ-রকম হয় না। আর আজ কিনা ওঁদের সামনে—’
‘বেশ তো! হয়েছে কী? কারো গায়েও পড়েনি, পড়েও যাইনি, হঠাৎ ব্রেক কষতে গিয়ে—’
‘না, না, তুমি তো ঠিকই নেমেছিলে, তবে তোমার মুখটা যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। আর বিকাশ তো—’
আমার নাম করতেই আমি খেঁকিয়ে উঠলাম, ‘চুপ করো, ভালো লাগে না!’
‘ও বোধ হয় একটু হেসেছিল’, অসিত তবু ছাড়ল না (‘ও’ বলতে কাকে বোঝায় তা বোধ হয় না বললেও চলে)।
‘হেসেছিল তো বয়ে গেল!’ চিৎকার করল হিতাংশু, কিন্তু সে চিৎকার যেন কান্না।
‘তুমি দেখেছিলে বিকাশ? ঠিক মোনালিসার হাসির মতো কি?’
‘যা বোঝো না তা নিয়ে ঠাট্টা কোরো না!’ বলতে গিয়ে আমার গলা ভেঙে গেল। সে-রাত্রে ভালো ঘুমোতে পারলাম না, দুদিন আধমরা হয়ে রইলাম, সাত দিন মন-মরা।
রাগ করি আর যা-ই করি, আমাদের মধ্যে অসিতটাই তুখোড়। সে কেবলই বলতে লাগল, ‘চল না একদিন যাই আমরা ওঁদের ওখানে।’
‘পাগল।’
‘পাগল কেন? দে-সাহেব বললেন তো যেতে! বললেন না?’
ক্রমে-ক্রমে হিতাংশুর আর আমারও ধারণা জন্মাল যে দে-সাহেব সত্যিই আমাদের যেতে বলেছেন, আমরা গেলে রীতিমতো সুখী হবেন তিনি, না-গেলে দুঃখিত হবেন—এমনকি তাঁকে অসম্মানই করা হবে তাতে। তাঁর সম্মান রক্ষার জন্য ক্রমশই আমরা বেশি রকম ব্যস্ত হতে লাগলাম। রোজ সকালে স্থির করি ‘আজ’, রোজ বিকেলে মনে করি, ‘আজ থাক’। কোনো দিন দেখি ওঁরা বাগানে বসেছেন বেতের চেয়ারে; কোনো দিন বাড়ির সামনে মোটরগাড়ি দাঁড়ানো, তার মানে শহরের একমাত্র ব্যারিস্টার দাস-সাহেব বেড়াতে এসেছেন। আর কোনো দিন বা চুপচাপ দেখে ধরে নিই ওঁরা বাড়ি নেই। দৈবাৎ একদিন হয়তো চোখে পড়ে দে-সাহেব একা বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, মনে হয় এইটে ভারি সুসময়, কিন্তু বাগানের গেটের সামনে পা থমকে যায় আমাদের, অসিতের যতটা নয় ততটা হিতাংশুর, হিতাংশুর ততটা নয় যতটা আমার, একটু ঠেলাঠেলি ফিসফিসানি হয়, আর শেষ পর্যন্ত তারা-কুটির ছাড়িয়ে মোড় ঘুরে আমরা অন্যদিকে চলে যাই। কেবলই মনে হয় এখন গেলে বিরক্ত হবেন, আবার তখনই ভাবি—বিরক্ত কেন, আর এ নিয়ে এত ভাববারই বা কী আছে, মানুষ কি মানুষের সঙ্গে দেখা করে না? আমরা চোরও নই, ডাকাতও নই, যাব, বসব, আলাপ করব, চলে আসব—ব্যস!
সেদিন আকাশে মেঘ টিপটিপ বৃষ্টি। বাইরে থেকে মনে হলো ওঁরা বাড়িতেই আছেন। ছোট্ট গেট ঠেলে সকলের আগে ঢুকল অসিত, লম্বা ফরসা, সুশ্রী; তারপর হিতাংশু, গম্ভীর, চশমা পরা, ভদ্রলোক মাফিক; আর সকলের শেষে পুঁচকে আমি। বাগান পার হয়ে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম আমরা, কাউকে ডাকব কি না, কাকে ডাকব, কী বলে ডাকব—এসব আমরা যতক্ষণ ধরে ভাবছি, ততক্ষণ পরদা ঠেলে দে-সাহেব নিজেই বেরিয়ে এলেন। দাঁতের ফাঁকে পাইপ চেপে ধরে বললেন, ‘Yes?’
এই বিজাতীয় সম্ভাষণে সপ্রতিভ অসিতও একটু বিচলিত হলো। ‘আমি—আমরা—মানে আমরা এসেছিলাম—আপনি বলেছিলেন—’ আবছা আলোয় তখন দে-সাহেব আমাদের চিনলেন। ‘ও, তোমরা! তা…’
অসিত আবার বলল, ‘আপনি বলেছিলেন আমাদের একদিন আসতে।’
‘ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ…’ একটু কেশে—‘এসো, এসো তোমরা’, পর্দা তুলে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন দে-সাহেব, আমরাও দাঁড়িয়ে থাকলাম।
‘যাও, ভেতরে যাও।’
ঢুকতে গিয়ে হিতাংশু তার নিজেরই বাড়ির চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে আমার পা মাড়িয়ে দিল, খুব লাগল আমার, কিন্তু চুপ করে থাকা ছাড়া তখন আর উপায় কী। আমাদের কাদামাখা স্যান্ডেলে ঝকঝকে মেঝে নোংরা করে এলাম আমরা। কী সুন্দর সাজানো ঘর, এমন কখনো দেখিনি। পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। সামনের দিকে সোফায় বসে মিসেস দে উল বুনছেন, আর দেয়ালের সঙ্গে ঠেকানো কোণের চেয়ারটিতে বসে আছে আমাদের মোনালিসা, কোলের ওপর মস্ত মোটা নীল মলাটের বইয়ের পাতায় চোখ নামিয়ে।
দে-সাহেব বললেন, ‘সুমি, এই আমাদের পুরানা পল্টনের থ্রি মস্কেটিঅর্স। এটি কেশব বাবুর ছেলে, আর এরা…’
হিতাংশু পরিচয় করিয়ে দিল, ‘এর নাম অসিত আর এই হচ্ছে বিকাশ।’
মিসেস দে মৃদু হেসে মৃদুস্বরে বললেন, ‘তিন বন্ধু বুঝি তোমরা? বেশ, রোজই তো দেখি তোমাদের। বসো।’
একটা লম্বা সোফায় ঝুপঝুপ বসে পড়লাম তিনজনে। মিসেস দে ডাক দিলেন—’তরু’!
মোনালিসা চোখ তুলল।
‘এঁরা আমাদের প্রতিবেশী—আর এই আমার মেয়ে।’
মোনালিসা বই রেখে উঠল, ছিপছিপে সবুজ একটি গাছের মতো দাঁড়াল, অল্প হাওয়ায় গাছ যেমন নড়ে, তেমনি করে মাথা নোয়াল একটু, তারপর আবার চেয়ারে বসে বই খুলে চোখ নিচু করল।
আমার মনে হলো আমি স্বপ্ন দেখছি।
অসিত কলকাতার ছেলে, আমাদের সকলের চাইতে খবর রাখে বেশি, চটপট কথা বলতেও পারে; আর হিতাংশু—সেও তার বাবার সঙ্গে নানা দেশ ঘুরেছে, উচ্চারণ পরিষ্কার, আর তা ছাড়া এই তারা-কুটির তো তাদেরই বাড়ি। কথাবার্তা যা একটু তা ওরা দুজনেই বলল, আমি মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ, কী বলব ভেবেও পেলাম না, বলতেও ভরসা হলো না, পাছে আমার বাঙাল টান বেরিয়ে পড়ে। মোনালিসাকে দেখবার ইচ্ছা ভেতরে-ভেতরে পাগল করে দিচ্ছিল আমাকে, কিন্তু কিছুতেই কি একবারও চোখ তুলতে পারলাম!
ইলেকট্রিসিটি না থাকলে জীবন কী রকম দুর্বহ, ঢাকার মশা কী সাংঘাতিক, রমনার দৃশ্য কত সুন্দর, এসব কথা শেষ হবার পর মিসেস দে বললেন, ‘তোমরা কি কলেজে পড়ো?’
অসিত যথাযথ জবাব দিয়ে সগর্বে বলল, ‘হিতাংশু পনেরো টাকা স্কলারশিপ পেয়েছে ম্যাট্রিকে।’
‘বাঃ বেশ, বেশ। আমার মেয়ে তো অঙ্কের ভয়ে পরীক্ষাই দিতে চায় না।’
হঠাৎ ঘরের কোণ থেকে তারের মতো একটি আওয়াজ বেজে উঠল, ‘বাবা, কীটস কত বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন?’
দে-সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমরা কেউ বলতে পারো?’
অসিত ফস করে বলল, ‘বিকাশ নিশ্চয়ই বলতে পারবে—বিকাশ কবিতা লেখে।’
‘সত্যি?’ মুখে একটি ছেলেমানুষি হাসি ফোটালেন মিসেস দে, আর মুহূর্তের জন্য—আমি অনুভব করলাম—মোনালিসার চোখও আমার ওপর পড়ল। হাত ঘেমে উঠল আমার, কানের ভেতর যেন পিঁ-পিঁ আওয়াজ দিচ্ছে।
সবসুদ্ধু কতটুকু সময়? পনেরো মিনিট? কুড়ি মিনিট? কিন্তু বেরিয়ে এলাম যখন এত ক্লান্ত লাগল, কলেজে চারটা-পাঁচটা লেকচার শুনেও তত লাগে না।
মিসেস দে জোর করেই দুটা ছাতা দিয়েছিলেন আমাদের, কিন্তু ছাতা আমরা খুললাম না, টিপটিপ বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মাঠের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম। হঠাৎ অসিত—বকবক না করে ও থাকতেও পারে না—বলে উঠল, কী চমৎকার ওঁরা!’
‘সত্যি! চমৎকার!’ হিতাংশু সায় দিল সঙ্গে সঙ্গে।
আমি কথা বললাম না, কোনো কথাই ভালো লাগছিল না আমার।
একটু পরে অসিত আবার বলে, ‘কিন্তু জুতোগুলো বাইরে ছেড়ে গেলেই পারতাম আমরা! আর হিতাংশু, তুমি আবার আজ হোঁচট খেলে!’
‘কখন?’
‘ঘরে ঢুকতে গিয়ে।’
‘যাঃ!’
‘যাঃ আবার কী। আর ঘুরে ঢুকে নমস্কার করেছিলে তো মিসেস দে-কে?’
‘নিশ্চয়ই!’ একটু চুপ করে থাকল হিতাংশু, তারপর হঠাৎ বলল, কিন্তু যখন মোনালিসা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল…’
অন্ধকারে আমরা তিন বন্ধু একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম এবং অন্ধকারেই বোঝা গেল যে তিনজনেরই মুখ ফ্যাকাসে হয়েছে। একটি মেয়ে, একজন ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন, আর আমরা কিনা জরদ্গবের মতো বসেই থাকলাম—উঠে দাঁড়ালাম না, কিছু বললাম না, কিচ্ছু না, ওঁরা আমাদের বাঙাল ভাবলেন, কাঠ-বাঙাল, জংলি, বর্বর, খাস কলকাতার ছেলে অসিত মিত্তিরও আমাদের মুখ-রক্ষা করতে পারল না।
কী যে মন-খারাপ হলো, কী আর বলব।
পরের দিন তিনজনে আবার গেলাম ছাতা ফেরত দিতে। চাকর আমাদের ঘরে নিয়ে বসাল, তারপর—তারপর মোনালিসাই এলো ঘরে, তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম, একটু হেসে বললাম, ‘এই ছাতাটা…’! ‘ও মা! এর জন্য আবার…বসুন…।’ মনে-মনে এই রকম ভেবে গিয়েছিলাম ঘটনাটা, কিন্তু হলো একটু অন্য রকম। চাকর এসে ছাতাটি নিয়ে ভেতরে চলে গেল, আর ফিরে এলো না, কেউই এলো না। আমরা একটু দাঁড়িয়ে থেকে মাথা নিচু করে নিঃশব্দে ফিরে এলাম—কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। না, না। ঐ সুন্দর করে সাজানো ঘর, যেখানে সাদা ধবধবে আলোয় দেয়ালের প্রতিটি কোণ ঝকঝক করে, আর কোণের চেয়ারে বসে পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়েটি কোনো এক নীল মলাটের আশ্চর্য বইয়ের পাতা ওল্টায়—সেখানে জায়গা নেই আমাদের। কিন্তু তাতে কী। মোনালিসা—মোনালিসাই। ঝমঝম করে বর্ষা নামল পুরানা পল্টনে, মেঘে-ঢাকা সকাল, মেঘ-ডাকা দুরু দুরু দুপুর, নীল জ্যোৎস্নায় ভিজে-ভিজে রাত্রি। পনেরো দিন ধরে প্রায় অবিরাম বৃষ্টির পর প্রথম যেদিন রোদ উঠল, সেদিন বাইরে এসে দেখি শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তারের মোটরগাড়ি তারা-কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে।
হিতাংশুকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমাদের বাড়িতে কারো অসুখ নাকি?’
‘না তো!’
তবে কি ওদের বাড়িতে—প্রশ্নটা উচ্চারিত না হয়েও ব্যক্ত হলো। পরের দিন হিতাংশু গম্ভীর মুখে বলল, ‘ওদের বাড়িতেই অসুখ।’
‘কার?’
‘ওরই অসুখ।’
‘ওর অসুখ!’
‘ওর!’
সেদিনও বড় ডাক্তারের গাড়ি দেখলাম, তার পরদিন দুবেলাই। আমরা কি একবার যেতে পারি না, কিছু করতে পারি না? ঘুরঘুর করতে লাগলাম রাস্তায়, ডাক্তারের গাড়ির আড়ালে। ডাক্তার বেরিয়ে এলেন, দে-সাহেব সঙ্গে সঙ্গে গেট পর্যন্ত। আমাদের চোখেই দেখলেন না তিনি, তারপর হঠাৎ দেখতে পেয়ে বললেন, ‘তোমরা একবার যাও তো ভেতরে, উনি একটু কথা বলবেন।’
সিঁড়ির ওপরের ধাপে দাঁড়িয়েছিলেন মিসেস দে, এক সিঁড়ি নিচে দাঁড়িয়ে অসিত বলল, ‘আমাদের ডেকেছেন, মাসিমা?’ কলকাতার ছেলে, ডাক-টাকগুলো দিব্যি আসে, আমি মরে গেলেও ওসব পারি না।
মিসেস দে বললেন, ‘তরুর অসুখ।’ তার কণ্ঠস্বর আমার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিল।
‘কী অসুখ?’
‘টাইফয়েড!’ ঐ ভয়ংকর শব্দটা আস্তে উচ্চারণ করে তিনি বললেন, ‘আমার কিছু ভালো লাগছে না।’
অসিত বলে উঠল, ‘কিছু ভাববেন না। আমরা সব করে দেব।’
‘পারবে, পারবে তোমরা? দ্যাখো বাবা, এই একটাই সন্তান আমার…’ বলতে বলতে চোখে তাঁর জল এলো।
মোনালিসা, কোনোদিন জানলে না তুমি, কোনোদিন জানবে না, কী ভালো আমাদের লেগেছিলো, কী সুখী আমরা হয়েছিলাম, সেই সাতাশ সনের বর্ষায়, পুরানা পল্টনে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, সেই জ্বরে ঝড়ে, বৃষ্টিতে থমথমে অন্ধকারে, ছমছমে ছায়ায়। দেড় মাস তুমি শুয়ে ছিলে, দেড় মাস তুমি আমাদের ছিলে। দেড় মাস ধ’রে সুখের স্পন্দন দিনে-রাত্রে কখনো থামল না আমাদের হৃৎপিণ্ডে। তোমার বাবা আপিস যান, ফিরে এসে রোগীর ঘরে উঁকি দিয়েই হাত-পা এলিয়ে শুয়ে পড়েন ইজি-চেয়ারে; তোমার মা-র সারাদিন পায়ের পাতা দাঁড়ায় না, কিন্তু রাত্তিরে আর পারেন না তিনি, রোগীর ঘরেই ক্যাম্পখাটে ঘুমোন, আর সারারাত পালা ক’রে ক’রে জেগে থাকি আমরা—কখনো একসঙ্গে দুজনে, ক্বচিৎ তিনজনেই, বেশির ভাগ একলা একজন। আর তোমাকে নিয়ে এই একলা রাত-জাগায় সুখ আমিই পেয়েছি বেশি—অসিত সারাদিন ছুটোছুটি করেছে সাইকেলে, হিতাংশুও বারবার। সবচেয়ে কাছের বরফের দোকান এক মাইল দূরে, ওষুধের দোকান দুই মাইল, ডাক্তারের বাড়ি সাড়ে তিন মাইল—কোনোদিন অসিত দশবার যাচ্ছে, দশবার আসছে, কতবার ভিজে কাপড় শুকোল তার গায়ে, কোনোদিন রাত বারোটায় হিতাংশু ছুটল বরফ আনতে, সব দোকান বন্ধ, রেলের স্টেশন নিঃসাড়, নদীর ধারে বরফের ডিপোতে গিয়ে লোকজনের ঘুম ভাঙিয়ে বরফ নিয়ে আসতে-আসতে দুটো বেজে গেলো তার, এদিকে আমি আইসব্যাগে জলের পরিমাণ অনুভব করছি বারবার, আর অসিত বাথরুমে বরফের ছোট ছোট ছড়ানো টুকরো দু-হাতে কুড়োচ্ছে। সাইকেলে আমার দখল নেই ব’লে বাইরের কাজ আমি কিছুই প্রায় পারি না, সারাদিন ঘুর-ঘুর করি তোমার মা-র কাছে কাছে, হাতের কাছে এগিয়ে দিই সব, ওষুধ ঢালি, টেম্পারেচার লিখি, ডাক্তার এলে তাঁর ব্যাগ হাতে ক’রে নিয়ে আসি, নিয়ে যাই। তারপর সন্ধ্যা হয়, রাত বাড়ে, বাইরে অন্ধকারের সমুদ্র, সে-সমুদ্রে ক্ষীণ আলো-জ্বলা একটি নৌকোয় তুমি আর আমি চলেছি ভেসে, তুমি তা জানলে না মোনালিসা, কোনোদিন জানবে না। সারাদিন, সারারাত মোনালিসা মূর্ছিতের মতো প’ড়ে থাকে, ভুল বকে মাঝে মাঝে—এত ক্ষীণ-স্বর যে কী বলছে বোঝা যায় না—তবু যে ক’টি কথা আমরা কানে শুনেছি তা-ই যত্ন ক’রে তুলে রেখেছি মনে, একের শোনা কথা অন্য দুজনকে বলাই চাই; কখনো হঠাৎ একটু অবসর হলে তিনজন ব’সে সেই কথা ক’টি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, যেন তিনজন কৃপণ সারা পৃথিবীকে লুকিয়ে তাদের মণি-মুক্তো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে, বন্ধ ঘরে, অন্ধকার রাত্রে। যদি বলেছে ‘উঃ’, সে যেন বাঁশির ফুঁয়ের মতো আমাদের হৃদয়কে দুলিয়ে গেছে; যদি বলেছে ‘জল’, তাতে যেন জলের সমস্ত তরলতা ছলছল ক’রে উঠেছে আমাদের মনে।
এক রাত্রে হিতাংশু বাড়ি গেছে আর অসিত বারান্দায় বিছানায় ঘুমুচ্ছে, আমি জেগে আছি একা। টেবিলের উপর জ্বলছে মোমবাতি, দেওয়ালের গায়ে ছায়া কাঁপছে বড়-বড়, অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ ক’রে ঐ আলোটুকু যেন আর পারছে না; আমিও আর পারছি না ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, ডাকাতের মতো ঘুম আমার হাত-পা কেটে-কেটে টুকরো ক’রে দিলো, মোমের মতোই গলে যাচ্ছে আমার শরীর। যতবার চাবুক মেরে নিজেকে সোজা করছি; লাফিয়ে উঠছে অতল থেকে বিশাল ঢেউ। ডুবতে ডুবতে মনে হ’লো মোনালিসা তুমিও কি এমন করেই যুদ্ধ করছ মৃত্যুর সঙ্গে, মৃত্যু কি এই ঘুমের মতোই টানছে তোমাকে, তবু তুমি আছো—কেমন ক’রে আছো! মনে হ’তেই ঘুম ছুটল। সোজা হ’য়ে বসলাম, তাকিয়ে রইলাম তোমার মুখের দিকে সেই ক্ষীণ আলোয় কাঁপা-কাঁপা ছায়ায় রাত চারটের স্তব্ধ মহান মুহূর্তে। তুমি কি মরবে? তুমি কি বেঁচে উঠবে? কোনো উত্তর নেই। তোমার কি ঘুম পেয়েছে? উত্তর নেই। তুমি ঘুমিয়েছ না জেগে আছো? উত্তর নেই। তবুও আমি তাকিয়ে থাকলাম, মনে হ’লো এর উত্তর আমি পাবই, পাব তোমারই মুখে, তোমার মুখের কোনো একটি ভঙ্গিতে হয়তো—কে জানে—তোমার কণ্ঠেরই কোনো একটি কথায়। আর, আমি অবাক হ’য়ে দেখলাম, আস্তে আস্তে চোখ তোমার খুলে গেলো, মস্ত বড় হ’লো, উন্মাদের মতো ঘুরে ঘুরে স্থির হ’লো আমার মুখের উপর। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল—‘কে?’
আমি তাড়াতাড়ি আইসব্যাগ চেপে ধরলাম।
‘কে তুমি?’
‘আমি।’
‘তুমি কে?’
‘আমি বিকাশ।’
‘ও, বিকাশ। বিকাশ, এখন দিন, না রাত্রি?’
‘রাত্রি।’
‘ভোর হবে না?’
‘হবে, আর দেরি নেই।’
‘দেরি নেই? আমার ঘুম পাচ্ছে, বিকাশ।’
আমি তার কপালে আমার বরফে-ঠাণ্ডা হাত রাখলাম।
‘আহ্, খুব ভালো লাগছে আমার।’
‘আমি বললাম, ‘ঘুমোও।’
‘তুমি চলে যাবে না তো?’
‘না।’
‘যাবে না তো?’
‘না।’
‘আমি তাহলে ঘুমুই, কেমন?’
নিশ্বাস উঠলো আমার ভিতর থেকে, নিশ্বাসের স্বরে বললাম,—‘ঘুমোও, ঘুমোও, আমি জেগে আছি, কোনো ভয় নেই।’
তুমি ঘুমিয়ে পড়লে আর বাইরে, দু-একটা পাখি ডাকল। ভোর হ’লো।
প্রলাপ, জ্বরের প্রলাপ, তবু এটা আমারই থাক। একলা আমার। এই একটা কথা ওদের দুজনেক বলি নি, হয়তো ওদেরও এমন কিছু আছে যা আমি জানি না, আর-কেউ জানে না। তুমি, মোনালিসা, তুমিও জানলে না, জানবে না কোনোদিন।
তারপর একদিন তুমি ভালো হলে। সে তো খুব সুখের কথা, কিন্তু আমরা যেন বেকার হ’য়ে পড়লাম। আর তুমি ভাতটাত খাবার দিন-পনের পরে যে-রবিবারে তোমার মা আমাদের তিনজনকে নিমন্ত্রণ ক’রে খাওয়ালেন, সেদিন আমার অন্তত মনে হ’লো যে এই খাওয়াটা আমাদের ফেয়ারওএল পার্টি।
কিন্তু তা-ই বা কেন? এখনো আমরা যেতে পারি, বসতে পারি কাছে, গ্রামোফোন বাজিয়ে শোনাতে পারি, সে ক্লান্ত হলে পিঠের বালিশটা দিতে পারি ঠিক ক’রে। এদিকে আকাশে কালো মেঘের সঙ্গে সাদা মেঘের খেলা, আর ফাঁকে-ফাঁকে নীলের মেলা, এই ক’রে-ক’রে আশ্বিন যেই এলো, ওঁরা চলে গেলেন মেয়ের শরীর সারাতে রাঁচি।
বাঁধাছাঁদা থেকে আরম্ভ ক’রে নারায়ণগঞ্জে স্টিমারে তুলে দেয়া পর্যন্ত সঙ্গে-সঙ্গে থাকলাম আমরা তিনজন।
ফার্স্ট ক্লাসের ডেকে রেলিং ধরে দাঁড়ানো মোনালিসার ছবিটি যখন চোখের সামনে ঝাপসা হ’লো তখন আমাদের মনে পড়লো যে ওঁদের রাঁচির ঠিকানাটা জেনে রাখা হয়নি আমার ইচ্ছে করছিলো বাড়ি ফিরেই একটা চিঠি লিখে ডাকে দিই, তা আর হ’লো না।
অসিত বললো, ‘ওরই তো আগে লেখা উচিত।’
‘তা কি আর লিখবে?’ একটু হতাশভাবেই বললো হিতাংশু।
‘কেন লিখবে না, না-লেখার কী আছে।’
কী আছে কে জানে, কিন্তু কুড়ি দিনের মধ্যেও কোনো চিঠি এলো না। এলো হিতাংশুর বাবার নামে মনি-অর্ডার, বাড়ি-ভাড়ার টাকা। তাই থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে আমরা চিঠি লিখব স্থির করলাম। ও লেখে নি বলে আমরাও না-লিখে রাগ দেখাব, এটা কোনোরকম যুক্তি বলেই মনে হলো না আমাদের। অসুখ থেকে উঠে গেছে, হয়তো এখনো ভালো ক’রে শরীর সারেনি—কেমন আছে সে খবরটা আমাদেরই তো নেয়া উচিত। কিন্তু চিঠিতে পাঠে কী লিখব? আপনি লিখব, না তুমি? মুখে ও অবশ্য আমাদের তুমিই বলেছে, আমরাও তা-ই, কিন্তু কতটুকু কথাই বা এ পর্যন্ত বলেছি আমরা—এতখানি কথা নিশ্চয়ই বলি নি যার জোরে কালির আঁচড়ে জ্বলজ্বলে একটা তুমি লিখে ফেলা যায়। তাছাড়া, কী লিখবই বা চিঠিতে? কেমন ভালো তো? এতেই তো সব কথা ফুরিয়ে গেলো। আমরা কেমন আছি, কী করছি, সে-সব লিখলে তো কতই লেখা যায়—কিন্তু মোনালিসা কি আমাদের খবর জানতে ব্যস্ত?
অনেকক্ষণ ধ’রে জটলা ক’রেও কোনো মীমাংসা যখন হ’লো না, তখন ওরা আমাকেই বললো চিঠিখানা রচনা ক’রে দিতে। আমি কবিতা-টবিতা লিখি, তাই।
সে-রাত্রেই লণ্ঠনের সামনে ঘামতে ঘামতে আমি লিখে ফেললাম :
সুচরিতাষু,
ভেবেছিলাম একখানা চিটি আসবে, চিঠি এলো না। ভাবতে-ভাবতে একুশ দিন কেটে গেলো। খুবই ভালো লাগছে বুঝি রাঁচিতে? অবশ্য ভালো লাগলেই ভালো, আমরা তাতেই খুশী। তারা-কুটিরের একতলা বন্ধ, পুরানা পল্টন তাই অন্ধকার। ওখানে পেট্রোম্যাক্স জ্বলত কিনা রোজ সন্ধ্যায়।
বসে বসে রাঁচির ছবি দেখছি আমরা। পাহাড়, জঙ্গল, লাল কাঁকরের, কালো-কালো-সাঁওতাল। হাসি, আনন্দ, স্বাস্থ্য। সত্যি, কী বিশ্রী অসুখ গেলো—আর যেন কখনো অসুখ না ক’রে।
কারো কোনো অসুখ না ক’রেও এমন কি হয় না যে আমাদের খুব খাটতে হয়? সত্যি, শুয়ে-ব’সে আর সময় কাটে না। চিঠি পেলে আবার আমাদের চিঠি লিখতে হবে, কিছু কাজ তবু জুটবে আমাদের।
মাসিমা মেসোমশায়কে প্রণাম।
আপনি তুমি দুটোই বাঁচিয়ে এর বেশি পারলাম না। এটুকুতেই রাত তিনটে বাজল। তাকিয়ে দেখি, কাটাকুটির ফাঁকে-ফাঁকে এই ক’টি কথা যেন কালো জঙ্গলে ঝিকিমিকি রোদ্দুর। বার-বার পড়লাম; মনে হ’লো বেশ হয়েছে, আবার মনে হ’লো ছি-ছি, ছিঁড়ে ফেলি এক্ষুনি। ছিঁড়ে ফেললামও, কিন্তু তার আগ ভালো একটি কাগজে নকল ক’রে নিলাম, আর পরদিন তিনজন বসিয়ে দিলাম যে যার নাম সই, চোখ বুজে ছেড়ে দিলাম ডাকে।
ঢাকা থেকে রাঁচি, রাঁচি থেকে ঢাকা। চারদিন, পাঁচদিন—আচ্ছা ছ-দিন। না, চিঠি নেই। সন্ধ্যায় কুয়াশা, একটু একটু শীত; চিঠি নেই। শিউলি ফুরিয়ে স্থলপদ্ম ফুটল; চিঠি নেই।
চিঠি এলো শেষ পর্যন্ত, হিতাংশুর নামে শীর্ণ একটা পোস্টকার্ড, লিখেছেন ওর মা। অনেকটা এই রকম :
কল্যাণীয়েষু,
হিতাংশু, অসিত, বিকাশ, তোমরা তিনজনে আমাদের বিজয়ার আশীর্বাদ জেনো। আমাদের রাঁচির মেয়াদ শেষ হ’লো, শিগগিরই ফিরব। ইতিমধ্যে, হিতাংশু তুমি যদি আমাদের ঘরগুলি খুলিয়ে তোমাদের চাকর দিয়ে ঝাঁটপাট করিয়ে রাখো, তাহলে বড় ভালো হয়। চাবি তোমার বাবার কাছে।
আশা করি ভালো আছো সকলে। তরুর শরীর এখন বেশ ভালো হয়েছে, মাঝে মাঝে সে তোমাদের কথা ব’লে। ইতি—তোমাদর মাসিমা।
মাঝে মাঝে আমাদের কথা ব’লে! আর আমাদের চিঠি? পোস্টকার্ডটি তন্ন তন্ন ক’রে খুঁজেও কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলো না যে চিঠিটা পৌঁছেছিলো। কি হ’লো চিঠির? কিন্তু সে কথা বেশিক্ষণ ভাববার সময় কই আমাদের, তক্ষুনি লেগে গেলাম কাজে। একদিনের মধ্যেই তারা-কুটিরের একতলাকে আমরা এমন ক’রে ফেললাম যে মেঝেতে মুখ দেখা যায়। কয়েকদিন পরে আর-একটি পোস্টকার্ড : ‘রবিবার ফিরছি, স্টেশনে এসো।’ শুধু স্টেশনে। আমরা ছুটলাম নারায়ণগঞ্জে।
আ, কী সুন্দর দেখলাম মোনালিসাকে, কচিপাতার রঙের শাড়ি পরনে, লাল পাড়, লালচে মুখের রং, একটু মোটা হয়েছে, একটু যেন লম্বাও। পাছে কাছে দাঁড়ালে ধরা প’ড়ে যে সে আমাকে মাথায় ছাড়িয়ে গেছে, আমি একটু দূরে দূরে থাকলাম, হিতাংশু ছুটোছুটি ক’রে বরফ লেমনেড কিনতে লাগল, আর অসিত কুলিকে ঠেলে দিয়ে বড়-বড় বাক্স-বিছানা হাই-হাই ক’রে তুলতে লাগল গাড়িতে।
মাসিমা বললেন, ‘তোমরা এ-গাড়িতেই এসো।’
‘না, না, সে কী কথা, আমরা-আমরা এই পাশের গাড়িতেই—’
‘আরে এসো না’—ব’লে দে-সাহেব অসিতের পিঠের উপর হাত রাখলেন।
নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা : মনে হ’লো আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়টি এতকাল এই পঁয়তাল্লিশটি মিনিটের জন্যই অপেক্ষা ক’রে ছিলো। ফার্স্ট ক্লাসের গদিকে অবজ্ঞা ক’রে আমরা বসলাম বাঙ্-বিছানার উপর; তাতে একটা সুবিধে এই হ’লো যে একসঙ্গে সকলকেই দেখতে পেলাম—দেখলাম মোনালিসা খুশী, ওর মা খুশী। বাবা খুশী, দেখতে-দেখতে আমরাও খুশীতে ভ’রে গেলাম; এতদিন যা বাধো-বাধো ছিলো তা সহজ হ’লো, এতদিন যা ইচ্ছে ছিলো তা মূর্ত হ’লো—রীতিমতো কলরব করতে-করতে চললাম আমরা; এতবড় রেলগাড়িটা যেন আমাদের খুশীর বেগেই চলেছে। মোনালিসা নাম ধ’রে-ধ’রে ডাকতে লাগল আমাদের—কত তার কথা, কত গল্প—আর গাড়ি যখন ঢাকা স্টেশনের কাছাকাছি, কোনো-এক ঝর্নার বর্ণনা দিচ্ছে সে, হঠাৎ আমি ব’লে উঠলাম, ‘আমাদের চিঠি পেয়েছিলে?’
‘তোমাদের চিঠি, না তোমার চিঠি?’
আমি একটু লাল হ’য়ে বললাম, ‘জবাব দাও নি যে?’
‘এতক্ষণ ধ’রে তো সেই জবাবই দিচ্ছি। বাড়ি গিয়ে আরও দেবো।’
মিথ্যো বলে নি মোনালিসা। স্বর্গের দরজা হঠাৎ খুলে গেলো আমাদের, আমরা তিনজন আমরা চারজন হ’য়ে উঠলাম।
তারপর একদিন মাসিমা আমাদের ডেকে বললেন, ‘একবার তোমরা তরুর জন্য খেটেছ, আর একবার খাটতে হবে। ঊনতিরিশে অঘ্রাণ ওর বিয়ে।’
ঊনতিরিশে! আর দশ দিন পরে!
ছুটে গেলাম ওর কাছে, বললাম, ‘মোনালিসা, এ কী শুনছি!’
ভুরু কুঁচকে বললো, ‘কী? কী বললে?’
গোপন নামটা হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় আমি একটু থমকে গেলাম, কিন্তু একবার যখন বেরিয়েই গেছে তখন আর ভয় কী! মরিয়া হলে মানুষের যে সাহস হয়, সেই সাহসের বশে আমি সোজা তাকালাম ওর চোখের দিকে, চোখের ভিতরে—যা যা আগে আমি কখনো করি নি—বেগুনি-বেগুনি কালো রঙের ওর চোখ, একফোঁটা হীরের মতো চোখের মণি—তাকিয়ে থেকে আবার বললাম, ‘মোনালিসা।’
‘মোনালিসা’ সে আবার কে?’
‘মোনালিসা তোমারই নাম’, বললো অসিত, ‘জানো না?’
‘সে কী?’
হিতাংশু বললো, ‘আর কোনো নামে আমরা ভাবতেই পারি না তোমাকে।’
‘মজা-তো—’ কৌতুকের রং লাগল ওর মুখে, মিলিয়ে গেলো, পলকের জন্য ছায়া পড়লো সেখানে, যেন একটি ক্ষণিক বিষাদের মেঘ আস্তে ভেসে গেল মুখের উপর দিয়ে। একটু তাকিয়ে রইল, চোখের পাতা দুটি চোখের উপর নামল একবার।
হঠাৎ, মুহূর্তের জন্য—কী কারণে বুঝলাম না—আমাদের একটু যেন মন-খারাপ হ’লো, কিন্তু তখনই তা উড়িয়ে দিল হাসির হাওয়া, আমাদের কথায় লাগল ঠাট্টার বুড়বুড়ি।
‘কী শুনছি? মোনালিসা, কী শুনছি?’
‘কী শুনছ বলো তো?’ ব’লে আঁচলে মুখ চেপে খিলখিল ক’রে হেসে পালিয়ে গেলো।
বর এলো বিয়ের দু’দিন আগে কলকাতা থেকে। ধবধবে ফর্সা, ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবি পরনে, কাছে দাঁড়ালে সূক্ষ্ম একটি সুগন্ধে মন যেন পাখি হ’য়ে উড়ে যায়। দেখে আমরা মুগ্ধ। হিতাংশু বারবার বলতে লাগল—’হীরেন বাবু কী সুন্দর দেখতে।’
অসিত জুড়ল—‘ধুতির পাড়টা!’
‘পা দুটো!’ বলে উঠলো হিতাংশু। ‘অমন ফর্সা পা না-হলে কি আর ও-রকম ধুতি মানায়!’
আমি ফস্ করে বললাম, ‘যা-ই বলো, ঠোঁটের কাছটা একটু বোকা-বোকা।’
‘কী! বোকা-বোকা!’ অসিত চেঁচিয়ে উঠলো, কিন্তু চিৎকার বেরোল না, কারণ লোকজন নিয়ে চ্যাঁচামেচি ক’রে-ক’রে বিয়ের অনেক আগেই সে-গলা ভেঙে ব’সে আছে। রেগে যাওয়া বেড়ালের মতো ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ ক’রে বললো, ‘এমন সুন্দর দেখেছ কখনো!’
‘মোনালিসার মতো তো নয়!’ আমি আমার গোঁ ছাড়লাম না।
‘একজন কি আর-একজনের মতো হয় কখনো! খুব মানিয়েছে দু’জনে। চমৎকার!’ ব’লে অসিত লাফিয়ে সাইকেলে উঠে বোঁ ক’রে কোথায় যেন চলে গেলো। বিয়ের সমস্ত ভারই তার উপর, তর্ক করার সময় কোথায়।
বিয়ের দিন শানাইয়ের শব্দে রাত থাকতেই আমার ঘুম ভাঙল। চোখ মেলেই মনে পড়লো সেই আর-একটি শেষ-রাত্রি, যখন মৃত্যুর হাত থেকে—তা-ই মনে হয়েছিলো তখন—মোনালিসাকে আমি ফিরিয়ে এনেছিলাম। সেদিন অন্ধকারের ভিতর থেকে একটু একটু ক’রে আলো বেরিয়ে আসা দেখতে-দেখতে যে আনন্দে আমি ভেসে গিয়েছিলাম, সেই আনন্দ ফিরে এলো আমার বুকে, গা কাঁটা দিয়ে উঠলো, শানাইয়ের সুরে চোখ ভ’রে উঠলো জলে। আর শুয়ে থাকতে পারলাম না, তারা-ভরা আকাশের তলায় দাঁড়ালাম এসে। শুনতে পেলাম বিয়েবাড়ির সাড়াশব্দ, শাঁখের ফুঁ—কাছে গেলাম। মনে হ’লো আর একবার যদি দেখতে পাই, এই ভোর হবার আগের মুহূর্তে, যখন আকাশ ঘোষণা করছে মধ্যরাত্রি আর হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ভোর—এই আশ্চর্য অপার্থিব সময়ে একটু দেখতে পাই যদি। কিন্তু না—গায়ে-হলুদ হচ্ছে, কত-কত অচেনা মেয়ে ঘিরে আছে তাকে, কত কাজ, কত সাজ—এর মধ্যে আমি তো তাকে দেখতে পাব না। বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতরকার চলাফেরা, কথাবার্তা শুনতে লাগলাম, আর সব ছাপিয়ে, সব ছাড়িয়ে শানাইয়ের সুর ঝরল, আমার চোখের সামনে কাঁপতে-কাঁপতে তারার ঝাঁক মিলিয়ে গেলো, ফুটে উঠলো মাঠে মাঠে গাছপালার চেহারা, মাটির অবয়ব, পৃথিবীতে আর একবার ভোর হলো।
সেদিনে অসিতের গলা একেবারেই ভেঙে গিয়ে নববধূর মতো ফিসফিসে হ’লো। এত ব্যস্ত সে, আমাকে যেন চেনেই না। হিতাংশুও ব্যস্ত, ব্যস্ত এবং একটু গর্বিত, কেননা বর সদলে বাসা নিয়েছেন তাদেরই বাড়ির দুটো ঘরে, একতলা দোতলায় দূতের কাজ করতে-করতে সে স্যান্ডেল ক্ষইয়ে ফেলল। আমি একবার হিতাংশুকে, একবার অসিতকে সাহায্য করার চেষ্টা করলাম সারাদিন ভ’রে, কিন্তু আমার নিজের মনে হ’লো না বিশেষ-কোনো কাজে লাগছি, আর শেষ পর্যন্ত যখন বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে কনেকে সাতপাক ঘোরাবার সময় এলো, তখনও আমি এগিয়ে গেলাম, কিন্তু আমাকে ঠেলে দিয়ে অসিত আর হিতাংশুই পিঁড়ি তুলল, দু’হাতে দু’জনের গলা জড়িয়ে ধ’রে ও সাত পাক ঘুরল, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম।
বিয়ের পরদিন থেকেই আমরা তিনজন হীরেন বাবুর চাকর বনে গেলাম। তাঁর মতো সুন্দর কেউ না, তাঁর মতো বিদ্যেবুদ্ধি কারো নেই, তাঁর মতো ঠাট্টা কেউ করতে পারে না। অন্য পুরুষদের বাঁদর মনে হ’লো তুলনায়—আমারও আর মনে হ’লো না যে তাঁর ঠোঁটের কাছটা একটু বোকা-বোকা। এমনকি, আমি চেষ্টা করতে লাগলাম তাঁর মতো ক’রে বসতে, দাঁড়াতে, হাঁটতে, হাসতে, কথা বলতে; ওরা দু’জনও তা-ই করলো, আবার তা দেখে হাসি পেলো আমার, হয়তো প্রত্যেকেই আমরা অন্য দু’জনের চেষ্টা দেখে হেসেছি মনে-মনে, যদিও মুখে কেউ কিছু বলি নি।
একদিন দুপুরবেলা হীরেনবাবুর কাছে খুব একটা মজার গল্প শুনছি, তিনি একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, ‘দ্যাখো তো ভাই, তরু গেলো কোথায়।’
‘ডেকে আনব?’ ব’লে আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম।
দক্ষিণের বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়ে ব’সে মোনালিসা চুল আঁচড়াচ্ছে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভুলে গেলাম। হঠাৎ যেমন নতুন লাগল তাকে, একটু অন্যরকম সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, পরনে কড়কড়ে শাড়ি, কানে হাতে গলায় চিকচিকে গয়না, আর কেমন একটা গন্ধ দিচ্ছে গা থেকে—হীরেনবাবুর সেন্টের গন্ধ না, নতুন ফার্নিচারের মদ-মদ গন্ধ না, চুলের তেল কি মুখের পাউডারেরও না—আমার মনে হ’লো এই সমস্ত মিলিত গন্ধের যেটা নির্যাস, সেটাই ভর করেছে মোনালিসার শরীরে। জোরে নিশ্বাস নিলাম কয়েকবার, মাথা যেন ঝিমঝিম ক’রে উঠলো।
চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, ‘কী?’
‘কিছু না’—সঙ্গে সঙ্গে কাজের কথাটা মনে পড়লো, ‘হীরেনবাবু ডাকছেন তোমাকে।’
আমার কথাটা যেন শুনতেই পেলো না মোনালিসা, নিশ্চিন্তে চুলই আঁচড়াতে লাগল।
‘শুনছ না কথা! হীরেনবাবু ডাকছেন তোমাকে।’
‘ডাকছেন তো হয়েছে কী। উনি ডাকলেই যেতে হবে?’
‘বাঃ—!’
চিরুনি থামিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো—‘আর কী—চলেই তো যাব শিগগির।’
আমি বললাম, ‘কত ভালো লাগবে তোমার কলকাতায় গিয়ে—ঢাকা কি একটা জায়গা!’
‘ঢাকা খুব ভালো।’ ঘাড় বেঁকিয়ে বাইরের দিকে তাকালো, একটু, শীতের দুপুরের সবুজ-সোনালি মাঠের দিকে। সেদিকে তাকিয়েই আবার বললো, ‘তোমরা আমাকে মনে রাখবে, বিকাশ?’
আমি ব্যস্ত হ’য়ে বললাম, ‘আর কথা না। চলো এখন।’
‘দেখছো না চুল আঁচড়াচ্ছি। বলো গিয়ে এখন যেতে পারবো না।’
কথা শুনে প্রায় ভড়কে গিয়েছিলাম, কিন্তু একটু পরেই মোনালিসা উঠলো, তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও এলাম ঘরে। এসেই বললাম, ‘তারপর? সেই লোকটার কী হ’লো, হীরেনবাবু?’
কিন্তু হীরেনবাবুর গল্প বলার উৎসাহ দেখি মিইয়ে গেছে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি, আর মোনালিসা চেয়ারে ব’সে টেবিলের কাপড় খুঁটতে লাগল।
আমি পীড়াপীড়ি করলাম, ‘বলুন না কী হ’লো!’
‘এখন থাক।’
আমি খাটে ব’সে একটি ইংরেজি বইয়ের পাতা উল্টিয়ে বললাম, ‘এটা পড়েছি, ভারি মজার বই।’
হীরেনবাবু হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আর-একটি বই টেনে নিয়ে বললেন, ‘এ-বইটাও ভারি মজার। এক কাজ করো তুমি—এটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে প’ড়ে ফ্যালো, আমি চট ক’রে একটু ঘুমিয়ে নিই। কেমন?’ বলতে-বলতে তিনি একেবারে উঠে দাঁড়ালেন।
আর কথা না-ব’লে আস্তে বেরিয়ে এলাম আমি, পিঠ দিয়ে অনুভব করলাম ও-ঘরের দরজা বন্ধ হ’য়ে গেলো। বাড়ি গেলাম না; বারান্দায় যেখানে ও ব’সেছিলো ঠিক সেখানটায় ব’সে পড়লাম। ওর চুলের গন্ধমাখা চিরুনিটা সেখানেই প’ড়ে ছিলো, হাতে তুলে নিয়ে দাঁতগুলির উপর আস্তে আস্তে আঙুল চালাতে লাগলাম, বার-বার, বার-বার।
আরো একদিন, আরো একদিন। যাবার দিন এলো, পেছোল, আর-একটা একটা দিন শুধু; তারপর চলে গেলো।
চিঠি এলো এবার, তিনজনের কাছে একখানা, চিঠি, মোটা নীল খামে, আমার নামে! তিনজনের হ’য়ে জবাব লিখলাম, আমি, একটু লম্বাই হ’লো, সেই সঙ্গে একটা কবিতাও লিখে ফেললাম, সেটা অবশ্য পাঠালাম না। চিঠি বন্ধ হ’য়ে গেলো শিগগিরই, তারপর শুধুই কবিতা লিখতে লাগলাম, দেখতে দেখতে খাতা ভ’রে উঠলো!
মাসিমার কাছে খবর পাই সবই। ভালো আছে ওরা, খুব ভালো আছে। হীরেন গাড়ি কিনেছেন, সেদিন ওরা আসানসোল বেড়িয়ে এলো। কলকাতায় কথা-বলা সিনেমা দেখাচ্ছেন, টোম্যাটোর সের এক পয়সা, তবে শীত কমে গেছে, হঠাৎ অসুখ-বিসুখ দেখা না দেয়। আর-একটু গরম পড়লেই ওরা চলে যাবে দারজিলিং।
না-দেখা দারজিলিং-এর ছবি দেখতে লাগলাম, মনে-মনে, কিন্তু সে-ছবি মুছে দিয়ে মাসিমা একদিন বললেন, ‘ওরা তো আসছে।’
আসছে! এখানে! ঢাকায়। দারজিলিং-এর কী হ’লো? আমাদের নীরব প্রশ্নের উত্তরে বললেন, ‘শরীরটা খারাপ হয়েছে ওর, আমার কাছেই থাকবে এখন।’
‘কী? অসুখ করেছে আবার?’ চমকে উঠলাম তিনজনে।
‘না, অসুখ ঠিক না, শরীরটা ভালো নেই আর কি’, মাসিমা মৃদু হাসলেন।
খুব খারাপ লাগল। খারাপ লাগল মাসিমার কথা শুনে, হাসি দেখে। শরীর ভালো না, অথচ অসুখও না—এ আবার কী-রকম কথা? আর মাসিমা কেমন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ,—যেন খুশীই হয়েছেন খবর শুনে। রীতিমতো রাগ হ’লো মনে মনে।
ওরা পৌঁছোবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা তিন মূর্তি গিয়ে হাজির হলাম। মোনালিসা সোফায় ব’সে আছে একটু এলিয়ে, হাতে সিগারেটের টিন। চকিতে আমরা তিনজন মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলাম—হীরেনবাবু কি সিগারেট ধরিয়েছেন ওকে?
আমাদের দেখে ফিকে একটু হাসলো। কথা বললো না।
‘কেমন আছো মোনালিসা?’ আমরা চেষ্টা করলাম স্ফূর্তির সুর লাগাতে।
সিগারেটের টিনটা মুখের কাছে এনে তার সঙ্গে একবার মুখ ঠেকিয়ে ডালা বন্ধ ক’রে বললো, ‘এই—’
‘তোমার নাকি অসুখ?’
সে-কথার কোনো জবাব না-দিয়ে বললো, ‘তোমাদের কী খবর?’ তারপর আস্তে আস্তে এটা-ওটা গল্প করতে লাগল, আর সিগারেটের টিনটা মুখে তুলতে লাগল ঘন ঘন।
হীরেনবাবু ঘরে এসে ব্যস্তভাবে বললেন, ‘তরু এখন কেমন আছো?’
ক্লান্ত চোখ তুলে বললো, ‘ভালো।’
‘তুমি বরং একটু শোও।’
‘না, এই বেশ আছি।’
‘এই যে তোমরা এসেছো দেখছি। তরু তো এদিকে—’ হঠাৎ থেমে গেলেন হীরেনবাবু।
‘হয়েছে কী ওর?’
‘হয় নি কিছু, তবে…’
তবে কী? ওর কী এমন সাংঘাতিক কোনো অসুখ করেছে যা কারো কাছে বলাও যায় না? আর ও যেন কেমন হ’য়ে গেছে, যেন আধ-মরা, আস্তে কথা ব’লে, একভাবে স্থির হ’য়ে ব’সে থাকে, হাসি পেলে ভালো ক’রে হাসেও না। মায়েদের মুখে শুনেছি যে বিয়ের পরে মেয়েদের শরীর আরো ভালো হয়, কিন্তু আমাদের মোনালিসার নাকি এই হ’লো?
ছোট একটা প্লেট হাতে ক’রে মাসিমা এসে বললেন, ‘এটা একটু মুখে দিয়ে দ্যাখ তো?’
‘কী, মা?’
‘দ্যাখ না—’ ব’লে তিনিই আঙুল দিয়ে মুখে গুঁজে দিলেন।
‘না, না, আর না—’, মোনালিসার মুখে কষ্টের রেখা ফুটে উঠলো, গলার কাছটায় হাত রেখে মুখ নিচু করলো সে।
বেরিয়ে এসে খানিকক্ষণ নিঃশব্দ হাঁটলাম আমরা, মন বিষণ্ন খুবই। হঠাৎ অসিত বললো, ‘ও বার-বার থুতু ফেলছিলো সিগারেটের টিনে।’
‘যাঃ!’ আমি আঁতকে উঠলাম।
‘সত্যি! আমি দেখলাম!’
হিতাংশু বললো, ‘তা হলে এটাই বোধহয় ওর অসুখ।’
‘অসুখ না’, অসিত গম্ভীরভাবে বললো, ‘ওর ছেলে হবে।’
শুনে হিতাংশুটা খুকখুক ক’রে হেসে উঠলো।
‘হাসছো কেন?’—আমি রেগে গেলাম—‘হাসবার কী আছে এতে?’
অসিত বললো, ‘ঐ জন্যেই তো টক এনে দিলেন মাসিমা। এ-রকম হলে টক খেতে ভালো লাগে।’
‘তুমি সবই জানো!’ রাগে গর্জে উঠলাম আমি।
‘হ’লো কী তোমার?’ অসিত যেন সকৌতুকে আমার দিকে তাকালো।
‘যাও! কিছু ভালো লাগছে না আমার, আমি বাড়ি যাই।’ ওদের ত্যাগ ক’রে একা ফিরে এলাম বাড়িতে, বেলা শেষের আলোয় একটা বই খুলে পড়তে ব’সে গেলাম।
হীরেনবাবু ফিরে গেলেন দু’দিন পরেই। দুপুরবেলা গাড়ি। ঘোড়ার গাড়িতে মাল তোলা হ’লো : হীরনেবাবু উঠতে গিয়ে থমকালেন। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, ‘কিছু ফেলে এসেছেন, নিয়ে আসবো?’
‘না, না, আমি যাচ্ছি।’
তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে গেলেন তিনি, ফিরে এসে কোনোদিকে না তাকিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। চাবুকের শব্দ হ’লো। অসিত সাইকেলে উঠলো—স্টেশনে যাবে সে। হিতাংশু গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, ‘কবে আসবেন আবার?’
‘আসবো—তোমরা দেখো ওকে’, ব’লে হীরেনবাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমার মনটা হু হু ক’রে উঠলো।
কী স্তব্ধ সেই দুপুরবেলা, কী-রকম ছবির মতো সুন্দর, সেই উনিশ-শো-আটাশ সনে, পুরানা পল্টনের ফাল্গুন মাসে! ঘোড়ার গাড়ি আর অসিতের সাইকেল, ছোট হ’তে-হ’তে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হ’লো; আমি আর হিতাংশু ভেতরে এলাম। বালিশে মুখ গুঁজে মোনালিসা ফুলে ফুলে কাঁদছে।
‘মোনালিসা!’
‘শোনো, কথা শোনো।’
‘হীরেনবাবু আবার তো আসবেন—’
‘এরপর ওঁকে আর যেতেই দেব না আমরা!’
‘আর না—আর কেঁদো না, মোনালিসা, তোমার পায় পড়ি।’ থামল না কান্না। আমি মেঝেতে ওর কাছে হাঁটু ভেঙে ব’সে পড়লাম, ওর মাথায় হাত রেখে গুনগুন ক’রে বলতে গেলাম, ‘আর না, আর কাঁদে না, একটু থামো, একটু চুপ ক’রো মোনালিসা!’ হঠাৎ গলা ভেঙে গিয়ে আমিও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।
একটু পরে মোনালিসা আমাকে ঠেলা দিয়ে বললো, ‘এই—কাঁদছ কেন? বোকা!’ আমি দু’হাতে মুখ ঢেকে থাকলাম, আমাকে চুলে ধ’রে ঝাঁকানি দিয়ে আবার বললো, ‘পুরুষমানুষ—কাঁদতে লজ্জা ক’রে না। থামো এক্ষুনি!’
আমি হাত সরিয়ে ভেজা চোখে তাকালাম। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সুখে আমার বুক কেঁপে উঠলো, তারপর সারাদিন ধ’রে একটু একটু কাঁপল, রাত্রে ঘুমের মধ্যেও ভুলতে পারলাম না।
আমরা তিনজন ওকে ঘিরে রইলাম। ও যাতে ভালো থাকে, কখনো মন খারাপ না ক’রে। হঠাৎ এক-একটা অদ্ভুত জিনিষ ওর খেতে ইচ্ছা ক’রে, অসিত শহর ঢুঁড়ে তা জোগাড় ক’রে আনে। দেখেই ওর ইচ্ছে চলে যাবে, জানা কথা; কবে আবার নতুন ইচ্ছে হবে সেই আশায় থাকি আমরা। আর যদি কখনো একটু খায়, খেয়ে ভালো ব’লে, তাহলে তো কথাই নেই—আহ্লাদে আমরা হাবুডুবু।
হীরেনবাবুর চিঠি আসতে দেরি হলেই আমরা বলি, উনি হঠাৎ এসে অবাক ক’রে দেবেন ব’লেই চিঠি লিখছেন না। কথাটা ঠিক নয় জেনেও প্রতিবারেই মোনালিসার মুখ উজ্জ্বল হ’য়ে ওঠে। আমরা চুপ ক’রে উপভোগ করি।
হীরেনবাবু এলেন তিন মাস পরে। ততদিন ওর শরীরটা অনেকটা সেরেছে, খায়, বেড়ায়, ফেরিওলা ডেকে কাপড় কেনে, চেহারাও ভারী হয়েছে একটু। এবারে দিন দশেক থাকলেন তিনি, তারপর পুজোর সময় এসে এক মাস কাটালেন।
ততদিন ওর শরীর আবার খারাপ হচ্ছে। ডাক্তার আসছেন ঘন-ঘন, ওষুধ দিচ্ছেন, কিন্তু যা শুনি তাতে মনে হয় কিছুই উপকার হচ্ছে না। কী কষ্ট জানি না, বুঝি না, শুধু চোখে দেখতে পাই;—চোখে কালি পড়েছে, দু’টো কথা বললেই হাঁপিয়ে প’ড়ে, মুখটা এক-এক সময় নীল হ’য়ে যায়। আমরা কাছে কাছে ঘুরঘুর করি, শুয়ে থাকলে হাওয়া করি হাতপাখায়, কখনো একটু ভালো দেখলে হাসি-ঠাট্টায় ভোলাতে চাই—কিছুই পারি না।
একদিন আমি বললাম, ‘বাবর নিয়েছিলেন হুমায়ুনের অসুখ, ও-রকম পারলে বেশ হ’তো।’
অসিত হো হো ক’রে হেসে উঠলো—’আর যাই পারো, ওর এ-অসুখটা তুমি নিতে পারবে না!’
লাল হ’য়ে বললাম, ‘অসুখ না, অসুখের কষ্ট।’
হিতাংশু বললো, ‘কী কষ্ট, সত্যি! সারারাত নাকি পায়চারি ক’রে—ঘুমোতে পারে না, শুতেও নাকি কষ্ট হয়।’
অসিত বললো, ‘হবে না, দেখতে কীরকম হয়েছে দেখেছ!’
আমি ঝাঁঝিয়ে উঠে বললাম, ‘কীরকম আবার হবে! সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর।’
‘যত সুন্দরই হোক, এই শেষের সময়টা…’
আর-এক পরদা গলা চড়িয়ে বললাম, ‘এই সময়টাই তো সবচেয়ে সুন্দর!’
সত্যিই তাই, আমার চোখে সত্যিই তা-ই দেখলাম। দিন যত কাটল, তত ওকে আরো বেশি সুন্দর দেখলাম আমি, ওর সমস্ত শরীর এক অসহ্য সৌন্দর্যে ভরপুর হ’য়ে উঠলো আমার চোখে। একদিন ওকে না-ব’লে পারলাম না সে-কথা। আগের বছর যেদিনে ওরা রাঁচি থেকে ফিরেছিলো, যেদিন রেলগাড়ির একটা ছোট কামরায় সমস্ত স্বর্গ ধ’রে গিয়েছিলো, ঠিক সেইরকম একটি শীতের আমেজ-লাগা দিনে হঠাৎ ও বললো, ‘বিকাশ তোমার হয়েছে কী বলো তো? বড্ড আজকাল তাকিয়ে থাকো আমার দিকে!’
আমি একটুও লজ্জিত না হ’য়ে জবাব দিলাম, ‘তুমি আজকাল খুব সুন্দর হয়েছ কি না, তাই।’
‘আগে বুঝি সুন্দর ছিলাম না?’
‘এখনকার মতো না!’
‘তাই বুঝি?’ মোনালিসা ভুরু কুঁচকে বাইরে মাঠের দিকে তাকালো। একটু চুপ ক’রে থেকে বললো, ‘সত্যি আমাকে ভালোবাসো তোমরা। কিন্তু ও-রকম ক’রে আর তাকিয়ো না, ভারি অসুবিধে লাগে আমার।—ইস্, কী রোদ!’
আমি উঠে সামনের জানালাটা ভেজিয়ে দিলাম।
‘একটু ঘুমিয়ে নিই কেমন?’
পায়ের কাছে একখানা চাদর ছিলো, ভাঁজ-করা, খুলে গায়ের উপর ছড়িয়ে দিতে-দিতে বললাম, ‘আজকাল তুমি বেশ ভালো আছো, না?’
‘আমি তো ভালোই আছি।’
ওর মুখে দেখলাম সাহসের সঙ্গে আশা, আশার সঙ্গে ভয়, ভয়ের সঙ্গে ধৈর্য। পায়ের পাতা দুটির উপর থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে বললাম, ‘হীরেনবাবু চলে গেলেন কেন?’
‘বা রে! ওর বুঝি কাজকর্ম নেই?’
‘কবে আসবেন আবার?’
‘আসবেন সময়মতো।’
‘কী দরকার ছিলো যাবার—আমার মোটেও ভালো লাগে না!’
‘হয়েছে হয়েছে, আর সর্দারি করতে হবে না’—বলে পাশ ফিরে চোখ বুজল। বোজা চোখেই ব’লে নিলো, ‘আমি কিন্তু ঘুমোলাম’, এবং বলবার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লো। আহা, রাত্তিরে ঘুমোতে পারে না, কত ক্লান্তি ওর শরীরে! মনে-মনে বললাম—কার কাছে বললাম জানি না—ওর ভালো হোক, ওর ভালো হোক।
রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনে হ’লো ও হয়তো এতক্ষণ ছটফট করছে কষ্টে, উঠে পায়চারি করছে ঘরের মধ্যে, আর বাইরে শেয়াল-ডাকা অন্ধকার, আর আকাশে এখনো সাত-আট ঘণ্টা রাত্রি। কেন আমি কিছু করতে পারি না, কেন এক্ষুনি যেতে পারি না ওর কাছে, কোনো অলৌকিক উপায়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি না ওকে? চোখের উপর কষ্ট দেখতে হবে, কিছু করা যাবে না, এই কি মানুষের ভাগ্য? সত্যি কি আমাদের হাত-পা বাঁধা, কোনো উপায় নেই? ভাবতে ভাবতে ঘুম ছুটল চোখের, কবিতার লাইন মনে এলো, উঠে বসতেই চোখে পড়লো ছায়া-ছায়া জ্যোৎস্না ফুটেছে বাইরে, আমার জানালা দিয়ে আবছা দেখা যাচ্ছে তারা-কুটির স্বপ্নের মতো। বেশিক্ষণ তাকালাম না, লণ্ঠন জ্বেলে কেরোসিনের গন্ধে আর মশার কামড়ে ব’সে ব’সে কবিতা বানাতে লাগলাম।
রোজ হ’তে লাগল এ-রকম, আমার রাত্রি থেকে ঘুম প্রায় চলে গেলো। আমিও জেগে আছি ওর সঙ্গে-সঙ্গে, আমি ওর প্রহরী, সকল দুঃখ থেকে আমি বাঁচাব ওকে—এ কথা ভাবতে-ভাবতে দেবতা মনে হ’লো নিজেকে, কবিতায় এমন সুন্দর সুন্দর কথা এলো যে নিজেই অবাক হলাম।
এমনি এক রাত্রে—রাত তখন দুটো প্রায়—লিখতে লিখতে হঠাৎ আমার হাত কেঁপে একটা অক্ষর বেঁকে গেলো। শুনলাম বাইরে কে ডাকছে আমাকে, ‘বিকাশ বিকা—শ!’ একটু অপেক্ষা করলাম, আবার শুনলাম চাপা গলার ডাক। আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখি, ওরা দু’জন ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে।
সে রাত্রে তখনও চাঁদ ওঠেনি, সারা রাত্রেও বোধহয় ওঠেনি, অমাবস্যার কাছাকাছি রাত সেটা। আকাশ ছিলো তারায় ঝকঝকে, তারই ধুলোর মতো আলোয় আমরা তিনজন দাঁড়ালাম—শীতের রাত্রি, মাঠের মধ্যে, ঢিপঢিপ বুকে।
‘কী, অসিত? হিতাংশু কী খবর?’
‘আরম্ভ হয়েছে বোধহয়’, কথা বললো হিতাংশু।
‘আরম্ভ হয়েছে?’
‘একতলায় শুনলাম চলাফেরা, কথাবার্তা, আর চাপা একটা গোঙানি। ঘুমের মধ্যেই যেন শুনলাম, তারপর আর বিছানায় থাকতে পারলাম না। অসিতকে ডেকে তুলে তোমার কাছে এলাম। তুমি কি জেগেই ছিলে?’
আমি কথা বললাম না, তারার আলোয় দেখলাম হিতাংশুর মুখ শাদা হ’য়ে গেছে, আর অসিত মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে দূরের দিকে। এ-কদিনে আমরাও যেন বদলে গিয়েছিলাম; হাসি, ঠাট্টা, ঘোরাঘুরি কমে গিয়েছিলো আমাদের, বেশি কথা বলতাম না, আর এতদিন ধ’রে যে-মানুষকে নিয়ে লক্ষ কথা আমরা বলেছি, তার সম্বন্ধে একেবারে নীরব হ’য়ে গিয়েছিলাম। রুদ্ধশ্বাস আমরা, প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস।
আমরা বুঝলাম না যে আমরা কাঁপছি, জানলাম না যে আমরা হাঁটছি, কখন বাগানের ছোট গেট খুলে এসে সিঁড়ির তলায় দাঁড়ালাম। নিশ্চয়ই আমরা কোনো শব্দ করি নি, কোনো কথাও বলি নি, কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দে-সাহেব টর্চ হাতে বেরিয়ে এলেন, যেন আমাদেরই অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ। নিচুগলায় বললেন, ‘অসিত, একবার যাও তো সাইকেলটা নিয়ে ডক্টর মুখার্জির কাছে—একেবারে সঙ্গে ক’রে নিয়ে আসবে তাঁকে।’
অন্ধকারে হাওয়ার মতো মিলিয়ে গেলো অসিত। আমি আর হিতাংশু সিঁড়ির উপরেই ব’সে পড়লাম। একটা কান্না, চাপা একটানা, আমাদের পিঠ ফুঁড়ে বুকের মধ্যে ঢুকলো, তার যেন আওয়াজ নেই, শুধু কষ্ট আছে, যেন পৃথিবীর প্রাণে আঘাত দিয়েছে কেউ, পৃথিবীর বুক থেকে এই কান্না উঠছে, তাই কোনোদিন থামবে না।
ওকে চোখে দেখতে পারি না আমরা, দূর থেকেও না; ও-ঘরে যেতে পারি না আমরা, ঘরের কাছেও না। শুধু বাইরে ব’সে থাকতে পারি, শীতে, অন্ধকারে, না-জেগে, না-ঘুমিয়ে, আকাশের সামনে, অদৃষ্টের মুখোমুখি।
ডাক্তারের আনাগোনা শুরু হ’লো, চললো বাকি রাত ভ’রে, চললো তার পরের দিন। ভোর হ’তেই চড়া মাশুলের টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম হীরেনবাবুকে—মনে মনে ভাবলাম, টেলিগ্রাম যত দ্রুতই ছুটে যাক, তার চেয়েও দ্রুতবেগে ছুটে আসুক হীরেনবাবুর মন, কাল বিকেলের আগে তিনি পৌঁছতে পারবেন না কিছুতেই—কী অসহায় মানুষ, কী নিরুপায়! ডাক্তার, নার্স, ওষুধ, ইনজেকশন, পরিশ্রম, প্রার্থনা;—তবু অসহায়, তবু মানুষ অসহায়—কী হচ্ছে, কী হ’লো, কী হবে, এসব প্রশ্নের উত্তর নেই কারো চোখে, ডাক্তারের মুখ পাথরের মতো, ওর মা-বাবার মুখে সংক্ষিপ্ত ফরমাশ ছাড়া আর-কোনো কথা নেই, মাসিমা আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি পর্যন্ত ক’রেন না, আর দে-সাহেবের পরিপাটি চেহারাটির তলায় একজন কোঁকড়ানো বুড়োমানুষ যে লুকিয়ে ছিলো তা কে জানতো! কে জানতো আকাশের নীল নরম ঘোমটার তলায় এই কান্না লুকিয়ে আছে! আর আমাদের কি আর কিছু নেই, আর কিছু করবার নেই, শুধু কান পেতে এই কান্না শোনা ছাড়া?
দুপুরের আগেই বিকেল হ’য়ে গেলো সেদিন, বিকেলের আগেই অন্ধকার। তারপর, রাত যখন একটু ভারি হয়েছে, হঠাৎ যেন পৃথিবীর বুক চিরে চিৎকার উঠলো একটা; উঠলো, পড়লো, আবার উঠলো আকাশের দিকে; আকাশ চুপ, তারাদের নড়চড় হ’লো না; আবার উঠলো চিৎকার, যেন প্রতিমার সামনে ছাগশিশুর আর্তরব, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বিরামহীন। আমরা ছুটে চলে গেলাম বাইরে, মাঠের মধ্যে, কিন্তু যতদূর সে-শব্দ চলে আমাদের, মাতা পৃথিবীর আদিম কান্না এটা, এ থেকে নিস্তার কোথায়?
ফিরে এলাম। ভিতরে আলো, ব্যস্ততার ঢেউয়ের পর ঢেউ, ফাঁকে ফাঁকে ডাক্তারের মোটা গলা, আর বাইরে অফুরন্ত তারা, অসীম অন্ধকার, অপরূপ রাত্রি, কিন্তু পৃথিবীর কান্না তো থামে না।
যে-তারা ছিলো মাথার উপরে নেমে এলো পশ্চিমে, যে-তারা ছিলো চোখের বাইরে উঠে এলো দিগন্তের উপরে, পুবের কালো ফিকে হ’লো, ছোট ছোট অনেক তারা মুছে গিয়ে মস্ত সবুজ একলা একটি তারা জ্বলজ্বল করতে লাগল সেখানে। এই সেই অপার্থিব মুহূর্ত, সেই অলৌকিক লগ্ন, যখন আমি জেগে উঠে বাইরে এসেছিলাম ওর বিয়ের দিন, যখন আমি ওকে পেয়েছিলাম মৃত্যুর হাত থেকে, অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে একটিমাত্র ভেসে চলা আলো-জ্বলা নৌকায়। অন্তত একমুহূর্তের জন্য সেদিন সে আমার হয়েছিলো, আজ কি আবার এলো সেই মুহূর্ত?
অসিত ফিসফিস ক’রে বললো, ‘কী হ’লো?’
হিতাংশু বললো, ‘কই, না!’
‘সব যেন চুপ?’
‘তাই তো।’
‘যাব একবার ভেতরে?’ অসিত উঠে দাঁড়াল, কিন্তু গেলো না। অনেক, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমরা, কিন্তু আর কোনো শব্দ নেই, সব স্তব্ধ, তারপর হঠাৎ দেখি দে-সাহেব আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভোরের প্রথম ছাইরঙা আলোয় দেখলাম তাঁর ঠোঁট নড়ে উঠলো, এমন স্থির হ’য়ে আমরা তাকিয়েছিলাম আর এমন স্তব্ধ চারদিক যে তাঁর কথাটা আমরা কানে না-শুনে যেন চোখ দিয়ে দেখলাম :
‘এসো তোমরা, ওকে দেখবে।’
অসিত আর হিতাংশুই সব করলো, রাশি রাশি ফুল নিয়ে এলো কোথা থেকে, আরো কত কিছু বেলা দু’টো পর্যন্ত শুধু সাজাল শুধু সাজাল, তারপর নিয়ে যাবার সময় সকলের আগে রইল ওরা দু’জন। আরো অনেকে এলো কাঁধ দিতে, শুধু আমি বেঁটে ব’লে বাদ পড়লাম, পিছনে পিছনে হেঁটে চললাম একা-একা। ঠিক একা-একাও নয়, কারণ ততক্ষণ হীরেনবাবু এসে পৌঁছেছেন, গাড়ির কাপড়ে জুতো-ছাড়া পায়ে তিনিও চললেন আমার পাশে পাশে।
হীরেনবাবু পরের বছর আবার বিয়ে করলেন, দে-সাহেব চলে গেলেন বদলি হ’য়ে। কিছুদিন পর্যন্ত লোকেরা বলাবলি করলো ওঁদের কথা, তারপর তারা-কুটিরের একতলায় অন্য ভাড়াটে এলো, পুরানা পল্টনে আরও অনেক বাড়ি উঠলো, ইলেকট্রিক আলো জ্বললো। অসিত স্কুল থেকে বেরিয়ে চাকরি নিলো তিনসুকিয়ায়, ছ-মাসের মধ্যে কী একটা অসুখ ক’রে হঠাৎ মরে গেলো। হিতাংশু এম.এস.সি. পাস ক’রে জার্মানিতে গেলো পড়তে আর ফিরল না, সেখানকারই একটা মেয়েকে বিয়ে ক’রে সংসার পাতল, এখন এই যুদ্ধের পরে কেমন আছে, কোথায় আছে কে জানে। আর আমি—আমি এখনো আছি, ঢাকায় নয়, পুরানা পল্টনে নয়, উনিশ-শো সাতাশে কি আটাশে নয়, সে-সব আজ মনে হয় স্বপ্নের মতো, কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু স্বপ্ন, ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে একটু হাওয়া—সেই মেঘে-ঢাকা সকাল, মেঘ-ডাকা দুপুর, সেই বৃষ্টি, সেই রাত্রি, সেই—তুমি! মোনালিসা, আমি ছাড়া আর কে তোমাকে মনে রেখেছে!

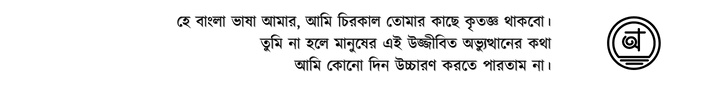

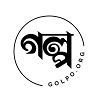

0 মন্তব্যসমূহ