আমি কখনো কখনো মজা পেয়ে ভাবি যে রবীন্দ্রনাথ ‘সোনার তরী’র একটি কবিতায় কেমন করে বাদলার দিন কাটানো যায় জানাতে গিয়ে যেখানটায় ছোটগল্প সম্বন্ধে লিখেছেন, সেখানে ‘নিতান্তই সহজ সরল’ না লিখে যদি ‘নিতান্তই সরল সহজ’ লিখতেন তাহলে নিশ্চয়ই ছন্দের ভুল হতো না। কিন্তু যা হতো তা এই যে ‘তারি দু-চারিটি অশ্রুজল’ এই ছত্রটি মিলের খাতিরে আর লিখতে পারতেন না। কারণ ‘সরল’-এর সঙ্গে ‘অশ্রুজল’ মেলে, ‘সহজের’ সঙ্গে মেলে না। সেক্ষেত্রে ছোটগল্প বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বহু উদ্ধৃত বহু খ্যাত ঋষিবাক্যের মূল বক্তব্য কি একই থাকত? সম্ভব বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সংজ্ঞা কি তাহলে আপতিক? নেহাৎ পদ্য মেলানো ছাড়া আর কিছু নয়?
সত্যিই সমিল পদ্যে কথাবার্তা বলা খুবই কঠিন। বাংলাভাষায় এক-একটা শব্দের তো খুব মিল পাওয়া যায় না—কাজেই মিলের ছোট গণ্ডির মধ্যে বাধ্য হয়ে বক্তব্যকে ছেঁটে-কেটে মাপমতো করে ঢুকিয়ে দিতে হয়। মিলের নিয়ম স্বীকার করলে রবীন্দ্রনাথের মতো বড় কবির পক্ষেও অতিক্রম করা সম্ভব নয়। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বিষয়ক ছত্র ক’টিকে আমি গভীর সন্দেহের চোখে দেখে থাকি। রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞা মানি কিনা, কোনো সংজ্ঞাই আসলে মানি কিনা, সে-প্রশ্ন এখানে উঠছে না। প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে রবীন্দ্রনাথ মিলের জাল ফেলে এক-এক খেপে তাঁর মনের কথার সমস্তটাই তুলে আনতে পেরেছিলেন, না জালে যতটুকু আটকাচ্ছিল ঠিক ততটাই হাজির করেছিলেন? আসলে কিন্তু ‘গল্পগুচ্ছ’-এর অফুরন্ত ঐশ্বর্যের অন্যমনস্ক অনুসন্ধান করলেও দেখা যায়, রচনার নিজস্ব তীব্র বেগ আর মানুষের চাপ নিয়ে সব লেখকের মতোই রবীন্দ্রনাথও হিমশিম খাচ্ছেন। সংজ্ঞা মিলিয়ে লেখার কথাই ওঠে না, রবীন্দ্রনাথের মতো বড় লেখকের পক্ষে নয়ই—এমনকী তিনি নিজের সংজ্ঞা বানালেও নয়। লেখকমাত্রেরই নিজের নিজের অরণ্য আছে। একেবারে একা তাঁকে মানুষের, প্রকৃতির, ইট-কাঠ-লোহার ঘরবাড়ি বুনো জঙ্গলে ঢুকে পড়তে হয়। কাটছাঁট করা, পথ কাটা, মাপজোক চালানো সবই তার একার কাজ।
রবীন্দ্রনাথ যে-গল্পগুলি লিখেছেন—সংখ্যা তাদের কম নয়, একশোরও বেশি—সেগুলির সঙ্গে রাবীন্দ্রিক সংজ্ঞার যোগ কতটা? প্রতীকী অর্থে একটু স্যাঁৎসেঁতে ভালোবাসার সঙ্গে যে-ছোট প্রাণ, ছোট দুঃখ ইত্যাদির কথা তিনি বলেছিলেন, হয়তো তাঁর গল্পে সে-সব আছে—তবে বড় বড় দুঃখের কথাও কম নেই। আর ‘নিতান্তই সহজ সরল’ বলা তো কিছুতেই ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথের বহু গল্পে যে মারাত্মক জটিল প্যাঁচ ও তীব্র ঘূর্ণি আছে তা বলাই বাহুল্য। তাঁর ছোটগল্পের জগতে সকালের উজ্জ্বল আলোও যেমন আছে—তেমনিই আছে মেঘ-ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুতের আকাশ। মানুষের সংসারের প্রায় সবই পাওয়া যায় তাঁর লেখায় তাঁর নিজের মতো করে। এই বৈভবের সামনে দাঁড়িয়ে সংজ্ঞার কথা মনে করলেই হাসি পেয়ে যায়। আমার ধারণা তিনি নিজেও ‘বর্ষাযাপন’ কবিতাটি লিখেই দায় সেরেছিলেন—গল্প লেখার সময় নিশ্চয়ই কবিতাটিকে সামনে নিয়ে বসতেন না।
তবে এটাও ঠিক—কবিতা যিনি লিখেছিলেন, গল্পগুলিও তাঁর। এজন্যে ‘গল্পগুচ্ছ’-এর ভুবন এত বিচিত্র হলেও তা যে একজনেরই তৈরি এবং তাঁর নাম যে রবীন্দ্রনাথ—এ কথা আমরা শেষ পর্যন্ত জানি। রবীন্দ্রনাথের অনন্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বিনা ব্যতিক্রমে তাঁর প্রত্যেকটি গল্পই বাঁধা আছে।
মনে হয় ছোটগল্পের সংজ্ঞা লেখা রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল না—না নিজের জন্যে, না অন্যের জন্যে। সাধারণভাবে ছোটগল্পের জন্যেও নয়। তিনি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর মনোভাবমাত্র—যেমন করে তিনি চারপাশের পৃথিবী দেখতে চাইতেন, আঁকতে চাইতেন যেমন করে ভাবতেন এবং লিখতেন। আমাদের পছন্দ হোক আর না-হোক যেভাবে লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল, তিনি শুধু তাই জানিয়েছেন আমাদের। সব লেখাতেই তাঁর এই মনোভাব প্রলেপের মতো লেগে আছে বলেই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্প রবীন্দ্রনাথের—নিজের দেওয়া সংজ্ঞা তিনি মেনে চলুন আর না-চলুন।
সব লেখকের বেলাতেই এটা খাটে। যত বিভিন্নতাই থাকুক, চেখভের লেখা সহজেই চেনা যায়। ‘কেরানী’র মতো আকারে ছোটগল্পই হোক—আর ‘সাত নম্বর ওয়ার্ড’-এর মতো দীর্ঘ গল্পই হোক—চেখভের অভ্রান্ত ছাপ চোখ এড়ানোর উপায় নেই। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো ইচ্ছে করলে একটা সংজ্ঞা তৈরি করতে পারতেন, সেটা ভুলে যেতে পারতেন এবং ভুলে গিয়েও সম্পূর্ণ চেখভীয় সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিয়েই গল্প লিখতে বাধ্য হতেন। এই কথা পুরনো-নতুন সব বড় লেখকের সম্পর্কে বলা চলে এবং কথাটা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলতে হয় লেখকমাত্রেই অনন্য, স্বতন্ত্রভাবে ভোগ্য ও অনুসন্ধানযোগ্য। সাহিত্যের সাধারণ নিয়মকানুন তৈরি করে লেখকদের উপর গড় প্রয়োগ কিছুতেই সমর্থন করা চলে না। কারণ এ কথা আমরা কখনো ভুলি না যে সাধারণ নিয়ম তৈরির পদ্ধতি আরোহাত্মক, অবরোহমূলক নয়। সাহিত্য বিষয়ক সাধারণ নিয়মকানুনের সিদ্ধান্ত নয়, লেখকদের রচনা বরং বিচার করেই সাধারণ নিয়মকানুন তৈরি হয়।
কাজেই লেখকে-লেখকে ভিন্নতা আমি চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে রাজি এবং যতটা খোলামন নিয়ে আমি তাঁদের সম্মুখীন হতে চাই, তাকে কেউ নৈরাজ্যিক বললেও আমার আপত্তি হবে। রবীন্দ্রনাথের জন্যেও রাবীন্দ্রিক সংজ্ঞা যে যথেষ্ট নয় সেই কথা দিয়েই তো এই লেখাটা শুরু হয়েছে।
কথাগুলি সমালোচকদের ভালো লাগবার কথা নয়। সংজ্ঞা আর সাধারণ নিয়মকানুনের চুম্বক নিয়ে এঁরা বসে আছেন। লেখা পেলেই চুম্বকে ঠেকিয়ে দেখেন ভালো কি ভালো নয়। এরকম ব্যবসাদার সমালোচকদের বিরক্তির অন্ত থাকবে না আমার কথায়। তবে এঁদের কথা আমি জানি না। সাধারণ পাঠক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা এই যে
—লেখকমাত্রেরই নিজের নিজের উপনিবেশ আছে—সেখানকার ভাষা আলাদা, ঘরবাড়ি মানুষজনের চেহারা, চলাফেরা সবই আলাদা। তারাশঙ্করের সাহিত্যের জনপদ, ঘরগেরস্থি, মানুষজন, দালান-কোঠা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে অনেক দূরে।
পৃথিবীর সাহিত্যের বড় শিল্পীদের প্রত্যেকের নিজের তৈরি ভুবন আছে—সাহিত্য পাঠকের এটাই বোধহয় প্রথম অভিজ্ঞতা। নিজের নিজের পৃথিবীর দরজা কেউ বন্ধ করে রাখেন, কেউ রাখেন হাট করে খুলে, কারোর পৃথিবীর মূল স্বাদ মধুর কারো-বা তেতো। কোথাও ঢুকলে জড়িয়ে পড়তে হয়, রাস্তাগুলি গোলকধাঁধার মতো; অন্য কারোর রাস্তাগুলি সিধে এবং আলোয় ভরা। লেখকদের যে স্রষ্টা বলা হয় সেটা একমাত্র এইভাবেই বোঝা যায় যে, এই পৃথিবীতে বাস করেও কী-এক অদ্ভুত দায়ে তিনি আরো একটি দুনিয়া বানিয়ে ফেলেন। সাহিত্যের সমুদ্রে এইসব অসংখ্যা পৃথিবী পাশাপাশি টিকে আছে, ভাঙছে বা নতুন করে দেখা দিচ্ছে। হয়তো তারা সব সময়েই পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী নয়—কখনো কখনো গায়ে-গায়ে মেশামেশি করেও আছে বৈকি।
সন্দেহ হতে পারে, লেখাটার ঠিক এই জায়গায় একটা রহস্যের ভাব এনে ফেলা হয়েছে—যেন লেখকরা ভৌতিক ক্ষমতাওয়ালা বাজিকর, তালু মেলে ধরলেই তাতে অজানা রাজ্য দেখা দেয়। কথাটা ঠিক তা না-হলেও ভাবায় বৈকি—লেখকের ক্ষমতাকে স্রেফ প্রতিভা বলে কি ব্যাখ্যা করা যায়? কেন একজন লেখক অন্য কারো মতো না-হয়ে একমাত্র নিজের মতোই হন; তৈরি মানদণ্ড দিয়ে কেন যে একজন লেখকের পার পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে—এ প্রশ্নের সরল জবাব আমি আজও পাইনি।
তবে রহস্যের ছিটেফোঁটা মাত্র না-রেখে একটা কথা বোধহয় বলা চলে যে, সমাজে সাধারণ-অসাধারণ অন্যসব মানুষের মতোই লেখকও তাঁর রচনায় একটি প্রেক্ষিতের প্রতিনিধিত্ব করেন। জড় পদার্থের আছে স্থানকালের অবস্থান; মানুষের আছে প্রেক্ষিত। সামনে থেকে, পেছন থেকে, পাশ থেকে, কোনাকুনি বা সোজাসুজি লেখককে তাকাতেই হয়—তাকে মত দিতে হয়, মতের জন্যে খুঁটি গেড়ে বসতে হয়, কিছু কিছু মূল্যের জন্যে লড়তে হয়, কিছু কিছু বিশ্বাসের জন্যে মায়া রাখতে হয়। কোনাকুনি বা সোজাসুজি দেখা, আস্থা-বিশ্বাস-মায়া ইত্যাদি নিয়েই গড়ে ওঠে লেখকের প্রেক্ষিত—ব্যাপকভাবে যা নিয়ন্ত্রিত হয় তার জীবনের মূল কাঠামো দিয়ে। তাঁর প্রেক্ষিতের সীমা আসলে তাঁর অভিজ্ঞতারই সীমা। মাছের যেমন পুকুরের জলটুকুতেই অস্তিত্বের সীমা, লেখকেরও তেমনি তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার দালানটুকুর মধ্যে চলাফেরা। প্লেটো যেমন বলেন, ‘ধারণার জগৎই মূল
—এই বাস্তব জগৎ তার একটা অনুলিপিমাত্র’—প্রায় একইভাবে বলা যায়, লেখকের অভিজ্ঞতায় জানা প্রতিবেশের শর্তে বাঁধা জগতেরই চিত্র হচ্ছে তাঁর রচনা। এর হাত থেকে কোনো লেখকের নিষ্কৃতি আছে বলে মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে পরবর্তীদের তফাৎ করতে এমনকী আনাড়ি সমালোচককেও যখন যুগ, কাল, সময়, পরিবেশ, সমাজ সমস্যাগত পার্থক্য ইত্যাদির উল্লেখ করতে দেখা যায়, তখুনি একথার প্রমাণ পাই এবং সত্যি করে এইভাবে বিচার করেই, লেখককে আমরা ভালো বুঝতে পারি। একজন লেখকের সঙ্গে আর-একজন লেখকের তফাৎ তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—অনন্যতাও আর রহস্যের মতো মনে হয় না। এই অর্থে, লেখামাত্রেই এক ধরনের আত্মচরিত—বিশেষ করে উপন্যাস ও ছোটগল্প তো বটেই। লেখক নিজে যা জেনেছেন, দেখেছেন বিশ্বাস করেছেন, ভালো বা মন্দ বলে বিচার করেছেন—ঘুরে-ঘুরে তাই চলে লেখায়। সজাগ হয়ে আটকালেও অজান্তে লেখায় এসবের ছাপ পড়ে যায়। বানোয়াট কাহিনী হিসেবে যাঁরা গল্প উপন্যাস পড়েন এবং ঔপন্যাসিককে যাঁরা কাহিনী থেকে বেশি মর্যাদা দিতে চান না, তাঁরা করুণার পাত্র। কারণ লেখক সমাজ, রাষ্ট্র এবং মানুষ সম্পর্কে যে-মন্তব্য করেছেন, তা কখনোই এঁদের নজরে আসে না।
লেখকের অভিজ্ঞতার জগৎ অবশ্যই বহুস্তরা। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এখানে দুর্জ্ঞেয়ভাবে মিশে যায়, কৈশোর-স্বপ্ন থাকে, অভিমান থাকে, জীবনের শ্রম থাকে, ভালোবাসা ঘৃণা সবই থাকে, চেনা-অনুভূতি অজানা-বোধের প্রান্তদেশ ছুঁয়ে যায়। তাঁর এই অভিজ্ঞতার জগৎ যদি সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, তাহলে একজন লেখকের অনন্যতার ব্যাখ্যা খানিকটা পাওয়া যায়। কাজেই লেখককে স্বকীয় কণ্ঠ পেতে হবে বলার কোনো মানে নেই বরং বলা চলে স্বকীয়তাই লেখকের কপালের লিখন—চেষ্টা করেও কারো পক্ষে অন্য কারোর মতো হয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। হেমিংওয়ের সাহিত্য তাঁর জীবনেরই প্রজেকশন—গর্কিও তাই। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যেমন গুলিয়ে যাবার ভয় প্রায় কখনোই থাকে না, যমজ ছাড়া, লেখকদেরও তাই।
যে কথাগুলি এইমাত্র বলা গেল তাতে আর লেখকদের অনন্যতার উৎস দুর্জ্ঞেয় বলে নির্দেশ করা চলে না। শিমুল ফল পাকলে যেমন ফেটে ছড়িয়ে পড়ে, একজন লেখকের অভিজ্ঞতায় জানা জগতের চাপও তেমনি সংজ্ঞা আর নিয়মের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে। তাঁর জন্যে আর-কোনো নিয়মই কাজ করে না।
তবু তো দেখি লেখায় লেখায় সাদৃশ্য—লেখকদের অসংখ্য স্বতন্ত্র জগৎও তো পরস্পরের মধ্যে ঢুকে যায়। একের প্রভাব পড়ে আরেকজনের উপরে—একজন লেখক অন্যদের উপর এমন উৎকট চাপ দিতে থাকেন যে তাঁর রাজত্বের আর অবসান হতে চায় না।
এর উত্তরে বোধহয় বলা যায়—অনন্যতার বীজ লেখকের অভিজ্ঞতার জগতে থেকে যায় ঠিকই—কিন্তু তার অভিজ্ঞতার জগৎও তো স্থানকালে বাঁধা। দৃষ্টিগ্রাহ্য স্পর্শগ্রাহ্য বাস্তব সমাজ সংগঠনের মধ্যেই লেখক বাড়েন। তাঁর অবস্থান বা প্রেক্ষিত গড়ে ওঠে সমাজে। এ জন্যে বলতে হয়, শিল্পীর অভিজ্ঞতা একদিক থেকে বিশেষ ও অনন্য; অন্যদিক থেকে সার্বিক ও সামাজিক। বড় লেখকের লেখা যেমন অদ্ভুতভাবে স্বকীয়—অন্যদিকে তেমনি প্রতিনিধিত্বশীল। হয়তো এই প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটিকেই আমরা সমসাময়িকতা নাম দিয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি অতুল্যভাবে, চূড়ান্তভাবে বঙ্কিমী—কিন্তু তাঁর জগৎ সেকালের অন্য অনেক লেখকেরও জগৎ। তাঁর প্রসঙ্গগুলি এদিক থেকে সমসাময়িক, সার্বিক এবং তাঁর সমাজের একটি স্তরের সম্পর্কিত। বাংলাদেশে ছয়ের দশকে যাঁরা কবিতা লিখতেন—এখনো তাঁদের আমরা চিনতে চাই কতকগুলি সামান্য লক্ষণ দিয়ে। এসব সামান্য বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে আসলে আমরা এই সময়ের কবিদের শিথিলভাবে একসঙ্গে বাঁধতে চেষ্টা করি। তার বেশি কিছু নয়।
কথাটা যদি সাধারণভাবে সত্যি হয়, তাহলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের পরিচয় নানা লেখকের রচনায় স্বাভাবিকভাবেই ধরা পড়বে। এই কথাটিকে আর-একটু টানলেই বলা যেতে পারে সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থাকলে, সেই শ্রেণী পরিপোষিত লেখকের রচনায় মূলত মধ্যশ্রেণীরই ছবি আর কথা থাকবে। লুকোনোর কোনো উপায়ই নেই, দুধের সাদা রঙের মতোই এটা স্বাভাবিক। যে-লেখকের অভিজ্ঞতার জগতে নানা স্তরের মানুষের আনাগোনা তার রচনায় সেই সব মানুষেরই পদপাত ঘটবে। এই নিয়মের লঙ্ঘন হবার উপায় নেই বলে বিভ্রাটও কম দেখি না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়েই বেশিরভাগ লিখেছেন—মধ্যবিত্ত সমাজের একেবারে তলার দিকটা নিয়ে। কিছু পরিচয়ের সূত্রে শ্রমিক কৃষিকদের নিয়েও লিখেছেন। শ্রমিক কৃষকদের নিয়ে তাঁর লেখা ঠিক সেই অনুপাতেই খাঁটি যে-অনুপাতে তিনি তাদের ঠিক ঠিক জানতেন—তার বেশিও নয়, কমও নয়। বিভ্রাটের খবর পাওয়া যায় তখুনি—যখন দেখা যায় শ্রমিক বা কৃষকের চেহারার মধ্যে মধ্যবিত্তের ভূত ঢুকে বসে আছে। এই গোলমাল ‘গল্পগুচ্ছে’ বার বার ঘটতে পারত—যদি রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষকে পুঙ্খানুপুঙ্খে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতায় আঁকতে চেষ্টা করতেন। তিনি তা না-করে তাঁর পক্ষে যা করা স্বাভাবিক ছিল তাই করেছেন—একটু দূর থেকে এঁকেছেন এবং প্রাত্যহিকতা খসিয়ে দিয়ে মানুষের ধারণাটাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। এইসব কারণে কেউ যদি শ্রেণী সাহিত্যের কথা তোলেন, শ্রেণী ঘৃণার কথাও উল্লেখ করেন আমি উত্তেজিত হয়ে তাঁর গলা টিপে ধরতে যাব না। যে-পাঠক আমাদের দেশের গরিব মানুষদের মধ্যে কাজ করেন বা তাদের পক্ষে আছেন, মধ্যশ্রেণীর লেখককে তিনি অবশ্য বুর্জোয়া অপদার্থ বলে গাল দিতে পারেন। লেখক দলভুক্ত তো বটেই, তিনি ইচ্ছে করলে দলে যোগ দিতে পারেন, না-ও যদি দেন তবু তিনি দলভুক্ত থাকেন সন্দেহ নেই। লেখকের অনন্যতায় জোর দিয়েও এখন আমি বলব লেখক সমাজের তৈরি। তিনি অনুরোধ রাখুন আর না-রাখুন, তার লেখাকে সামাজিকভাবে মূল্যবান করে তোলার দাবি উঠতে পারে তাঁর কাছে। অন্যান্য সামগ্রীর মতো সামাজিক সম্পত্তি হিসেবেও তাঁর লেখা ব্যবহৃত হতে পারে।
তবুও লেখক আপন দেশ, অনেকের সম্মিলিত শ্রমে ও অসংখ্য মানুষের বর্মে গড়ে উঠলেও—ঠিক রচনার মুহূর্তে তিনি একা। বহুজনের স্পর্শ-লাগা, ঘষা-খাওয়া অভিজ্ঞতার জগৎকে ফুটিয়ে তোলার কাজে যে-যে উপকরণ তিনি ব্যবহার করতে পারেন একহিসেবে তা সামান্য। এই উপকরণের নাম শব্দ—লেখকের একমাত্র হাতিয়ার হাজার রকম কৌশল তিনি গ্রহণ করতে পারে, অসংখ্য কলকব্জাও তিনি তৈরি করতে পারেন—কিন্তু এই মূল উপকরণের সুবিধে ও সীমাবদ্ধতার দায় তাঁকে বইতেই হয়।
শব্দ সবাই ব্যবহার করে—লিখে বা না-লিখে; আলু পটলের দরাদরি করে বা দলিল রচনা করে। খবরের কাগজে। শব্দ-প্রবাহ মানুষের সব প্রয়োজন বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এই একমাত্র উপকরেণ ব্যবহার করতে গিয়ে নিজের জগতের মাটি, মানুষ, আকাশ, টাকাকড়ি, জীবনযাপন পুনর্গঠিত করতে গিয়ে এত জটিল সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় লেখককে, কেউ তখন সাহায্যে আসে না। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া বা তার উপকার করার সাধ্য কারো নেই। যদিও অন্যের মতো লেখকও প্রত্যেক দিন নানা প্রয়োজনে অজস্র বাক্যরাশি উদ্গীরণ করে থাকেন, শব্দ ব্যবহারের নিয়মকানুন লেখা পুঁথি আছে তাঁর হাতের কাছে—তাঁরই মতো আরও অনেক লেখকের রচনাও আছে তাঁর সামনে—কিছুই যথেষ্ট নয়।
ঠিক এখানে এসেই লেখককে একা হয়ে যেতে হয়। যে-জগতের পত্তনি নিয়েছেন তিনি—একটি একটি করে সেখানে গাছ, বাড়ি, নদী, মানুষ সাজাতে হয়, একা কোদাল চালিয়ে রাস্তা তৈরি করতে হয়—নিজের সব বিচিত্র নিয়ম চালু করতে হয়।
সোজা কথায়, লেখককে স্থাপন করতে হয় একটি নিজস্ব উপনিবেশ।

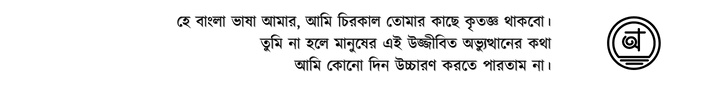

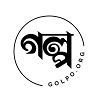

0 মন্তব্যসমূহ