নেংটি ইঁদুরদের জ্যোৎস্না এবং প্রত্যুষের আলো পান করতে আমিও দেখেছি; এরকম ভাববার কোনও কারণ নেই যে, প্রভাত-সূর্যের প্রথম আলো এবং মাধবী পূর্ণিমার পূর্ণ জ্যোৎস্না কেবল মানুষেরই পানীয়— শুধু নেংটি নয়, ধেড়েরাও চাষির মাঠের ধান-শিষ চুরি করে মাটির সুড়ঙ্গে নামিয়ে নেবার সময় শ্রম-শ্রান্ত হয়ে আকাশে মুখ তুলে জ্যোৎস্না চেটে নেয়— এ আমি দেখেছি।
ইংরেজি ভাষায় ধেড়ে ইঁদুরের নাম হল ব্যান্ডিকুট (bandicoot)।
নেংটি ধান-সংগ্রহে উৎসাহী নয়। ওর কাজ অন্য রকম। বলতে কি, নেংটির ওপর আমার রাগটাগ নেই; মনিহারি দোকানে নেংটির কিছু উপদ্রব আছে; আমার লেখাপড়ার ঘরে ওরা দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ছোটাছুটি করে— বড় কোনও ক্ষতি আজ পর্যন্ত করেনি। কথাটা নেংটিকে নিয়ে নয়, কথা আসলে ব্যান্ডিকুট ব্যাপারে।
নেংটি ধান-সংগ্রহে উৎসাহী নয়। ওর কাজ অন্য রকম। বলতে কি, নেংটির ওপর আমার রাগটাগ নেই; মনিহারি দোকানে নেংটির কিছু উপদ্রব আছে; আমার লেখাপড়ার ঘরে ওরা দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ছোটাছুটি করে— বড় কোনও ক্ষতি আজ পর্যন্ত করেনি। কথাটা নেংটিকে নিয়ে নয়, কথা আসলে ব্যান্ডিকুট ব্যাপারে।
কবি গেয়েছেন, ‘জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা’— কথাটা ইঁদুরের বেলাতেও খাটে; আমার এক বন্ধু ছিল বাবু রুইদাস— ওরা রুইদাস টিকরে কাছারিপাড়ার ডিহির কাছে বাস করত— মাত্র চারঘর মুচি; ওদের নিজস্ব কোনও জমিজমা ছিল না; ওরা অন্যের জমিতে খাটত; পুজোয় ঢাক-কাঁসি বাজিয়ে রোজগার করত; ছাগশিশু খাসি করে কিছু কামাত; ওরা হিন্দুসমাজে এবং কিয়দংশ মুসলমান পাড়াতেও অচ্ছুত ছিল; কেন ওদের ঘৃণা করা হত জানি, কিন্তু সে কথা আপাতত এইবেলা থাক। পরে বলব।
ব্যান্ডিকুটের রাজারানিকে প্রণাম জানিয়ে গল্প শুরু করছি। সে বছর দুর্ভিক্ষ হয়েছে। সুপ্ত দুর্ভিক্ষ এ সমাজে বরাবরই আছে, প্রকট দুর্ভিক্ষ, মাঝেমধ্যেই দেখা দেয় যক্ষ্মা, ওলাওঠা, বসন্ত-করোনার মতো— দুর্ভিক্ষ এদেশের রাজনীতির প্রধান ব্যাধি; এ জিনিস রাম-মন্দির প্রতিষ্ঠার পরেও ঘোচে না— সে কারণেও খুদের গন্ধমাখা ইঁদুর-দেবতাকে প্রণাম।
আমার নাম জুলকার-নাইন হলেও, আমি নদীকে, সূর্যকে, নক্ষত্রকে রোজ-রোজ প্রণাম পেশ করি; আমি আধা-নাস্তিক ধরনের পাগলা কথক। গল্প বলতে ভালবাসি; নামাজ পড়ি, পুজোও দিই; বাইবেল পড়ি। তারপর কিছুকাল কিছুই করি না। মিথ্যা যদি বলি, আমার জিভ খসে পড়ে যাবে। যা বলছি, সত্য।
‘দুয়ারে রেশন’ যদি না থাকত, তাহলে এই ধরনের গল্প লিখতে যে দম লাগে তা আমার থাকত না— কবুল করছি, যা বলব সত্য বলব, স্রেফ সত্যই বলব; বাংলা-সাহিত্য যদি আবার কখনও সত্যবাদী হয়ে ওঠে, তাহলে এ গল্পের ভবিষ্যতে খোঁজ পড়বে।
জুলকার-নাইন যে-গল্পটা বয়ান করছে, তা ৫০-৬০ বছরের পুরনো, কিন্তু দুর্ভিক্ষ এদেশে কখনও পুরনো হয় না; ভিক্ষার অভাবকে বলে দুর্ভিক্ষ— করোনায় ভিখিরি বেড়েছে। ফেসবুকে সে-সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই।
রোগা কিশোরীর ছোট বুকের সাইজমাফিক বেগুনের দাম ২০ টাকা, দর করে ১৫ টাকায় কিনেছে জুলকারের বউ; চন্দনেশ্বরের বেগুন; মাধবপুরের রাহুল (আসল নাম সামাদ) ৩০ টাকায় দু’খানা বেগুন বেচে গেল— ভ্যানে করে বেচতে আসে।
যখন দুর্ভিক্ষ হয়, জিনিসের দাম বাড়ে।
দুর্ভিক্ষ হলে আজকাল ডিজেলের দাম বাড়ে— দুর্ভিক্ষকে চোখা করে তুলতে রোজ ডিজেলের দাম বাড়ানো হয়। ফেসবুকে বেগুনের সাইজ দেখানো হয়নি; উচিত ছিল। ডিজেল সম্পর্কে বার্তা নেই।
গ্যাসের দাম বাড়তে বাড়তে মানুষের লোভী জিভের চেয়ে লম্বা হয়ে গেছে, তা আগুনের চেয়ে সর্বদা লকলক করে। ফলে জুলকারের ছোট ছেলেকে কেরোসিন ও রান্নার কয়লার লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে।
কেরোসিনের লম্ফ জ্বলছে মুচিপাড়ার টিকরে; চটি বারান্দায়। বাবুর বাবা হরি। বাবুর পুরা নাম, বাবুলাল রুইদাস; বাবা হরিলাল রুইদাস; মা কৌশল্যা রুইদাস; বোন, লক্ষ্মী রুইদাস।
তখন পয়সাকে নয়া-পয়সা বলা হত। আটা ছিল ৩৬ নয়া-পয়সা সের; সের থেকে কিলো হয়েছে সদ্য-সদ্য। আমেরিকা গম পাঠাচ্ছে বলে আটা ৩৬ নয়া কিলো; পয়সাকে নয়া-পয়সা না বলে ‘নয়া’ বললেও চলত। আমরা ‘নয়া’ বলতাম।
— ‘যব ৩০ নয়া কিলো। ২৫ নয়া কিলো ভুট্টার আটা। তখন মজুরি ৩ সিকি। অর্থাৎ ১২ আনা। ভাল মজুর হলে এক টাকা কিংবা পাঁচ সিকা। সিকা বলতে পারো, সিকিও বলতে পারো। তুই কত করে পাস বাবু?’
— ‘বাবা তিন সিকা। মুই পাঁচ সিকা জুলকার। বাবা বলছে, লিখাপড়া ছেড়ে দে বাবু! খাটলে পাঁচ সিকা ঘরে আসবে বাপ। বাপের সাইজ ছোট, আমার সাইজ বড়, সেই জন্যে!’
— ‘আমার পাঁচ সিকা। বাবার তিন সিকা। আমায় সিনাও বড় জুলকার।’
— ‘হ্যাঁ, তোর বুক বড়। কোমরে, দাবনায় বল আছে বাবুলাল!’
— ‘তাতে কী!’
— ‘কেন?’
— ‘মজদুরি ফি-দিন তো জুটে না ভাই! তাছাড়া আমার স্কুল আছে; যেতে হয়।
— ‘আকাল কিনা! তাই স্কুল কামাই দিয়ে মজদুরি করিস।’
— ‘হুম!’ বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বাবু রুইদাস।
তারপর বলল, ‘লম্ফতে ফুঁ দিই, নিবাই? তেল কত আক্রা জুলু!’
— ‘দে। নিবিয়ে দে।’
সন্ধ্যায় তুলসীকে আলো দেখিয়ে লম্ফ নিবিয়ে দেওয়াটাই দুর্ভিক্ষের দস্তুর।
— ‘আকাশে অত আলো, পৃথিবীতে আলো কই! একটা কোনও পোষা তারা থাকলে এখন কত কাজ দিত ভাই! আজ আকাশে তারা কম; কোনও একটা খসে পড়লেও তো পারে। কুড়িয়ে এনে মেঝেয় চটের উপর রেখে ক্লাসের পড়া করি। প্ল্যানটা ভেবে দ্যাখ জুলু!’
জুলু হল জুলকার-নাইনের ডাকনাম। বাবু আর জুলু দুই বন্ধু। দুই বন্ধুই দেখতে সুন্দর। বাবু তো রীতিমতো রূপবান। ফলে কেউ ওকে রুইদাস ভাবতে পারে না।
— ‘চ ঝালিয়ে নিই। হ্যারিকেনের সবুজ কাচ এনেছে বাবা; সেই আলো ভাগ করে দুজনে পড়ব। ইংরেজি আর বাংলা। দুধে ভিজিয়ে ভুট্টা খাব। সাদা-সাদা।’
জুলুর প্রস্তাবে বাবু চুপ করে রইল।
আকাশে একটি নক্ষত্র টিমটিম করছে; মনে হচ্ছে, দপ করে জ্বলে উঠে তেলের অভাবে নিবে যাবে। বারান্দায় বসে বন্ধুর সঙ্গে সেই নক্ষত্রের দিকে চেয়ে আছে বাবুলাল; তার সর্বাঙ্গে ক্ষুধা নখরে নখরে আঁচড়াচ্ছে।
— ‘কী হল! মা তোকে ডেকে নেবার জন্য বলেছে। বলেছে, বাবুকে সঙ্গে নে আয়; বলবি মাসি ডাকছে।’
একথা শোনামাত্র বুকের মধ্যে তার হৃৎপিণ্ড তড়াক করে লাফিয়ে উঠল আর পেট কলকল করে ডেকে উঠল। খিদেয় এইভাবে পেট ডাকে— এই অভিজ্ঞতা জুলুর হয়েছে অন্যভাবে। রোজার মাসে সে দু’চারটি রোজা রেখে পেট ডাকতে দেখেছে।
জুলু তার দাদিমাকে পেটের উপরকার গেঞ্জি তুলে দেখিয়ে বলেছিল; ‘দ্যাখো দাদি, পেটটা কেমন ডাকছে! মনে হচ্ছে, জল কাটছে।’
দাদিমা বলেছেন, ‘জ্ঞান তো হল! রোজা আর করতে হবে না। তোমার বাকি রোজা আমি দুটি-চারটি করে রেখে পুরা করব বছরভর, তুমি ভেবো না। বাচ্চাদের দু’চারটিই যথেষ্ট। আসলে পেটের জ্বালা না বুঝলে রসুলের ধর্ম হয় না।’
— ‘আজ্ঞে!’
— ‘তুমি আজ্ঞে বলো কেন?’
— ‘জি বললেও চলে, তবে আজ্ঞেই ভাল দাদিমা!’
— ‘তুমি তো কবি সিকন্দর, যা ভাল বোঝো!’
জুলুর একটা ‘তোলা’ অর্থাৎ তুলে রাখা নাম রয়েছে আর সেটি হল, সিকন্দর-এ-আনাম।
ফার্সি ভাষায় সম্রাট আলেকজান্দারকে বলা হয় ‘সিকন্দর’— তাঁরই উপাধি হল, জুলকার-নাইন (নাইন আসলে ‘নেইন’), সিকন্দর-এ-আজম মানে সম্রাট আলেকজান্দার। সিকন্দর-এ-আনাম মানে হল শ্রেষ্ঠ মানুষদের রাজা— মানবশ্রেষ্ঠ।
ভাল ভাল নামের মধ্যেই বাংলার মুসলমান বেঁচে থাকতে চায়। পরিযায়ী শ্রমিকের নামও সিকন্দর।
প্রধানত এই মুসলমানের সঙ্গেই বেঁচে রয়েছে বাবুদের মুচি-টিকরের একটি ছোট জনগোষ্ঠী; এরা হিন্দুর দিকে ঝুঁকে আছে, মুসলমানের দিকেও; কিন্তু ওরা ছোটজাত— অচ্ছুত; বড়ই আশ্চর্য লাগে, এরা কোনও সমাজেরই আপনার কেউ নয়। এরা পর।
জুলুর ফ্যামিলি এইসব মানে না।
উগ্রভাবে জাতপাত-বিরোধী।
বাপ মনসুর আহমেদ বিচিত্র মানুষ। আধেক আস্তিক, আধেক নাস্তিক। বা বলা যায় কখনও আস্তিক, কখনও নাস্তিক— সকালে-বিকালে তাঁর মনের বদল ঘটে। কিছুদিন নামাজ পড়েন, তারপর বন্ধ করে দেন। সকালে পড়লেন, বিকেলে পড়লেন না।
মা জহুরা আহমেদ গভীরভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী নামাজী, ঠাকুমা গভীরতর আমলবাদী নামাজী।
দাদিমা অর্থাৎ ঠাকুমা মনসুরকে বলেন, ‘এমনটি করতে নেই বাপ; এই বলছ আছে, এই বলছ নাই!’
বাবা বলেছেন, ‘হ্যাঁ মা। আমি ওই রকমই।’
— ‘ভবিষ্যতে তুই কী হবি আমান?’
জুলুর কাছে জানতে চেয়েছে বাবু।
জুলু উর্ফে আমান বলেছে, ‘তুইই বল না, আমি কী করব?’
এই দুই বন্ধু স্কুলে ফার্স্ট-সেকেন্ড বয়; বাবু ফার্স্ট হলে, দ্বিতীয় স্থানে থাকে জুলু; স্কুলে জুলুকে ‘আনাম’ নামে ডাকা হয়— সেটি শুনতেও ভাল। ভাবতেও ভাল।
ওরা দু’জনই জীবন-ঔৎসুক্যের মাত্রায় আশ্চর্য আকুল প্রাণী— সব ব্যাপারে এটা-কেন, ওটা-কেন ভাব; পড়ার ব্যাপারে সর্বগ্রাসী। স্কুল লাইব্রেরি ছাড়াও দুটি নদী পেরিয়ে ওরা দুই বন্ধু মিলে নতুন হাসানপুরে যায় ওখানকার গ্রন্থাগার থেকে বই আনতে— তবে কোনও গ্রামেই খবরের কাগজ যায় না।
জুলু তো ১৪ বছর বয়েস থেকে ছড়া-কবিতা লেখে। সেই ছড়ার প্রধান পাঠক বাবু। এখন ওরা দশম শ্রেণির ছাত্র— প্রবল দুর্ভিক্ষের মুখে পড়েছে।
জুলু ব্যঙ্গ করে লিখেছে—
‘খাই খাই করো কেন
এসো-আহা-আহা-রে!
মানুষ বুঝে না পায়,
অন্ন কয় কাহারে!’ ইত্যাদি।
বাংলার কবি বলেছেন, ‘অন্নই ওংকার।’
— ‘আমার এত খিদে পায় কেন, ভাই!’
— ‘ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়।’
— ‘গদ্যের এত দোষ কেন ভাই!’
— ‘ক্ষুধার দেশে পদ্যও সতী থাকতে পারে না।’
— ‘আগে রুটি, তারপর ভগবান।’
— ‘সুকান্ত ছিলেন দুর্ভিক্ষের কবি।’
— ‘২৮ দিন ভাতের হাঁড়ি চড়েনি টিকরে। কুত্তি-বাজরার রুটি খেয়ে মাথা ঘোরার ব্যামো হয়েছে। মাঝে-মাঝে ঢুলে পড়ে যাই। ক্লাসে একদিন পড়ে গেলাম। তখন হাসির হুল্লোড় হল, তারপর সবাই চুপ। ভাবল, ক্লাসের ফার্স্টবয় এভাবে পড়ে যায় কেন? তাই না?’
মানুষ যত অভাবী ততই সে খোদা মানে, একথা ঠিক নয়— তাদের বেশির ভাগই খোদায় আধা বিশ্বাসী, আধা অবিশ্বাসী— তাছাড়া চাইলেই তো ভগবানে অধিকার পাওয়া যায় না। রুইদাসদের মন্দিরে ঢোকার অধিকারই নেই; পূজায় অধিকার দূর থেকে। বাইরে থাকো; ঢাক বাজাও আর কাঁসি বাজাও।
— ‘জানমহম্মদের দোকানে কাঁসি বাঁধা দিতে গেলাম। জানভাই বললে, থালা হলে নিতাম, কাঁসি কী হবে! তা ছাড়া এ জিনিস কাঁই-কাঁই করে কাঁদে; আকালে ওই রকম ‘শোর’ সহ্য হয় না বাবু!’
— ‘ওহ্! বাবুলাল!’
— ‘হ্যাঁ জুলু! সব বর্তন দুর্ভিক্ষে গেল। তোর মনে আছে, রুইদাস বাড়ির কাঁসা-পিতলের বর্তন সূর্যের আলোয় কেমন জ্বলতে থাকে— যেন সেই আলো দিয়ে মায়েরা ঘরের গরিবি ঢেকে রাখে। মনে পড়ে!’
— ‘আগে গেল ঝরা, তারপর এল খরা! কী করবি বল! আমার বাবার তবু মাস-বেতন আছে। প্রাইমারির মাস্টার কিনা; বাবাই তো হেড-পণ্ডিত। কিন্তু ভয় হচ্ছে, ছাত্রের অভাবে স্কুল না বন্ধ হয়ে যায়! আগে ঝরা, পরে খরা, এমন কেন হল! ম্যালথাসের থিয়োরি এবার হায়ার সেকেন্ডারি (একাদশ শ্রেণির উচ্চমাধ্যমিক) ফাইনালে আসছেই, ইলেভেনের দাদারা সব বলাবলি করছিল।’
— ‘ম্যালথাস আসবে না!’
— ‘কেন?’
— ‘যেটা বেশি আসবে মনে হয়, সেটা আসে না। সামনে বছরে আমাদের বেলায় আসবে। কিন্তু বাঁচব তো! ম্যালথাস পড়বারও তো স্টুডেন্ট চাই জুলু!’
— ‘অত নেগেটিভ ভাবলে হয়! চ। এবার তো ঝরা-খরা ক্ষান্তি দিয়েছে বাবু! ধান পাকতে শুরু করেছে। ষাটী মরাইতে এল বলে; মা বলেছে, মুচিডিহি রুইদাস টিকরে দুই-তিন মণ ষাটী ধান খয়রাত করবেন মাস্টারমশাই! মা তো বাবাকে হয় পণ্ডিত বলে, নয় তো মাস্টারমশাই। রাগের সময় পণ্ডিত, মর্জি হলে মাস্টারমশাই। চ তাহলে!’
লক্ষ্মী দাদাকে বলল, ‘তুই যা দাদা, মাসি ডাকছে।’
খিদেয় পুড়ছে লক্ষ্মী, তবু দাদাকে মাস্টার-বাড়ি যেতে বলল।
মানুষ যত অভাবী ততই সে খোদা মানে, একথা ঠিক নয়— তাদের বেশির ভাগই খোদায় আধা বিশ্বাসী, আধা অবিশ্বাসী— তাছাড়া চাইলেই তো ভগবানে অধিকার পাওয়া যায় না। রুইদাসদের মন্দিরে ঢোকার অধিকারই নেই; পূজায় অধিকার দূর থেকে। বাইরে থাকো; ঢাক বাজাও আর কাঁসি বাজাও।
ব্যান্ডিকুটের রাজারানিকে প্রণাম জানিয়ে গল্প শুরু করছি। সে বছর দুর্ভিক্ষ হয়েছে। সুপ্ত দুর্ভিক্ষ এ সমাজে বরাবরই আছে, প্রকট দুর্ভিক্ষ, মাঝেমধ্যেই দেখা দেয় যক্ষ্মা, ওলাওঠা, বসন্ত-করোনার মতো— দুর্ভিক্ষ এদেশের রাজনীতির প্রধান ব্যাধি; এ জিনিস রাম-মন্দির প্রতিষ্ঠার পরেও ঘোচে না— সে কারণেও খুদের গন্ধমাখা ইঁদুর-দেবতাকে প্রণাম।
আমার নাম জুলকার-নাইন হলেও, আমি নদীকে, সূর্যকে, নক্ষত্রকে রোজ-রোজ প্রণাম পেশ করি; আমি আধা-নাস্তিক ধরনের পাগলা কথক। গল্প বলতে ভালবাসি; নামাজ পড়ি, পুজোও দিই; বাইবেল পড়ি। তারপর কিছুকাল কিছুই করি না। মিথ্যা যদি বলি, আমার জিভ খসে পড়ে যাবে। যা বলছি, সত্য।
‘দুয়ারে রেশন’ যদি না থাকত, তাহলে এই ধরনের গল্প লিখতে যে দম লাগে তা আমার থাকত না— কবুল করছি, যা বলব সত্য বলব, স্রেফ সত্যই বলব; বাংলা-সাহিত্য যদি আবার কখনও সত্যবাদী হয়ে ওঠে, তাহলে এ গল্পের ভবিষ্যতে খোঁজ পড়বে।
জুলকার-নাইন যে-গল্পটা বয়ান করছে, তা ৫০-৬০ বছরের পুরনো, কিন্তু দুর্ভিক্ষ এদেশে কখনও পুরনো হয় না; ভিক্ষার অভাবকে বলে দুর্ভিক্ষ— করোনায় ভিখিরি বেড়েছে। ফেসবুকে সে-সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই।
রোগা কিশোরীর ছোট বুকের সাইজমাফিক বেগুনের দাম ২০ টাকা, দর করে ১৫ টাকায় কিনেছে জুলকারের বউ; চন্দনেশ্বরের বেগুন; মাধবপুরের রাহুল (আসল নাম সামাদ) ৩০ টাকায় দু’খানা বেগুন বেচে গেল— ভ্যানে করে বেচতে আসে।
যখন দুর্ভিক্ষ হয়, জিনিসের দাম বাড়ে।
দুর্ভিক্ষ হলে আজকাল ডিজেলের দাম বাড়ে— দুর্ভিক্ষকে চোখা করে তুলতে রোজ ডিজেলের দাম বাড়ানো হয়। ফেসবুকে বেগুনের সাইজ দেখানো হয়নি; উচিত ছিল। ডিজেল সম্পর্কে বার্তা নেই।
গ্যাসের দাম বাড়তে বাড়তে মানুষের লোভী জিভের চেয়ে লম্বা হয়ে গেছে, তা আগুনের চেয়ে সর্বদা লকলক করে। ফলে জুলকারের ছোট ছেলেকে কেরোসিন ও রান্নার কয়লার লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে।
কেরোসিনের লম্ফ জ্বলছে মুচিপাড়ার টিকরে; চটি বারান্দায়। বাবুর বাবা হরি। বাবুর পুরা নাম, বাবুলাল রুইদাস; বাবা হরিলাল রুইদাস; মা কৌশল্যা রুইদাস; বোন, লক্ষ্মী রুইদাস।
তখন পয়সাকে নয়া-পয়সা বলা হত। আটা ছিল ৩৬ নয়া-পয়সা সের; সের থেকে কিলো হয়েছে সদ্য-সদ্য। আমেরিকা গম পাঠাচ্ছে বলে আটা ৩৬ নয়া কিলো; পয়সাকে নয়া-পয়সা না বলে ‘নয়া’ বললেও চলত। আমরা ‘নয়া’ বলতাম।
— ‘যব ৩০ নয়া কিলো। ২৫ নয়া কিলো ভুট্টার আটা। তখন মজুরি ৩ সিকি। অর্থাৎ ১২ আনা। ভাল মজুর হলে এক টাকা কিংবা পাঁচ সিকা। সিকা বলতে পারো, সিকিও বলতে পারো। তুই কত করে পাস বাবু?’
— ‘বাবা তিন সিকা। মুই পাঁচ সিকা জুলকার। বাবা বলছে, লিখাপড়া ছেড়ে দে বাবু! খাটলে পাঁচ সিকা ঘরে আসবে বাপ। বাপের সাইজ ছোট, আমার সাইজ বড়, সেই জন্যে!’
— ‘আমার পাঁচ সিকা। বাবার তিন সিকা। আমায় সিনাও বড় জুলকার।’
— ‘হ্যাঁ, তোর বুক বড়। কোমরে, দাবনায় বল আছে বাবুলাল!’
— ‘তাতে কী!’
— ‘কেন?’
— ‘মজদুরি ফি-দিন তো জুটে না ভাই! তাছাড়া আমার স্কুল আছে; যেতে হয়।
— ‘আকাল কিনা! তাই স্কুল কামাই দিয়ে মজদুরি করিস।’
— ‘হুম!’ বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বাবু রুইদাস।
তারপর বলল, ‘লম্ফতে ফুঁ দিই, নিবাই? তেল কত আক্রা জুলু!’
— ‘দে। নিবিয়ে দে।’
সন্ধ্যায় তুলসীকে আলো দেখিয়ে লম্ফ নিবিয়ে দেওয়াটাই দুর্ভিক্ষের দস্তুর।
— ‘আকাশে অত আলো, পৃথিবীতে আলো কই! একটা কোনও পোষা তারা থাকলে এখন কত কাজ দিত ভাই! আজ আকাশে তারা কম; কোনও একটা খসে পড়লেও তো পারে। কুড়িয়ে এনে মেঝেয় চটের উপর রেখে ক্লাসের পড়া করি। প্ল্যানটা ভেবে দ্যাখ জুলু!’
জুলু হল জুলকার-নাইনের ডাকনাম। বাবু আর জুলু দুই বন্ধু। দুই বন্ধুই দেখতে সুন্দর। বাবু তো রীতিমতো রূপবান। ফলে কেউ ওকে রুইদাস ভাবতে পারে না।
— ‘চ ঝালিয়ে নিই। হ্যারিকেনের সবুজ কাচ এনেছে বাবা; সেই আলো ভাগ করে দুজনে পড়ব। ইংরেজি আর বাংলা। দুধে ভিজিয়ে ভুট্টা খাব। সাদা-সাদা।’
জুলুর প্রস্তাবে বাবু চুপ করে রইল।
আকাশে একটি নক্ষত্র টিমটিম করছে; মনে হচ্ছে, দপ করে জ্বলে উঠে তেলের অভাবে নিবে যাবে। বারান্দায় বসে বন্ধুর সঙ্গে সেই নক্ষত্রের দিকে চেয়ে আছে বাবুলাল; তার সর্বাঙ্গে ক্ষুধা নখরে নখরে আঁচড়াচ্ছে।
— ‘কী হল! মা তোকে ডেকে নেবার জন্য বলেছে। বলেছে, বাবুকে সঙ্গে নে আয়; বলবি মাসি ডাকছে।’
একথা শোনামাত্র বুকের মধ্যে তার হৃৎপিণ্ড তড়াক করে লাফিয়ে উঠল আর পেট কলকল করে ডেকে উঠল। খিদেয় এইভাবে পেট ডাকে— এই অভিজ্ঞতা জুলুর হয়েছে অন্যভাবে। রোজার মাসে সে দু’চারটি রোজা রেখে পেট ডাকতে দেখেছে।
জুলু তার দাদিমাকে পেটের উপরকার গেঞ্জি তুলে দেখিয়ে বলেছিল; ‘দ্যাখো দাদি, পেটটা কেমন ডাকছে! মনে হচ্ছে, জল কাটছে।’
দাদিমা বলেছেন, ‘জ্ঞান তো হল! রোজা আর করতে হবে না। তোমার বাকি রোজা আমি দুটি-চারটি করে রেখে পুরা করব বছরভর, তুমি ভেবো না। বাচ্চাদের দু’চারটিই যথেষ্ট। আসলে পেটের জ্বালা না বুঝলে রসুলের ধর্ম হয় না।’
— ‘আজ্ঞে!’
— ‘তুমি আজ্ঞে বলো কেন?’
— ‘জি বললেও চলে, তবে আজ্ঞেই ভাল দাদিমা!’
— ‘তুমি তো কবি সিকন্দর, যা ভাল বোঝো!’
জুলুর একটা ‘তোলা’ অর্থাৎ তুলে রাখা নাম রয়েছে আর সেটি হল, সিকন্দর-এ-আনাম।
ফার্সি ভাষায় সম্রাট আলেকজান্দারকে বলা হয় ‘সিকন্দর’— তাঁরই উপাধি হল, জুলকার-নাইন (নাইন আসলে ‘নেইন’), সিকন্দর-এ-আজম মানে সম্রাট আলেকজান্দার। সিকন্দর-এ-আনাম মানে হল শ্রেষ্ঠ মানুষদের রাজা— মানবশ্রেষ্ঠ।
ভাল ভাল নামের মধ্যেই বাংলার মুসলমান বেঁচে থাকতে চায়। পরিযায়ী শ্রমিকের নামও সিকন্দর।
প্রধানত এই মুসলমানের সঙ্গেই বেঁচে রয়েছে বাবুদের মুচি-টিকরের একটি ছোট জনগোষ্ঠী; এরা হিন্দুর দিকে ঝুঁকে আছে, মুসলমানের দিকেও; কিন্তু ওরা ছোটজাত— অচ্ছুত; বড়ই আশ্চর্য লাগে, এরা কোনও সমাজেরই আপনার কেউ নয়। এরা পর।
জুলুর ফ্যামিলি এইসব মানে না।
উগ্রভাবে জাতপাত-বিরোধী।
বাপ মনসুর আহমেদ বিচিত্র মানুষ। আধেক আস্তিক, আধেক নাস্তিক। বা বলা যায় কখনও আস্তিক, কখনও নাস্তিক— সকালে-বিকালে তাঁর মনের বদল ঘটে। কিছুদিন নামাজ পড়েন, তারপর বন্ধ করে দেন। সকালে পড়লেন, বিকেলে পড়লেন না।
মা জহুরা আহমেদ গভীরভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী নামাজী, ঠাকুমা গভীরতর আমলবাদী নামাজী।
দাদিমা অর্থাৎ ঠাকুমা মনসুরকে বলেন, ‘এমনটি করতে নেই বাপ; এই বলছ আছে, এই বলছ নাই!’
বাবা বলেছেন, ‘হ্যাঁ মা। আমি ওই রকমই।’
— ‘ভবিষ্যতে তুই কী হবি আমান?’
জুলুর কাছে জানতে চেয়েছে বাবু।
জুলু উর্ফে আমান বলেছে, ‘তুইই বল না, আমি কী করব?’
এই দুই বন্ধু স্কুলে ফার্স্ট-সেকেন্ড বয়; বাবু ফার্স্ট হলে, দ্বিতীয় স্থানে থাকে জুলু; স্কুলে জুলুকে ‘আনাম’ নামে ডাকা হয়— সেটি শুনতেও ভাল। ভাবতেও ভাল।
ওরা দু’জনই জীবন-ঔৎসুক্যের মাত্রায় আশ্চর্য আকুল প্রাণী— সব ব্যাপারে এটা-কেন, ওটা-কেন ভাব; পড়ার ব্যাপারে সর্বগ্রাসী। স্কুল লাইব্রেরি ছাড়াও দুটি নদী পেরিয়ে ওরা দুই বন্ধু মিলে নতুন হাসানপুরে যায় ওখানকার গ্রন্থাগার থেকে বই আনতে— তবে কোনও গ্রামেই খবরের কাগজ যায় না।
জুলু তো ১৪ বছর বয়েস থেকে ছড়া-কবিতা লেখে। সেই ছড়ার প্রধান পাঠক বাবু। এখন ওরা দশম শ্রেণির ছাত্র— প্রবল দুর্ভিক্ষের মুখে পড়েছে।
জুলু ব্যঙ্গ করে লিখেছে—
‘খাই খাই করো কেন
এসো-আহা-আহা-রে!
মানুষ বুঝে না পায়,
অন্ন কয় কাহারে!’ ইত্যাদি।
বাংলার কবি বলেছেন, ‘অন্নই ওংকার।’
— ‘আমার এত খিদে পায় কেন, ভাই!’
— ‘ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়।’
— ‘গদ্যের এত দোষ কেন ভাই!’
— ‘ক্ষুধার দেশে পদ্যও সতী থাকতে পারে না।’
— ‘আগে রুটি, তারপর ভগবান।’
— ‘সুকান্ত ছিলেন দুর্ভিক্ষের কবি।’
— ‘২৮ দিন ভাতের হাঁড়ি চড়েনি টিকরে। কুত্তি-বাজরার রুটি খেয়ে মাথা ঘোরার ব্যামো হয়েছে। মাঝে-মাঝে ঢুলে পড়ে যাই। ক্লাসে একদিন পড়ে গেলাম। তখন হাসির হুল্লোড় হল, তারপর সবাই চুপ। ভাবল, ক্লাসের ফার্স্টবয় এভাবে পড়ে যায় কেন? তাই না?’
মানুষ যত অভাবী ততই সে খোদা মানে, একথা ঠিক নয়— তাদের বেশির ভাগই খোদায় আধা বিশ্বাসী, আধা অবিশ্বাসী— তাছাড়া চাইলেই তো ভগবানে অধিকার পাওয়া যায় না। রুইদাসদের মন্দিরে ঢোকার অধিকারই নেই; পূজায় অধিকার দূর থেকে। বাইরে থাকো; ঢাক বাজাও আর কাঁসি বাজাও।
— ‘জানমহম্মদের দোকানে কাঁসি বাঁধা দিতে গেলাম। জানভাই বললে, থালা হলে নিতাম, কাঁসি কী হবে! তা ছাড়া এ জিনিস কাঁই-কাঁই করে কাঁদে; আকালে ওই রকম ‘শোর’ সহ্য হয় না বাবু!’
— ‘ওহ্! বাবুলাল!’
— ‘হ্যাঁ জুলু! সব বর্তন দুর্ভিক্ষে গেল। তোর মনে আছে, রুইদাস বাড়ির কাঁসা-পিতলের বর্তন সূর্যের আলোয় কেমন জ্বলতে থাকে— যেন সেই আলো দিয়ে মায়েরা ঘরের গরিবি ঢেকে রাখে। মনে পড়ে!’
— ‘আগে গেল ঝরা, তারপর এল খরা! কী করবি বল! আমার বাবার তবু মাস-বেতন আছে। প্রাইমারির মাস্টার কিনা; বাবাই তো হেড-পণ্ডিত। কিন্তু ভয় হচ্ছে, ছাত্রের অভাবে স্কুল না বন্ধ হয়ে যায়! আগে ঝরা, পরে খরা, এমন কেন হল! ম্যালথাসের থিয়োরি এবার হায়ার সেকেন্ডারি (একাদশ শ্রেণির উচ্চমাধ্যমিক) ফাইনালে আসছেই, ইলেভেনের দাদারা সব বলাবলি করছিল।’
— ‘ম্যালথাস আসবে না!’
— ‘কেন?’
— ‘যেটা বেশি আসবে মনে হয়, সেটা আসে না। সামনে বছরে আমাদের বেলায় আসবে। কিন্তু বাঁচব তো! ম্যালথাস পড়বারও তো স্টুডেন্ট চাই জুলু!’
— ‘অত নেগেটিভ ভাবলে হয়! চ। এবার তো ঝরা-খরা ক্ষান্তি দিয়েছে বাবু! ধান পাকতে শুরু করেছে। ষাটী মরাইতে এল বলে; মা বলেছে, মুচিডিহি রুইদাস টিকরে দুই-তিন মণ ষাটী ধান খয়রাত করবেন মাস্টারমশাই! মা তো বাবাকে হয় পণ্ডিত বলে, নয় তো মাস্টারমশাই। রাগের সময় পণ্ডিত, মর্জি হলে মাস্টারমশাই। চ তাহলে!’
লক্ষ্মী দাদাকে বলল, ‘তুই যা দাদা, মাসি ডাকছে।’
খিদেয় পুড়ছে লক্ষ্মী, তবু দাদাকে মাস্টার-বাড়ি যেতে বলল।
মানুষ যত অভাবী ততই সে খোদা মানে, একথা ঠিক নয়— তাদের বেশির ভাগই খোদায় আধা বিশ্বাসী, আধা অবিশ্বাসী— তাছাড়া চাইলেই তো ভগবানে অধিকার পাওয়া যায় না। রুইদাসদের মন্দিরে ঢোকার অধিকারই নেই; পূজায় অধিকার দূর থেকে। বাইরে থাকো; ঢাক বাজাও আর কাঁসি বাজাও।
কৌশল্যাও বললেন, ‘যাও, মাসি যখন ডেকেছে। পাও যদি ফ্যানাভাত খেয়ে এসো। মানুষের দয়ার চেয়ে সংসারে বড় কিছু নাই। যাও সৌমিত্র, জহুরা মাসি যখন বলেছে, যেতে হয়।’
সৌমিত্র বাবুর তোলা নাম।
— ‘রুইদাসের এত ভাল নাম, তুই কোথাও পাবি না আমান। আমার ভারি লজ্জা করে।’
— ‘লজ্জা কীসের, মায়ের নাম কৌশল্যা হলে, ছেলের নাম সৌমিত্র হবে না কেন!’
— ‘এবার তুই ক্লাসে ফার্স্ট হবি আলবাত। আমি হব না।’
— ‘কেন! তুইই হবি।’
— ‘না, না। সে আমি চাই না।’
— ‘কেন?’
সেদিন চুপ করে গিয়েছিল বাবু।
কিন্তু জুলু বুঝেছিল, বন্ধুর উচ্চারণ আন্তরিক; যেন বন্ধুর এ কামনা অশেষ; জীবন-সার্থকতার শিখরে দেখতে চায় বন্ধুকে; তারপর তো কলেজ পড়া হবে না বাবুর। বাবা তিন সিকির মজুর, কলেজে ছেলেকে পড়তে দেন, সাধ্য কোথায়! দুর্ভিক্ষের পর ছেলে বাঁচলে পাঁচ সিকার মজুর হবে; খেত-খামারি করে খাবে! সংসার বাঁচবে। একজন ভাল ঢাকি হবে সৌমিত্র। ও যখন কাঁসিকে কাঁই-কাঁই করে কাঁদায় তখন রামায়ণ-মহাভারত ও ব্রহ্মাণ্ড কাঁদতে থাকে— সেই কাঁসি বন্ধক দিতে গিয়ে নিরাশ হয়েছে বাবু। দুর্ভিক্ষের সময়, ছোট-ছোট মুদিখানা বন্ধ হয়ে যায়— লোকে ভাতের থালা বাঁধা দিতে আসে।
জুলকার-নাইন লিখেছে—
‘থালা আছে ভাত নাই
বিষয় কর অবধান—
আমানি খাবার গর্ত,
দেখো বিদ্যমান।’
সৎ ও মহৎ পাঠকমাত্রই জানেন, এই ২০২২ সালে যে, মানবমনের অবধান-শক্তি বাড়ানোই সাহিত্যের কাজ।
টিকর থেকে কাহারপাড়ার দিকে যাচ্ছে দুই বন্ধু। বাবু আর জুলু। বোরাকুলির পুব-মাঠে চাঁদ কিন্তু দিগন্ত ফুঁড়ে উঠেছে; মানুষের বেগড় প্রকাণ্ড মাথার মতো রক্তমাখা চাঁদ। বিশাল আবের মতো। ওরা টিকর থেকে কামু মণ্ডলের পাড়া দিয়ে এসে মাধবপুর হয়ে শিশাপাড়ার খালের ধারে এসে দাঁড়াল; তখনই ভয়াবহ চাঁদটাকে দেখতে পেল।
— ‘চাঁদ এত খারাপ দেখতে হয়!?’
রাজ্যের বিস্ময় চোখে মেখে বলে ওঠে জুলু।
বাবু বলে, ‘হয় বইকি! চাঁদে ঘড়ি মারলে হয় শুনেছি; চাষিরা সেই রকমই তো বলে; ঘড়ি মারে চাঁদ অর্থাৎ সংকেত দেয়— যদি দ্রুত সাদা রং ধরে, বুঝব, এ যাত্রা বেঁচে যাব ভাই! ওই দ্যাখ! পায়ের তলা দিয়ে তিন-চারটে ধানী-ধেড়ে গায়ে ধান মেখে চলে গেল আনাম!’
— ‘আরে তাই তো!’
— ‘তোদের জমিতে গিয়ে নামল জুলু। তোদের ষাটী সাবাড় করে দেবে বন্ধু! কী হবে! আমরা তো আশা করে আছি!’
— ‘অ্যাই, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক। কথা বলিস না। তুই অত কাঁদছিস কেন? শোন বাবু, এত ভয় পাস না। চাঁদ ওঠা দ্যাখ! কতক্ষণে সাদা হয় দ্যাখ; মোতিহারি হয় দ্যাখ! নিধিনগরের বাতাসার মতো হলেও চলবে; বিষ্টুময়রার চিনির খাজার মতো সাদা! দ্যাখ না!’
— ‘তুইও তো কথা বলে যাচ্ছিস জুলু!’
— ‘চেপে বলছি না!’
ইঁদুরেরা ব্যস্ত; ওদের থামবার সময় নেই; কারও কথা কান পেতে শোনার সময় নেই।
৬ বিঘার এই প্লটে ষাটী ধান বুনেছেন মনসুর মাস্টার, দাশু সেখের থেকে কেনা লাঙলে। বিঘা প্রতি মণ ফলন হলে ২৪ মণ ষাটী ফলবে— মাস্টারের ভাগে আসবে পুরো। তার থেকে মণ দুই-চার রুইদাস টিকরে যাবে— তার থেকে এক মণ পাবে হরি রুইদাস। এক মণে ৩০ সের চাল— একমাসের খোরাক হয়ে যাবে বাবুদের। জুলু বলেছে, এক মণে ২৮ সেরের বেশি চাল হয় না বাবা! বাবা বলেছেন, ব্যাপারটা মোটের উপর বলছি কিনা! যা হোক। ষাটীর ফলন আড়াই-তিন মণের বেশি হয়তো হবে না।
— ‘চাঁদের এরকম ঘোলাটে আলো, মেটে সিঁদুরের আভা, কখনও দেখেছিস বাবু?’
— ‘আমাদের বয়েস ১৬-১৭; কী এমন অভিজ্ঞতা বল!’
— ‘জীবনের পক্ষে দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা বিরাট অভিজ্ঞতা বাবুলাল!’
— ‘তুই মুসলমান, আমি মুচি; ঘড়ি মেরে চাঁদ উঠছে, ইঁদুরেরা কী করছে ভগবান জানে জুলকার! গা কেমন সিরসির করছে, শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা ঘাম নামছে আনাম!’
— ‘আচ্ছা! খোদাকেই ডাকি তাহলে! হে খোদা! চাঁদটাকে সাদা পদ্মের রং দাও প্রভু; দ্রুত ওপরে তোলো! ষাটীর কী হল দেখি! ষাটী তো ৬০ দিনে ফলে পেকে ওঠে, তাই নাম ষাটী— একে কবির ভাষায় বলা যায়, অন্নের দ্রুতিলিখন; এটাই ঈশ্বরের বিদ্যাসাগরীয় বর্ণবোধ সৌমিত্র!’
— ‘বিদ্যাসাগর মশাই কি নাস্তিক ছিলেন জুলু!’
— ‘সংশয়বাদী ছিলেন; স্যার নিশিনাথ সেন বলেছেন।’
— ‘আর যাই হোক। বিষয়টা ঈশ্বর ব্যাপারে নেগেটিভ! তাই না, জুলু!’
— ‘হ্যাঁ। বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বরের কোনও জায়গা নেই, জানিস তো! আচ্ছা! ব্যান্ডিকুট কি, এই ধেড়েরা কি, খোদারই সৃষ্টি? তবে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ধেড়েরা বোধহয় ফার্স্টবয়, তাই না? চাঁদ যত উঠবে, ধেড়ের কাজ তত বেড়ে যাবে।’
চাঁদ দ্রুত রুপালি রং ধরতে শুরু করেছে। চাঁদের বেঢপ গড়নটাও বদলে গিয়ে স্বাভাবিক হচ্ছে; ইঁদুরের ব্যস্ততা সত্যি-সত্যিই আরও বেড়ে গেল।
কিন্তু ওরা দুই বন্ধু বুঝতে পারে না, বাস্তবিকই ইঁদুরেরা কী করছিল। ওরা অগত্যা খই-দুধ খেতে নীল কাচের হ্যারিকেনের কাছে আসে।
সাদা খইয়ের ওপর নীল আলো পড়েছে; দুধের উপর নীল আভা; আকাশে চাঁদটা বরফের মতো ঠান্ডা আর সাদা। দক্ষিণের আকাশের তলায় একটি তারা কীসের ঘষা খেয়ে ছেতরে ঝাঁটার মতো হয়ে গেছে।
কোথাও কি ভয়ানক খারাপ কিছু হবে? হওয়ার আর বাকি কী আছে? মাটির উনানে ছাইয়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে সাদা মেনিটা; তুলোর মতন নরম— মেনিও ক্ষুধার্ত। অনেকদিন মাছভাত পায় না। ছাইগুলো পুরনো; কুত্তি-বাজরার রুটি তয়ের করার ছাই। ২৮দিন ভাত খায়নি লক্ষ্মী; খালি ভাত-ভাত করে। কুত্তি-বাজরা-ভুট্টা— কিন্তু দুধে ডুবিয়ে ভুট্টার খই খেতে গিয়ে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল বাবুলাল।
কালী গাইটার দিকে বারবার চোখ চলে যাচ্ছিল বাবুর। ওটার দুধেই স্নান করছে ভুট্টার ভাজা দানা; কালীকে মনে মনে নমঃ করছিল সৌমিত্র।
— ‘কী হল বাবু, খাচ্ছিস না কেন? খা।’ বলে ওঠে জুলকার।
— ‘খাচ্ছি তো!’ বলে ওঠে বাবু।
— ‘খাও। চিন্তা কোরো না সৌমিত্র। বোনের জন্য খই আর দুধ দুই-ই রেখেছি।’ বললেন জহুরা মাসি।
— ‘আমরা গাই-গরুর মাংস খাই না মাসিমা। তবু নিন্দে করে লোকে।’ বলল বাবু।
জহুরা বললেন, ‘আমরাও খাই না। আমার শাশুড়ি সুফি মহিলা কিনা—’
‘আমার খুব সুফি হওয়ার ইচ্ছে মাসিমা! কিন্তু বাবার ইচ্ছে হিন্দু-সমাজে যদি একটু জায়গা হয়!’
বাউল-সুফির পথই শূদ্রপথ; এই পথেই থেকে গেলাম চিরকাল।
— ‘কালী-গাইয়ের জন্য রসিদা বেওয়ার জমি থেকে চাপাতি এনে দেব মাসিমা। দুধ ডবল হবে। সেই দুধের রেখা দিয়ে আমরা ছায়াপথ সাজাব মাসিমা। খইয়ের মতো তারা ফুটবে আকাশে’, বলে পাগলের মতো হাসতে লাগল বাবু।
ও ওরকমই; আমার চেয়েও কবিতা-প্রবণ; কবিতা যে লেখে না, কিন্তু বিচিত্র ধরনের কল্পনা করতে ভালবাসে।
‘তুমি কালীর জন্য চাপাতি আনবে বাবা?’
মা অবাক সুরে জানতে চাইল।
বাবু বলল, ‘আজ্ঞে! দুধ দেখলেই আমার কেমন আনন্দ হয়। দুধ, ঘি, মাখন, ছানা, দই, ঘোল ইত্যাদি প্রভৃতি কত কী! একটা প্রাণী থেকে এত কিছু, কত রকমের মিষ্টান্ন! এবারে ষাটীর চালের পায়েস খাব মাসিমা! তোমাকে কানে-কানে একটা কথা বলতে চাই।’
— ‘কানে! কানে!’
— ‘আজ্ঞে মাসিমা। কানে কানে!’
— ‘কখন?’
— ‘এখনই!’
মিনিট দুই-তিন বাবুর সঙ্গে মায়ের কথা হল— বাড়ির বাইরের প্রাঙ্গণে; খেজুর-তাল-নিম-সজনে ইত্যাদি গাছগুলির তলায়— কাছেই কটি কাঁটাল গাছ; চাঁদের আলোয় কাঁঠাল পাতা ধুয়ে যাচ্ছে; দূরে কোথাও রাত-চরা বকের দল উড়ে গেল।
শিশাডিহির দিকে চলে গেল বাবুলাল; আমাকে কিছু বলেও গেল না। বোনের জন্য দুধ আর ভাজা-ভুট্টার খই সঙ্গে নিয়ে গেছে বাবু।
দুই
লক্ষ্মীর জন্য খই-দুধ। বাপ-মা-ও যেন খায়। বলেটলে কাঁধে কোদাল আর হাতে শাবল; অন্য কাঁধে চটের দু-খানা বস্তা নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল বাবু।
— ‘কী করতে কোথায় যাচ্ছিস বাবু! এত রাত হয়েছে; ব্যাপার কী!’
বলে ওঠে মা; কৌশল্যা।
— ‘জেনে রাখো, লড়তে যাচ্ছি আর কিছু না।’
বলেই হনহন করে এগিয়ে চলল ফার্স্টবয় সৌমিত্র রুইদাস। সঙ্গে নিয়েছে কাঁসি আর সেটা বাজানোর দণ্ড।
যথাস্থানে চলে এল সে। ৬ বিঘার প্লট। দেখল, সব ধান শিষ হয়ে মাটিতে শুয়ে গেছে।
তারপর দেখল, সব গাছে শিষ নেই। ইঁদুরে কেটে নিয়েছে। তারপর দেখল, অসংখ্য ইঁদুর ধান-শিষ নিয়ে গর্তে ঢুকে যাচ্ছে। এরা ধেড়ে বলে মানুষকে ভয় পায় না। এরা মোটা-সোটা, নাদা-নাদা, রোমশ।
ধান চলে যাচ্ছে পাশের তিন বিঘার প্লটে; রসিদা বেওয়ার জমিতে। বাবুলাল কাঁসি বাজাতে শুরু করল; শুরু হল মানুষে-ইঁদুরে লড়াই। আদিম কোনও যুদ্ধ।
একা কোনও এক রুইদাস-পুত্র লড়াইয়ে নেমেছে।
কাঁসি বাজছে।
কাঁই-কাঁই করে কাঁদছে পৃথিবী।
এ কাঁসি বন্ধক নেয়নি জান মহম্মদ মুদি।
তাই এই কাঁসি কাঁদছে।
— ‘সত্য হও, চির-সত্য হও হে কাঁসি।’
— ‘আবহমান হও।’
— ‘যুগ থেকে যুগান্তরে কাঁদো।’
— ‘কাঁদো কাঁসি কাঁদো।’
— ‘অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এক মুচি তোমাকে কাঁদাতে থাকুক। ভাগো, ব্যান্ডিকুট। ভাগো।’
পাগলা বাবুলাল লাফাচ্ছে আর কাঁসি বাজাচ্ছে। দুঃখে আর আনন্দে লাফাচ্ছে।
আনন্দে লাফাচ্ছে আর নিচু জাত বলে তার বুক ভেঙে যাচ্ছে; দরদর করে নিঃশব্দে অশ্রু নামছে চোখ থেকে গাল বেয়ে। সে আনন্দে লাফাচ্ছে এবং জাতি-অপমানে কাঁদছে; চাঁদের রোশনি ঈশ্বর-কৃপায় টলটল করছে চারিদিকে; চারটি রাতচরা বক আকাশের সারা তল্লাটে ছড়িয়ে দিচ্ছে তার অক-অক ডাক; কাঁসি বাজছে আহ্লাদে। নাচছে বাবুলাল।
ব্যান্ডিকুট ভয় পেয়েছে। তারা পালাবার কথা ভাবছে। তারা ভড়কেছে।
— ‘ভাগো!’
মানুষের কণ্ঠস্বরে নিম্নবর্ণের পশু ভয় পেল।
বাবুলাল চিৎকার জুড়ে দিল; আরও জোরে লাফাতে লাগল। আরও জোরে কাঁই-কাঁই করে উঠল কাঁসি।
ব্যান্ডিকুটের গহ্বর ও সুড়ঙ্গে নামল বাবুলাল।
দুই চোখ বড় বড় করে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল সৌমিত্র; তার কাঁসি থেমে গেল।
— ‘হা ভগবান! তুমি এভাবে গরিব ছোটজাতকে বাঁচাতে চাও পিতা!’
ধীরে ধীরে তার গলা থেকে এই সব অপ্রাকৃত কথা বার হয়ে এল। সে ভেবে পেল না, খোদাকে বিশ্বাস করবে না কি নয়?
— ‘ভগবান! আমাকে যখন দিলেই, তখন আর কেড়ে নিও না, হে ঈশ্বর! এই দেশে যেন মানুষ হয়ে বাঁচতে পারি। এ দেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম; অবাক পৃথিবী, সেলাম তোমারে সেলাম!’
এভাবে সুকান্তের কবিতা আবৃত্তি করল বাবুলাল। তারপর ধীরে ধীরে বস্তায় ধান ভরতে লাগল।
তখন পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলো আকাশে, বাতাসে, নিসর্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল।
পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলোটা যেন সন্ধানী চোখ নিয়ে আকাশে, বাতাসে, মাটিতে এবং ষাটী ধানের জমিতে চক্কর দিয়ে ফিরছে। বস্তা ভর্তি করে তুলেছে বাবুলাল।
এই টর্চের আলোটা সে চেনে। এটা চৌকিদারি টর্চের সন্ধানী সংকেত। চৌকিদার লোকনাথের উদ্ধত খবরদারি এই তেরছা আলোর প্রক্ষেপে ছড়াতে ছড়াতে চলে।
এরপর বার কতক হয়দরী হাঁক দেবে লোকনাথ।
লোকনাথ মধ্যবর্ণের মানুষ; অল্পই লেখাপড়া জানে, বিদ্যায় মোটে সড়গড় নয়, বানান করে বই পড়ে; টিপছাপের বদলে নামসই করতে পারে। লোকনাথের বেজায় গুমোর; নিচু জাতকে লোক-দেখিয়ে ঘৃণা করে। মুচিপাড়ার টিকরে যায় না। গেলে, নদীতে চান করে তবে বাড়ি ঢোকে। সে নিজেকে উচ্চবর্ণই ভাবে।
মুচিদের ছায়া মাড়ায় না।
ধানভর্তি বস্তা মাথায় নিয়ে হাঁটছে বাবুলাল।
বাপ আর বোন তাকে ঢুঁড়তে-ঢুঁড়তে শিশাডিহি এসে পৌঁছেছিল, মেয়ে লক্ষ্মীকে পাহারায় রেখে হরিলাল আরও বস্তা আনতে টিকরে ছুটে গেছে; বছর এগারোর বালিকা লক্ষ্মী একা ভয়ে-ভয়ে ধান পাহারা দিচ্ছে। একটা কঞ্চি দিয়ে ইঁদুর তাড়াচ্ছে— যাঃ যাঃ করে চাপা আর্তনাদ করছে। দাদা বলেছে, বস্তা দুই-তিন ধান সাবড়েছে ইঁদুরে, তার বেশি না।
লক্ষ্মী ভয়ে কাঁসি বাজাতে পারছে না। কারণ লোকনাথের ‘জাগো’ ‘জাগো’ হয়দরী শুনেছে।
সে জানে, ‘লুকনাথ’ ভাল লোক না।
রুইদসদের প্রচণ্ড ঘৃণা করে।
মুখের অন্ন কেড়ে নিতেও দ্বিধা করবে না। ধান বাজেয়াপ্ত করে দেবে।
যদিও এই ধানের আসল মালিক জহুরা আহমেদ।
লক্ষ্মী সব জানে। তাই সাহস আছে, ভয়ও আছে।
গর্ত অনেকখানি করেছে ইঁদুরেরা; ধানের সঞ্চয় তিন বস্তাই হবে, তার বেশি না। এক বস্তা মাথায় নিয়ে দাদা তাড়াতাড়ি করে ছুটল। বাবা বস্তা আনতে গেছে।
লোকনাথ বাবুলালকে পিছন থেকে বলে উঠল, ‘এ তোর কী হল রুইদাস। নসু দফাদারকে দিয়ে তোকে অ্যারেস্ট করাব, চ।’
— ‘কেন অ্যারেস্ট করাবে কাকা! কী করলাম, কোন পাপ করলাম জাগা লুকনাথ বাবা!’
— ‘আমি তোর বাবা-কাকা হলাম কবে?’
— ‘মানুষে-মানুষে সম্বন্ধ তো আজকের নয় চৌকিদার মামা! মানুষ জাগে, চোর পালায় লুকনাথ ঝা! আপনি বড় জাত কাকাবাবু।’
— ‘চোপ!’
‘চোপ’ বলে এমনই গর্জে উঠল লোকনাথ যে আকাশের চাঁদটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল।
মাধবপুরের মাঠপাড়া হয়ে বাবুলাল জুলকারদের বাড়ি পৌঁছতে চাইছিল; কাজিপাড়া এসেই নসুর হাতে গ্রেফতার হয়ে গেল সে— আকাশ-ছোঁয়া লম্বা কোহিতুর আমগাছটার সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলা হল সৌমিত্রকে।
মুচিকে ছোঁবে না বলেই নসিহত সেখ দফাদারকে দিয়ে এই কাজ করাল লোকনাথ— লোকনাথ গরিব, কিন্তু উঁচু জাতি।
বাপ খবর পেয়ে ছুটে এল; সঙ্গে দুখানা বস্তা।
বস্তা দেখেই লোকনাথ বলে উঠল, ‘বাপও তাহলে সঙ্গে আছে। বাপ-বেটা মিলে ধানচুরি করছিল। নসু, অ্যাই নসু, বাপটাকেও বেঁধে দে।’
ভযে হরিলাল হাউমাও করে কেঁদে উঠে লোকনাথের পায়ে পড়ে গেল, কিন্তু রক্ষা পেল না।
বাপকেও বাঁধা হল ঘোড়ানিম গাছটার সঙ্গে। কোহিতুরে ছেলে, ঘোড়ানিমে বাপ; সারারাত বাঁধা রইল তারা।
শ্রাবণ মাসের শেষাশেষি বা ভাদ্রের গোড়ায় ষাটী ধান পেকে উঠেছিল; দিনকয় আকাশে কোনও মেঘ ছিল না; শ্রাবণের রোদ সোনার চেয়ে দামি বর্ণে আকাশ-বাতাস উতলা করে রেখেছিল; চাঁদ হয়ে উঠেছিল দেবদূতের আত্মার চেয়ে শুভ্র।
ভোররাতে মেঘ জমল; বৃষ্টি হল; শীতে কেঁপে উঠল পাতলা আধছেঁড়া ফ্রক-পরা লক্ষ্মীর শরীর; সে বৃষ্টির মধ্যেও ইঁদুর তাড়াচ্ছিল আর ভাবছিল দাদা এবং বাবা বৃষ্টি থামলেই ধানের এখানে এসে পৌঁছবে।
রসিদা বেওয়ার ফাঁকা জমিতে সুড়ঙ্গ চালিয়ে দিয়েছে ধেড়ে ইঁদুরের দল; ধানের সঙ্গে খোসা জমেছে; ধান খেয়েছে তারা এবং আস্তও রয়েছে বস্তা-তিন মতন।
বৃষ্টি থামল; রাত্রি কাবার হয়ে গেল।
দিনের আলোয় ইঁদুরেরা অদৃশ্য হয়ে গেল।
বৃষ্টিভেজা শরীরে লক্ষ্মী কাজীপাড়ায় পৌঁছল।
সেখানে দাদা ও বাবাকে বাঁধা অবস্থায় দেখে তার মুখ শুকিয়ে গেল; নিজেকেও তার কেন যেন অন্নের কারণে অপরাধী কিংবা ধানচোর মনে হল; সর্বাঙ্গে তার ধান আর ইঁদুরের গন্ধ; লক্ষ্মীকে দাদা চাপা গলায় বলল, ‘তুই বাড়ি চলে যা লক্ষ্মী; আমাদের ‘বাইশী’ হয়েছে; পানিশমেন্ট হবে সভা বসিয়ে, যা পালা!’
বাইশী হচ্ছে, বাইশ গ্রামের মানুষ নিয়ে অপরাধীর বিচার।
লক্ষ্মী বলল, ‘দাদা আমি যাব না। আমি দেখব।’
— ‘ঠিক আছে। তুই গিয়ে মাসিমাকে বলে আয়, আমরা আটক রয়েছি, মাসি হয়ে রসিদা বেওয়া (বিধবা)কে খবর করবি; তোমার জমি থেকে ধান চুরি হয়েছে, চোর দেখবে চলো বলবি। যা, দৌড় লাগা।’
— ‘আচ্ছা!’ বলে জুলকারদের বাড়ির দিকে উড়ে চলল লক্ষ্মী।
তিন
গল্পটা এখন জুলকার-নাইন বলছে না, বলছে অন্য কোনও আনাম। মজলিস শুরু হল সকাল দশটায়। জুলকারের বাবাও এসেছেন লোকনাথের কারসাজি দেখতে।
মনসুর জানেন, লোকনাথ জাতি-অহংকারে আর্য-অপেক্ষা বাড়া। জহুরা কিন্তু রসিদাকে জড়িয়ে ধরে কাঠের গুঁড়ির পরে বসে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছেন গাছে-বাঁধা বাপ-বেটার দিকে। আর যত যত মুরুব্বি এসেছেন তাঁদের দিকে তাকাচ্ছেন; জহুরার গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্মী; লক্ষ্মীর মা কৌশল্যার চোখ দিয়ে নিঃশব্দে জল ঝরছে।
ধানের বস্তার দিকে মনসুর মাঝেমাঝে দেখছেন।
তবারক মিঞা হরিলালকে প্রশ্ন করলেন, ‘কী হে হরি, আকালের দিনে ছেলেকে নিয়ে মনসুর মাস্টারের জমির ধান সাবাড় করলে!’
হরি তো বোকা-গুর্বো; বললে, ‘কী করব! ২৮ দিন ভাত খাইনি মিঞাসাব! বেগতিকে সব ঘটে গেল বাবা! সদ্যমরা গরুর গো-মাংস চুরি করি নাই, মিঞাভাই; টাটকা ধান বস্তায় ভরেছি।’
তখন তবারক বললেন বাবুর উদ্দেশে, ‘শিক্ষিত হয়ে তুমি এই কাজ করতে পারলে বাবু!’
বাবুলাল বলল, ‘শিক্ষিত বলেই তো পারলাম জনাব।’
— ‘কীরকম!’
বড্ড অবাক হয়ে তবারক মুনশী প্রশ্ন করলেন সৌমিত্রকে।
সৌমিত্র বলল, ‘আজ্ঞে। পড়ে-বুঝেই চুরি করেছি।’
— ‘বল, সেটা!’
— ‘কী বলব?’
— ‘পড়েটড়ে কী বুঝেছ তুমি!’
— ‘বইটা কিন্তু ইংরেজিতে লেখা।’
গোলমুখো, মাথা নেড়া, থুতনিতে দু’চার নরি দাড়ি তবারক ধাক্কা খেলেন ইংরেজির নাম শুনে; বোকা-বোকা হেসে আমতা-আমতা করে তবা মুনশী বললেন, ‘যা হোক, তা হোক, তবো বল শুনি, কী পড়েছ, বাংলা তর্জমা করে দিলেই সবাই বুঝে যাব।’
— ‘জনাব, এখানে ইংরেজি কেউ জানে না। জানে মনসুর মাস্টার আর তেনার পুত্র জুলকার। জুলকারকে বইটা পড়তে দিয়েছিলাম, ওর পড়বার সময় হয়নি। মাসিমার কাছে বইখানা আছে; নতুন হাসানপুর পাঠাগারের বই; পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা রইস মণ্ডলের ব্যক্তিগত সংগ্রহের বই; উনি সে বই পাঠাগারকে দান করে গেছেন, বইটি পূর্ববঙ্গ থেকে আনিয়েছিলেন। বইটির লেখক জেমস টেলর; ১৮৩৯ সালে এই বই লেখা হয়েছিল; রইস সে বই একশো বছর পর বাংলা বাজার থেকে জোগাড় করেন। সে বই ১৯৬৮ সালের দুর্ভিক্ষের বছর আমি পড়েছি। মাস-তিন আগে।’
মনসুর বললেন, ‘যাও জুলকার। নিয়ে এসো, বই।’
জহুরা তাঁর কোমর থেকে চাবি বার করে ছেলের হাতে দিয়ে বললেন, ‘কাঠের বাক্সে পাবে, জলদি করে আনো।’
জুলকার ছুটল।
বই এল। তবারক মুনশী বই হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, ‘তুমি যেমন আরবি জানু না, আমি তেমনই ইংরাজি জানু না বাবুলাল; শোধবোধ হয়্যা গেল। ইবার কও কী নিকেছে এই কিতাবে। অ্যাই কে আছিস, বাপ-বেটার বাঁধন খুল্যা দে।’
বাঁধন খোলা হল।
— ‘কও।’
— ‘আজ্ঞে।’
বাবুলাল বলতে শুরু করল বৃত্তান্ত। তা নিম্নরূপ:
বইটির নাম, ‘টপোগ্রাফি অফ ঢাকা’— প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা মিলিটারি অরফান প্রেস থেকে। প্রকাশকাল, ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ।
— ‘ব্যাস ব্যাস! আর শুনতে চাই না। এখন বল, ধান তুমি কীভাবে বস্তায় ভরলে? টেলর সাহেব ধানের ব্যাপারে কিছু বলেছেন?’
বলে ওঠেন তবা মুনশি।
বাবু বলল, ‘ সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছি মুনশি সাহেব। ওই বইতে ব্যান্ডিকুট ইঁদুরের কথা আছে, বাংলায় এদের ধেড়ে ইঁদুর বলে— এরা চাষির ধানের ক্ষতি করে। টেলর সাহেব বিবরণ দিয়েছেন, এই ইঁদুরেরা ধান নিয়ে মাটির নীচে তাদের কুঠরিতে জড়ো করে রাখে। এই সব কুঠরির সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ রক্ষার জন্য মাটি খুঁড়ে পথ তৈরি করে। গরিব লোকেরা হামেশাই এই সব ধেড়েদের বাসায় সন্ধানে ফেরে আর এক-একটা বাসা থেকে অনেক সময় এক থেকে দু’মণ ধান পেয়ে থাকে। দেখা গেল, ঠিক তেমনটাই শিশাডিহির মাঠে, জুলকারদের ষাটী ধান নিয়ে ঘটনা ঘটে গেছে। মাসিমাকে বলেছি ইঁদুরের মুখ থেকে অন্ন কেড়ে নিতে হলে হবে; তুমি কী বলছ বলো!’
— ‘আপনি কিছু বলবেন জহুরা আহমেদ?’
জানতে চান মুনশি।
হঠাৎ রসিদা বলে ওঠেন, ‘আকালের ধান ইঁদুরের মুখ থেকে নিলে লুকনাথের পক্ষে টর্চ ঘুমানোর কী থাকতে পারে! বাবুলাল পেটের দুঃখে লড়ছে; আমার জমিতে সুড়ঙ্গ করেছে ইঁদুরে, তার আমি কী করব? আমাকে কেন বাইশীতে ডাকা হল?’
জহুরা বলে ওঠেন, ‘আমাকে সব বলেই বাবু যা করবার করেছে; ও ওই বস্তা মাথায় করে আমার উঠোনে আনছিল; ওকে গাছে বাঁধা হল কেন আর হরিলালকেই বা এত অপদস্থ করা কেন? বাবু বলেছে, মাসিমা ষাটীর পায়েসে যেন জুলুর সঙ্গে ভাগ পাই। ব্যাস। এইই তো কথা! আমি বলেছি একবস্তা ধান মুচিপাড়ার টিকরে যাবে। ২৮ দিন ভাত খায়নি হরির পরিবার। দুর্ভিক্ষের সময় অত টর্চ-মারামারি কোরো না লোকনাথ। বাবুলালও আমার ছেলে; আমি জাত মানি না। অন্নই ভগবান। ব্যাস।’
শেষ কথা:
তারপর রুইদাস টিকর (ডিহির) থেকে রুইদাসরা এল ঢাক-ঢোল-কাঁসি নিয়ে শিশাডিহি। প্রচণ্ড বাদ্যি শুরু হল। ধেড়ে ইঁদুরের দল ষাটী ধানের সুড়ঙ্গ ছেড়ে পালাতে লাগল ভৈরব নদীর দিকে। নদীর বেগবান স্রোতে ঝাঁপ দিল।
রুইদাস টিকর ভাতের গন্ধে ভরে গেল।
রুইদাসরা মারী ও মন্বন্তরে মরেনি।
বাবুলাল বুড়ো হয়েছে।
ঢাক বাজাচ্ছে শেয়ালদা স্টেশনের চাতালে।
তার সঙ্গে কাঁসি বাজাচ্ছে তার নাতি।
এখন মারী ও দুর্ভিক্ষের ভারতে প্রতিদিন আত্মহত্যা করছে গরিব। প্রতিদিন অন্তত ৫০০জন করে।
তথাপি মারী ও মন্বন্তর অতিক্রম করে বাবুলালের ঢাক ও কাঁসি।
কোভিড ও ওমিক্রন তাড়াচ্ছে রুইদাস। ঢাক আর কাঁসি বেজেই চলেছে। থামছে না।
তাই ধেড়ে ইঁদুরের গল্পের কোনও শেষ নেই।
ওই ঢাক-ঢোল হল এই মারী ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিবাদ।
কেননা ওই বাদ্য মারী ও দুর্ভিক্ষের তাড়ানোর ক্ষেত্রে বাঙালির নিজস্ব পদ্ধতি।
বাবুলাল পাগলের মতো নাচছে আর ঢাক পেটাচ্ছে; তার নাতিও আশ্চর্য নাচ দিয়েছে কলকেতায়।
মাসি জহুরার রান্না করা ষাটী ধানের পরমান্ন আজও বাবুলাল রুইদাসের জিভে লেগে আছে; সে-কথা মনে এল বলে বাবুর বাদ্যি-বাজনার তোড় আরও বেড়ে গেল।
তার ছোট্ট নাতি ননি রুইদাস তালবাদ্যির প্রতিযোগিতায় দাদুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল; ননি, লক্ষ্মী রুইদাসের ছেলের ছেলে, ভাল নাম উত্তমকুমার।
সৌমিত্র বাবুর তোলা নাম।
— ‘রুইদাসের এত ভাল নাম, তুই কোথাও পাবি না আমান। আমার ভারি লজ্জা করে।’
— ‘লজ্জা কীসের, মায়ের নাম কৌশল্যা হলে, ছেলের নাম সৌমিত্র হবে না কেন!’
— ‘এবার তুই ক্লাসে ফার্স্ট হবি আলবাত। আমি হব না।’
— ‘কেন! তুইই হবি।’
— ‘না, না। সে আমি চাই না।’
— ‘কেন?’
সেদিন চুপ করে গিয়েছিল বাবু।
কিন্তু জুলু বুঝেছিল, বন্ধুর উচ্চারণ আন্তরিক; যেন বন্ধুর এ কামনা অশেষ; জীবন-সার্থকতার শিখরে দেখতে চায় বন্ধুকে; তারপর তো কলেজ পড়া হবে না বাবুর। বাবা তিন সিকির মজুর, কলেজে ছেলেকে পড়তে দেন, সাধ্য কোথায়! দুর্ভিক্ষের পর ছেলে বাঁচলে পাঁচ সিকার মজুর হবে; খেত-খামারি করে খাবে! সংসার বাঁচবে। একজন ভাল ঢাকি হবে সৌমিত্র। ও যখন কাঁসিকে কাঁই-কাঁই করে কাঁদায় তখন রামায়ণ-মহাভারত ও ব্রহ্মাণ্ড কাঁদতে থাকে— সেই কাঁসি বন্ধক দিতে গিয়ে নিরাশ হয়েছে বাবু। দুর্ভিক্ষের সময়, ছোট-ছোট মুদিখানা বন্ধ হয়ে যায়— লোকে ভাতের থালা বাঁধা দিতে আসে।
জুলকার-নাইন লিখেছে—
‘থালা আছে ভাত নাই
বিষয় কর অবধান—
আমানি খাবার গর্ত,
দেখো বিদ্যমান।’
সৎ ও মহৎ পাঠকমাত্রই জানেন, এই ২০২২ সালে যে, মানবমনের অবধান-শক্তি বাড়ানোই সাহিত্যের কাজ।
টিকর থেকে কাহারপাড়ার দিকে যাচ্ছে দুই বন্ধু। বাবু আর জুলু। বোরাকুলির পুব-মাঠে চাঁদ কিন্তু দিগন্ত ফুঁড়ে উঠেছে; মানুষের বেগড় প্রকাণ্ড মাথার মতো রক্তমাখা চাঁদ। বিশাল আবের মতো। ওরা টিকর থেকে কামু মণ্ডলের পাড়া দিয়ে এসে মাধবপুর হয়ে শিশাপাড়ার খালের ধারে এসে দাঁড়াল; তখনই ভয়াবহ চাঁদটাকে দেখতে পেল।
— ‘চাঁদ এত খারাপ দেখতে হয়!?’
রাজ্যের বিস্ময় চোখে মেখে বলে ওঠে জুলু।
বাবু বলে, ‘হয় বইকি! চাঁদে ঘড়ি মারলে হয় শুনেছি; চাষিরা সেই রকমই তো বলে; ঘড়ি মারে চাঁদ অর্থাৎ সংকেত দেয়— যদি দ্রুত সাদা রং ধরে, বুঝব, এ যাত্রা বেঁচে যাব ভাই! ওই দ্যাখ! পায়ের তলা দিয়ে তিন-চারটে ধানী-ধেড়ে গায়ে ধান মেখে চলে গেল আনাম!’
— ‘আরে তাই তো!’
— ‘তোদের জমিতে গিয়ে নামল জুলু। তোদের ষাটী সাবাড় করে দেবে বন্ধু! কী হবে! আমরা তো আশা করে আছি!’
— ‘অ্যাই, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক। কথা বলিস না। তুই অত কাঁদছিস কেন? শোন বাবু, এত ভয় পাস না। চাঁদ ওঠা দ্যাখ! কতক্ষণে সাদা হয় দ্যাখ; মোতিহারি হয় দ্যাখ! নিধিনগরের বাতাসার মতো হলেও চলবে; বিষ্টুময়রার চিনির খাজার মতো সাদা! দ্যাখ না!’
— ‘তুইও তো কথা বলে যাচ্ছিস জুলু!’
— ‘চেপে বলছি না!’
ইঁদুরেরা ব্যস্ত; ওদের থামবার সময় নেই; কারও কথা কান পেতে শোনার সময় নেই।
৬ বিঘার এই প্লটে ষাটী ধান বুনেছেন মনসুর মাস্টার, দাশু সেখের থেকে কেনা লাঙলে। বিঘা প্রতি মণ ফলন হলে ২৪ মণ ষাটী ফলবে— মাস্টারের ভাগে আসবে পুরো। তার থেকে মণ দুই-চার রুইদাস টিকরে যাবে— তার থেকে এক মণ পাবে হরি রুইদাস। এক মণে ৩০ সের চাল— একমাসের খোরাক হয়ে যাবে বাবুদের। জুলু বলেছে, এক মণে ২৮ সেরের বেশি চাল হয় না বাবা! বাবা বলেছেন, ব্যাপারটা মোটের উপর বলছি কিনা! যা হোক। ষাটীর ফলন আড়াই-তিন মণের বেশি হয়তো হবে না।
— ‘চাঁদের এরকম ঘোলাটে আলো, মেটে সিঁদুরের আভা, কখনও দেখেছিস বাবু?’
— ‘আমাদের বয়েস ১৬-১৭; কী এমন অভিজ্ঞতা বল!’
— ‘জীবনের পক্ষে দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা বিরাট অভিজ্ঞতা বাবুলাল!’
— ‘তুই মুসলমান, আমি মুচি; ঘড়ি মেরে চাঁদ উঠছে, ইঁদুরেরা কী করছে ভগবান জানে জুলকার! গা কেমন সিরসির করছে, শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা ঘাম নামছে আনাম!’
— ‘আচ্ছা! খোদাকেই ডাকি তাহলে! হে খোদা! চাঁদটাকে সাদা পদ্মের রং দাও প্রভু; দ্রুত ওপরে তোলো! ষাটীর কী হল দেখি! ষাটী তো ৬০ দিনে ফলে পেকে ওঠে, তাই নাম ষাটী— একে কবির ভাষায় বলা যায়, অন্নের দ্রুতিলিখন; এটাই ঈশ্বরের বিদ্যাসাগরীয় বর্ণবোধ সৌমিত্র!’
— ‘বিদ্যাসাগর মশাই কি নাস্তিক ছিলেন জুলু!’
— ‘সংশয়বাদী ছিলেন; স্যার নিশিনাথ সেন বলেছেন।’
— ‘আর যাই হোক। বিষয়টা ঈশ্বর ব্যাপারে নেগেটিভ! তাই না, জুলু!’
— ‘হ্যাঁ। বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বরের কোনও জায়গা নেই, জানিস তো! আচ্ছা! ব্যান্ডিকুট কি, এই ধেড়েরা কি, খোদারই সৃষ্টি? তবে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ধেড়েরা বোধহয় ফার্স্টবয়, তাই না? চাঁদ যত উঠবে, ধেড়ের কাজ তত বেড়ে যাবে।’
চাঁদ দ্রুত রুপালি রং ধরতে শুরু করেছে। চাঁদের বেঢপ গড়নটাও বদলে গিয়ে স্বাভাবিক হচ্ছে; ইঁদুরের ব্যস্ততা সত্যি-সত্যিই আরও বেড়ে গেল।
কিন্তু ওরা দুই বন্ধু বুঝতে পারে না, বাস্তবিকই ইঁদুরেরা কী করছিল। ওরা অগত্যা খই-দুধ খেতে নীল কাচের হ্যারিকেনের কাছে আসে।
সাদা খইয়ের ওপর নীল আলো পড়েছে; দুধের উপর নীল আভা; আকাশে চাঁদটা বরফের মতো ঠান্ডা আর সাদা। দক্ষিণের আকাশের তলায় একটি তারা কীসের ঘষা খেয়ে ছেতরে ঝাঁটার মতো হয়ে গেছে।
কোথাও কি ভয়ানক খারাপ কিছু হবে? হওয়ার আর বাকি কী আছে? মাটির উনানে ছাইয়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে সাদা মেনিটা; তুলোর মতন নরম— মেনিও ক্ষুধার্ত। অনেকদিন মাছভাত পায় না। ছাইগুলো পুরনো; কুত্তি-বাজরার রুটি তয়ের করার ছাই। ২৮দিন ভাত খায়নি লক্ষ্মী; খালি ভাত-ভাত করে। কুত্তি-বাজরা-ভুট্টা— কিন্তু দুধে ডুবিয়ে ভুট্টার খই খেতে গিয়ে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল বাবুলাল।
কালী গাইটার দিকে বারবার চোখ চলে যাচ্ছিল বাবুর। ওটার দুধেই স্নান করছে ভুট্টার ভাজা দানা; কালীকে মনে মনে নমঃ করছিল সৌমিত্র।
— ‘কী হল বাবু, খাচ্ছিস না কেন? খা।’ বলে ওঠে জুলকার।
— ‘খাচ্ছি তো!’ বলে ওঠে বাবু।
— ‘খাও। চিন্তা কোরো না সৌমিত্র। বোনের জন্য খই আর দুধ দুই-ই রেখেছি।’ বললেন জহুরা মাসি।
— ‘আমরা গাই-গরুর মাংস খাই না মাসিমা। তবু নিন্দে করে লোকে।’ বলল বাবু।
জহুরা বললেন, ‘আমরাও খাই না। আমার শাশুড়ি সুফি মহিলা কিনা—’
‘আমার খুব সুফি হওয়ার ইচ্ছে মাসিমা! কিন্তু বাবার ইচ্ছে হিন্দু-সমাজে যদি একটু জায়গা হয়!’
বাউল-সুফির পথই শূদ্রপথ; এই পথেই থেকে গেলাম চিরকাল।
— ‘কালী-গাইয়ের জন্য রসিদা বেওয়ার জমি থেকে চাপাতি এনে দেব মাসিমা। দুধ ডবল হবে। সেই দুধের রেখা দিয়ে আমরা ছায়াপথ সাজাব মাসিমা। খইয়ের মতো তারা ফুটবে আকাশে’, বলে পাগলের মতো হাসতে লাগল বাবু।
ও ওরকমই; আমার চেয়েও কবিতা-প্রবণ; কবিতা যে লেখে না, কিন্তু বিচিত্র ধরনের কল্পনা করতে ভালবাসে।
‘তুমি কালীর জন্য চাপাতি আনবে বাবা?’
মা অবাক সুরে জানতে চাইল।
বাবু বলল, ‘আজ্ঞে! দুধ দেখলেই আমার কেমন আনন্দ হয়। দুধ, ঘি, মাখন, ছানা, দই, ঘোল ইত্যাদি প্রভৃতি কত কী! একটা প্রাণী থেকে এত কিছু, কত রকমের মিষ্টান্ন! এবারে ষাটীর চালের পায়েস খাব মাসিমা! তোমাকে কানে-কানে একটা কথা বলতে চাই।’
— ‘কানে! কানে!’
— ‘আজ্ঞে মাসিমা। কানে কানে!’
— ‘কখন?’
— ‘এখনই!’
মিনিট দুই-তিন বাবুর সঙ্গে মায়ের কথা হল— বাড়ির বাইরের প্রাঙ্গণে; খেজুর-তাল-নিম-সজনে ইত্যাদি গাছগুলির তলায়— কাছেই কটি কাঁটাল গাছ; চাঁদের আলোয় কাঁঠাল পাতা ধুয়ে যাচ্ছে; দূরে কোথাও রাত-চরা বকের দল উড়ে গেল।
শিশাডিহির দিকে চলে গেল বাবুলাল; আমাকে কিছু বলেও গেল না। বোনের জন্য দুধ আর ভাজা-ভুট্টার খই সঙ্গে নিয়ে গেছে বাবু।
দুই
লক্ষ্মীর জন্য খই-দুধ। বাপ-মা-ও যেন খায়। বলেটলে কাঁধে কোদাল আর হাতে শাবল; অন্য কাঁধে চটের দু-খানা বস্তা নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল বাবু।
— ‘কী করতে কোথায় যাচ্ছিস বাবু! এত রাত হয়েছে; ব্যাপার কী!’
বলে ওঠে মা; কৌশল্যা।
— ‘জেনে রাখো, লড়তে যাচ্ছি আর কিছু না।’
বলেই হনহন করে এগিয়ে চলল ফার্স্টবয় সৌমিত্র রুইদাস। সঙ্গে নিয়েছে কাঁসি আর সেটা বাজানোর দণ্ড।
যথাস্থানে চলে এল সে। ৬ বিঘার প্লট। দেখল, সব ধান শিষ হয়ে মাটিতে শুয়ে গেছে।
তারপর দেখল, সব গাছে শিষ নেই। ইঁদুরে কেটে নিয়েছে। তারপর দেখল, অসংখ্য ইঁদুর ধান-শিষ নিয়ে গর্তে ঢুকে যাচ্ছে। এরা ধেড়ে বলে মানুষকে ভয় পায় না। এরা মোটা-সোটা, নাদা-নাদা, রোমশ।
ধান চলে যাচ্ছে পাশের তিন বিঘার প্লটে; রসিদা বেওয়ার জমিতে। বাবুলাল কাঁসি বাজাতে শুরু করল; শুরু হল মানুষে-ইঁদুরে লড়াই। আদিম কোনও যুদ্ধ।
একা কোনও এক রুইদাস-পুত্র লড়াইয়ে নেমেছে।
কাঁসি বাজছে।
কাঁই-কাঁই করে কাঁদছে পৃথিবী।
এ কাঁসি বন্ধক নেয়নি জান মহম্মদ মুদি।
তাই এই কাঁসি কাঁদছে।
— ‘সত্য হও, চির-সত্য হও হে কাঁসি।’
— ‘আবহমান হও।’
— ‘যুগ থেকে যুগান্তরে কাঁদো।’
— ‘কাঁদো কাঁসি কাঁদো।’
— ‘অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এক মুচি তোমাকে কাঁদাতে থাকুক। ভাগো, ব্যান্ডিকুট। ভাগো।’
পাগলা বাবুলাল লাফাচ্ছে আর কাঁসি বাজাচ্ছে। দুঃখে আর আনন্দে লাফাচ্ছে।
আনন্দে লাফাচ্ছে আর নিচু জাত বলে তার বুক ভেঙে যাচ্ছে; দরদর করে নিঃশব্দে অশ্রু নামছে চোখ থেকে গাল বেয়ে। সে আনন্দে লাফাচ্ছে এবং জাতি-অপমানে কাঁদছে; চাঁদের রোশনি ঈশ্বর-কৃপায় টলটল করছে চারিদিকে; চারটি রাতচরা বক আকাশের সারা তল্লাটে ছড়িয়ে দিচ্ছে তার অক-অক ডাক; কাঁসি বাজছে আহ্লাদে। নাচছে বাবুলাল।
ব্যান্ডিকুট ভয় পেয়েছে। তারা পালাবার কথা ভাবছে। তারা ভড়কেছে।
— ‘ভাগো!’
মানুষের কণ্ঠস্বরে নিম্নবর্ণের পশু ভয় পেল।
বাবুলাল চিৎকার জুড়ে দিল; আরও জোরে লাফাতে লাগল। আরও জোরে কাঁই-কাঁই করে উঠল কাঁসি।
ব্যান্ডিকুটের গহ্বর ও সুড়ঙ্গে নামল বাবুলাল।
দুই চোখ বড় বড় করে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল সৌমিত্র; তার কাঁসি থেমে গেল।
— ‘হা ভগবান! তুমি এভাবে গরিব ছোটজাতকে বাঁচাতে চাও পিতা!’
ধীরে ধীরে তার গলা থেকে এই সব অপ্রাকৃত কথা বার হয়ে এল। সে ভেবে পেল না, খোদাকে বিশ্বাস করবে না কি নয়?
— ‘ভগবান! আমাকে যখন দিলেই, তখন আর কেড়ে নিও না, হে ঈশ্বর! এই দেশে যেন মানুষ হয়ে বাঁচতে পারি। এ দেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম; অবাক পৃথিবী, সেলাম তোমারে সেলাম!’
এভাবে সুকান্তের কবিতা আবৃত্তি করল বাবুলাল। তারপর ধীরে ধীরে বস্তায় ধান ভরতে লাগল।
তখন পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলো আকাশে, বাতাসে, নিসর্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল।
পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলোটা যেন সন্ধানী চোখ নিয়ে আকাশে, বাতাসে, মাটিতে এবং ষাটী ধানের জমিতে চক্কর দিয়ে ফিরছে। বস্তা ভর্তি করে তুলেছে বাবুলাল।
এই টর্চের আলোটা সে চেনে। এটা চৌকিদারি টর্চের সন্ধানী সংকেত। চৌকিদার লোকনাথের উদ্ধত খবরদারি এই তেরছা আলোর প্রক্ষেপে ছড়াতে ছড়াতে চলে।
এরপর বার কতক হয়দরী হাঁক দেবে লোকনাথ।
লোকনাথ মধ্যবর্ণের মানুষ; অল্পই লেখাপড়া জানে, বিদ্যায় মোটে সড়গড় নয়, বানান করে বই পড়ে; টিপছাপের বদলে নামসই করতে পারে। লোকনাথের বেজায় গুমোর; নিচু জাতকে লোক-দেখিয়ে ঘৃণা করে। মুচিপাড়ার টিকরে যায় না। গেলে, নদীতে চান করে তবে বাড়ি ঢোকে। সে নিজেকে উচ্চবর্ণই ভাবে।
মুচিদের ছায়া মাড়ায় না।
ধানভর্তি বস্তা মাথায় নিয়ে হাঁটছে বাবুলাল।
বাপ আর বোন তাকে ঢুঁড়তে-ঢুঁড়তে শিশাডিহি এসে পৌঁছেছিল, মেয়ে লক্ষ্মীকে পাহারায় রেখে হরিলাল আরও বস্তা আনতে টিকরে ছুটে গেছে; বছর এগারোর বালিকা লক্ষ্মী একা ভয়ে-ভয়ে ধান পাহারা দিচ্ছে। একটা কঞ্চি দিয়ে ইঁদুর তাড়াচ্ছে— যাঃ যাঃ করে চাপা আর্তনাদ করছে। দাদা বলেছে, বস্তা দুই-তিন ধান সাবড়েছে ইঁদুরে, তার বেশি না।
লক্ষ্মী ভয়ে কাঁসি বাজাতে পারছে না। কারণ লোকনাথের ‘জাগো’ ‘জাগো’ হয়দরী শুনেছে।
সে জানে, ‘লুকনাথ’ ভাল লোক না।
রুইদসদের প্রচণ্ড ঘৃণা করে।
মুখের অন্ন কেড়ে নিতেও দ্বিধা করবে না। ধান বাজেয়াপ্ত করে দেবে।
যদিও এই ধানের আসল মালিক জহুরা আহমেদ।
লক্ষ্মী সব জানে। তাই সাহস আছে, ভয়ও আছে।
গর্ত অনেকখানি করেছে ইঁদুরেরা; ধানের সঞ্চয় তিন বস্তাই হবে, তার বেশি না। এক বস্তা মাথায় নিয়ে দাদা তাড়াতাড়ি করে ছুটল। বাবা বস্তা আনতে গেছে।
লোকনাথ বাবুলালকে পিছন থেকে বলে উঠল, ‘এ তোর কী হল রুইদাস। নসু দফাদারকে দিয়ে তোকে অ্যারেস্ট করাব, চ।’
— ‘কেন অ্যারেস্ট করাবে কাকা! কী করলাম, কোন পাপ করলাম জাগা লুকনাথ বাবা!’
— ‘আমি তোর বাবা-কাকা হলাম কবে?’
— ‘মানুষে-মানুষে সম্বন্ধ তো আজকের নয় চৌকিদার মামা! মানুষ জাগে, চোর পালায় লুকনাথ ঝা! আপনি বড় জাত কাকাবাবু।’
— ‘চোপ!’
‘চোপ’ বলে এমনই গর্জে উঠল লোকনাথ যে আকাশের চাঁদটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল।
মাধবপুরের মাঠপাড়া হয়ে বাবুলাল জুলকারদের বাড়ি পৌঁছতে চাইছিল; কাজিপাড়া এসেই নসুর হাতে গ্রেফতার হয়ে গেল সে— আকাশ-ছোঁয়া লম্বা কোহিতুর আমগাছটার সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলা হল সৌমিত্রকে।
মুচিকে ছোঁবে না বলেই নসিহত সেখ দফাদারকে দিয়ে এই কাজ করাল লোকনাথ— লোকনাথ গরিব, কিন্তু উঁচু জাতি।
বাপ খবর পেয়ে ছুটে এল; সঙ্গে দুখানা বস্তা।
বস্তা দেখেই লোকনাথ বলে উঠল, ‘বাপও তাহলে সঙ্গে আছে। বাপ-বেটা মিলে ধানচুরি করছিল। নসু, অ্যাই নসু, বাপটাকেও বেঁধে দে।’
ভযে হরিলাল হাউমাও করে কেঁদে উঠে লোকনাথের পায়ে পড়ে গেল, কিন্তু রক্ষা পেল না।
বাপকেও বাঁধা হল ঘোড়ানিম গাছটার সঙ্গে। কোহিতুরে ছেলে, ঘোড়ানিমে বাপ; সারারাত বাঁধা রইল তারা।
শ্রাবণ মাসের শেষাশেষি বা ভাদ্রের গোড়ায় ষাটী ধান পেকে উঠেছিল; দিনকয় আকাশে কোনও মেঘ ছিল না; শ্রাবণের রোদ সোনার চেয়ে দামি বর্ণে আকাশ-বাতাস উতলা করে রেখেছিল; চাঁদ হয়ে উঠেছিল দেবদূতের আত্মার চেয়ে শুভ্র।
ভোররাতে মেঘ জমল; বৃষ্টি হল; শীতে কেঁপে উঠল পাতলা আধছেঁড়া ফ্রক-পরা লক্ষ্মীর শরীর; সে বৃষ্টির মধ্যেও ইঁদুর তাড়াচ্ছিল আর ভাবছিল দাদা এবং বাবা বৃষ্টি থামলেই ধানের এখানে এসে পৌঁছবে।
রসিদা বেওয়ার ফাঁকা জমিতে সুড়ঙ্গ চালিয়ে দিয়েছে ধেড়ে ইঁদুরের দল; ধানের সঙ্গে খোসা জমেছে; ধান খেয়েছে তারা এবং আস্তও রয়েছে বস্তা-তিন মতন।
বৃষ্টি থামল; রাত্রি কাবার হয়ে গেল।
দিনের আলোয় ইঁদুরেরা অদৃশ্য হয়ে গেল।
বৃষ্টিভেজা শরীরে লক্ষ্মী কাজীপাড়ায় পৌঁছল।
সেখানে দাদা ও বাবাকে বাঁধা অবস্থায় দেখে তার মুখ শুকিয়ে গেল; নিজেকেও তার কেন যেন অন্নের কারণে অপরাধী কিংবা ধানচোর মনে হল; সর্বাঙ্গে তার ধান আর ইঁদুরের গন্ধ; লক্ষ্মীকে দাদা চাপা গলায় বলল, ‘তুই বাড়ি চলে যা লক্ষ্মী; আমাদের ‘বাইশী’ হয়েছে; পানিশমেন্ট হবে সভা বসিয়ে, যা পালা!’
বাইশী হচ্ছে, বাইশ গ্রামের মানুষ নিয়ে অপরাধীর বিচার।
লক্ষ্মী বলল, ‘দাদা আমি যাব না। আমি দেখব।’
— ‘ঠিক আছে। তুই গিয়ে মাসিমাকে বলে আয়, আমরা আটক রয়েছি, মাসি হয়ে রসিদা বেওয়া (বিধবা)কে খবর করবি; তোমার জমি থেকে ধান চুরি হয়েছে, চোর দেখবে চলো বলবি। যা, দৌড় লাগা।’
— ‘আচ্ছা!’ বলে জুলকারদের বাড়ির দিকে উড়ে চলল লক্ষ্মী।
তিন
গল্পটা এখন জুলকার-নাইন বলছে না, বলছে অন্য কোনও আনাম। মজলিস শুরু হল সকাল দশটায়। জুলকারের বাবাও এসেছেন লোকনাথের কারসাজি দেখতে।
মনসুর জানেন, লোকনাথ জাতি-অহংকারে আর্য-অপেক্ষা বাড়া। জহুরা কিন্তু রসিদাকে জড়িয়ে ধরে কাঠের গুঁড়ির পরে বসে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছেন গাছে-বাঁধা বাপ-বেটার দিকে। আর যত যত মুরুব্বি এসেছেন তাঁদের দিকে তাকাচ্ছেন; জহুরার গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্মী; লক্ষ্মীর মা কৌশল্যার চোখ দিয়ে নিঃশব্দে জল ঝরছে।
ধানের বস্তার দিকে মনসুর মাঝেমাঝে দেখছেন।
তবারক মিঞা হরিলালকে প্রশ্ন করলেন, ‘কী হে হরি, আকালের দিনে ছেলেকে নিয়ে মনসুর মাস্টারের জমির ধান সাবাড় করলে!’
হরি তো বোকা-গুর্বো; বললে, ‘কী করব! ২৮ দিন ভাত খাইনি মিঞাসাব! বেগতিকে সব ঘটে গেল বাবা! সদ্যমরা গরুর গো-মাংস চুরি করি নাই, মিঞাভাই; টাটকা ধান বস্তায় ভরেছি।’
তখন তবারক বললেন বাবুর উদ্দেশে, ‘শিক্ষিত হয়ে তুমি এই কাজ করতে পারলে বাবু!’
বাবুলাল বলল, ‘শিক্ষিত বলেই তো পারলাম জনাব।’
— ‘কীরকম!’
বড্ড অবাক হয়ে তবারক মুনশী প্রশ্ন করলেন সৌমিত্রকে।
সৌমিত্র বলল, ‘আজ্ঞে। পড়ে-বুঝেই চুরি করেছি।’
— ‘বল, সেটা!’
— ‘কী বলব?’
— ‘পড়েটড়ে কী বুঝেছ তুমি!’
— ‘বইটা কিন্তু ইংরেজিতে লেখা।’
গোলমুখো, মাথা নেড়া, থুতনিতে দু’চার নরি দাড়ি তবারক ধাক্কা খেলেন ইংরেজির নাম শুনে; বোকা-বোকা হেসে আমতা-আমতা করে তবা মুনশী বললেন, ‘যা হোক, তা হোক, তবো বল শুনি, কী পড়েছ, বাংলা তর্জমা করে দিলেই সবাই বুঝে যাব।’
— ‘জনাব, এখানে ইংরেজি কেউ জানে না। জানে মনসুর মাস্টার আর তেনার পুত্র জুলকার। জুলকারকে বইটা পড়তে দিয়েছিলাম, ওর পড়বার সময় হয়নি। মাসিমার কাছে বইখানা আছে; নতুন হাসানপুর পাঠাগারের বই; পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা রইস মণ্ডলের ব্যক্তিগত সংগ্রহের বই; উনি সে বই পাঠাগারকে দান করে গেছেন, বইটি পূর্ববঙ্গ থেকে আনিয়েছিলেন। বইটির লেখক জেমস টেলর; ১৮৩৯ সালে এই বই লেখা হয়েছিল; রইস সে বই একশো বছর পর বাংলা বাজার থেকে জোগাড় করেন। সে বই ১৯৬৮ সালের দুর্ভিক্ষের বছর আমি পড়েছি। মাস-তিন আগে।’
মনসুর বললেন, ‘যাও জুলকার। নিয়ে এসো, বই।’
জহুরা তাঁর কোমর থেকে চাবি বার করে ছেলের হাতে দিয়ে বললেন, ‘কাঠের বাক্সে পাবে, জলদি করে আনো।’
জুলকার ছুটল।
বই এল। তবারক মুনশী বই হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, ‘তুমি যেমন আরবি জানু না, আমি তেমনই ইংরাজি জানু না বাবুলাল; শোধবোধ হয়্যা গেল। ইবার কও কী নিকেছে এই কিতাবে। অ্যাই কে আছিস, বাপ-বেটার বাঁধন খুল্যা দে।’
বাঁধন খোলা হল।
— ‘কও।’
— ‘আজ্ঞে।’
বাবুলাল বলতে শুরু করল বৃত্তান্ত। তা নিম্নরূপ:
বইটির নাম, ‘টপোগ্রাফি অফ ঢাকা’— প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা মিলিটারি অরফান প্রেস থেকে। প্রকাশকাল, ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ।
— ‘ব্যাস ব্যাস! আর শুনতে চাই না। এখন বল, ধান তুমি কীভাবে বস্তায় ভরলে? টেলর সাহেব ধানের ব্যাপারে কিছু বলেছেন?’
বলে ওঠেন তবা মুনশি।
বাবু বলল, ‘ সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছি মুনশি সাহেব। ওই বইতে ব্যান্ডিকুট ইঁদুরের কথা আছে, বাংলায় এদের ধেড়ে ইঁদুর বলে— এরা চাষির ধানের ক্ষতি করে। টেলর সাহেব বিবরণ দিয়েছেন, এই ইঁদুরেরা ধান নিয়ে মাটির নীচে তাদের কুঠরিতে জড়ো করে রাখে। এই সব কুঠরির সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ রক্ষার জন্য মাটি খুঁড়ে পথ তৈরি করে। গরিব লোকেরা হামেশাই এই সব ধেড়েদের বাসায় সন্ধানে ফেরে আর এক-একটা বাসা থেকে অনেক সময় এক থেকে দু’মণ ধান পেয়ে থাকে। দেখা গেল, ঠিক তেমনটাই শিশাডিহির মাঠে, জুলকারদের ষাটী ধান নিয়ে ঘটনা ঘটে গেছে। মাসিমাকে বলেছি ইঁদুরের মুখ থেকে অন্ন কেড়ে নিতে হলে হবে; তুমি কী বলছ বলো!’
— ‘আপনি কিছু বলবেন জহুরা আহমেদ?’
জানতে চান মুনশি।
হঠাৎ রসিদা বলে ওঠেন, ‘আকালের ধান ইঁদুরের মুখ থেকে নিলে লুকনাথের পক্ষে টর্চ ঘুমানোর কী থাকতে পারে! বাবুলাল পেটের দুঃখে লড়ছে; আমার জমিতে সুড়ঙ্গ করেছে ইঁদুরে, তার আমি কী করব? আমাকে কেন বাইশীতে ডাকা হল?’
জহুরা বলে ওঠেন, ‘আমাকে সব বলেই বাবু যা করবার করেছে; ও ওই বস্তা মাথায় করে আমার উঠোনে আনছিল; ওকে গাছে বাঁধা হল কেন আর হরিলালকেই বা এত অপদস্থ করা কেন? বাবু বলেছে, মাসিমা ষাটীর পায়েসে যেন জুলুর সঙ্গে ভাগ পাই। ব্যাস। এইই তো কথা! আমি বলেছি একবস্তা ধান মুচিপাড়ার টিকরে যাবে। ২৮ দিন ভাত খায়নি হরির পরিবার। দুর্ভিক্ষের সময় অত টর্চ-মারামারি কোরো না লোকনাথ। বাবুলালও আমার ছেলে; আমি জাত মানি না। অন্নই ভগবান। ব্যাস।’
শেষ কথা:
তারপর রুইদাস টিকর (ডিহির) থেকে রুইদাসরা এল ঢাক-ঢোল-কাঁসি নিয়ে শিশাডিহি। প্রচণ্ড বাদ্যি শুরু হল। ধেড়ে ইঁদুরের দল ষাটী ধানের সুড়ঙ্গ ছেড়ে পালাতে লাগল ভৈরব নদীর দিকে। নদীর বেগবান স্রোতে ঝাঁপ দিল।
রুইদাস টিকর ভাতের গন্ধে ভরে গেল।
রুইদাসরা মারী ও মন্বন্তরে মরেনি।
বাবুলাল বুড়ো হয়েছে।
ঢাক বাজাচ্ছে শেয়ালদা স্টেশনের চাতালে।
তার সঙ্গে কাঁসি বাজাচ্ছে তার নাতি।
এখন মারী ও দুর্ভিক্ষের ভারতে প্রতিদিন আত্মহত্যা করছে গরিব। প্রতিদিন অন্তত ৫০০জন করে।
তথাপি মারী ও মন্বন্তর অতিক্রম করে বাবুলালের ঢাক ও কাঁসি।
কোভিড ও ওমিক্রন তাড়াচ্ছে রুইদাস। ঢাক আর কাঁসি বেজেই চলেছে। থামছে না।
তাই ধেড়ে ইঁদুরের গল্পের কোনও শেষ নেই।
ওই ঢাক-ঢোল হল এই মারী ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিবাদ।
কেননা ওই বাদ্য মারী ও দুর্ভিক্ষের তাড়ানোর ক্ষেত্রে বাঙালির নিজস্ব পদ্ধতি।
বাবুলাল পাগলের মতো নাচছে আর ঢাক পেটাচ্ছে; তার নাতিও আশ্চর্য নাচ দিয়েছে কলকেতায়।
মাসি জহুরার রান্না করা ষাটী ধানের পরমান্ন আজও বাবুলাল রুইদাসের জিভে লেগে আছে; সে-কথা মনে এল বলে বাবুর বাদ্যি-বাজনার তোড় আরও বেড়ে গেল।
তার ছোট্ট নাতি ননি রুইদাস তালবাদ্যির প্রতিযোগিতায় দাদুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল; ননি, লক্ষ্মী রুইদাসের ছেলের ছেলে, ভাল নাম উত্তমকুমার।

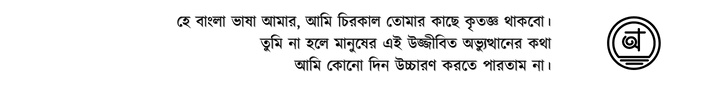

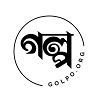

0 মন্তব্যসমূহ